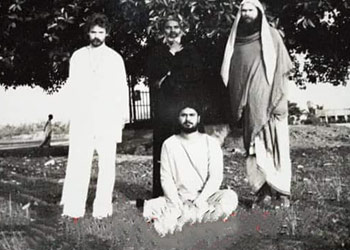[ স্থান :- পরমানন্দ মিশন সময় :- ২০/৫/১৯৯২ – ২৫/৫/১৯৯২ উপস্থিত ব্যক্তিগণ :- জয়দীপ, প্রণতিমা, খোকন মহারাজ, স্বরূপানন্দ প্রমুখ।]
জিজ্ঞাসু :– প্রাচীনকালে তপোবনগুলিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু ছিল__এমন শোনা যায়। তার মানে, সেগুলিই ছিল এখনকার বিদ্যালয়। কিন্তু তখনকার দিনে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কেমন ছিল গুরুজী ?
গুরুমহারাজ :– তপোবনগুলিতে প্রথম অবস্থায় শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি ছিল শুধুই ‘শ্রুতি’-র মাধ্যমে। কোনো so called পুস্তকের ব্যবহার প্রথমদিকে একদমই ছিল না। লিপির সৃষ্টি এবং ভূর্জপত্রে বা তালিপত্রে লেখার প্রচলন তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক পরে এসেছিল। ব্যাসদেবের সময় থেকে বেদাদি শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাশ্ত্র লিপিবদ্ধ হবার কাজ শুরু হয়েছিল।
তখনকার দিনে পাঠদানের জন্য আচার্য্য বা শিক্ষকেরা বিভিন্ন সূত্রের ব্যবহার করতেন – যেমন ধরো ‘ব্রহ্মসূত্র’ ! এইসব নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের বা ছাত্রদেরকে এক একদিনের পাঠদান হিসাবে এক একটি সূত্রের উল্লেখ করতেন। শিষ্যরা বা ছাত্ররা সেটি শুনে মুখস্ত করে নিতো এবং আপন আপন কাজে চলে যেতো ! কিন্তু সারাদিন ধরে চলতো নিদিধ্যাসন। ছাত্রদের মেধার level অনুযায়ী এক একজনের এই চিন্তন চলতো একদিন, দুদিন বা তিনদিন পর্যন্ত। এরপর যে যেমনটা সেই সূত্রের অর্থ বুঝলো – সে তেমনভাবে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করে গুরুকে শোনাতো। অধিকারীভেদে গুরুও সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে কিছু কথা যোগ বা বিয়োগ করে পৃথক পৃথক ভাবে শিষ্যদেরকে পাঠদান করাতেন৷
এক একজনের এক একটা পাঠ সম্পন্ন হোলে – তার জন্য আবার থাকতো নতুন পাঠ – অর্থাৎ আবার তাকে দেওয়া হোতো নতুন চিন্তার খোরাক। এইভাবেই দেখবে– একই ব্রহ্মসূত্রের নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে। অথচ তোমরা যদি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ভাষ্য পাঠ করো – তাহলে মনে হবে সবগুলোই সঠিক। সব মতগুলিই পরম্পরাগতভাবে বহুকাল ধরে সমাজে প্রচলিতও রয়েছে। ব্যাসদেব-শুকদেব-শংকরাচার্য্য–শ্রীধরস্বামী-রামানুজ প্রমুখরা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করেছেন বা টিকা-টিপ্পনী লিখে গেছেন। একই সূত্রের ব্যাখায় আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, আবার সেই সূত্রের অন্য ব্যাখ্যা করেছেন রামানুজাচার্য্য ! তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দ্বৈতবাদ (বিশিষ্ট)।
যাইহোক, এইভাবেই প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরাম্পরাক্রমে জিজ্ঞাসা উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি চলতো।৷(ক্রমশঃ)
জিজ্ঞাসু :– প্রাচীনকালে তপোবনগুলিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু ছিল__এমন শোনা যায়। তার মানে, সেগুলিই ছিল এখনকার বিদ্যালয়। কিন্তু তখনকার দিনে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কেমন ছিল গুরুজী ?
গুরুমহারাজ :– তপোবনগুলিতে প্রথম অবস্থায় শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি ছিল শুধুই ‘শ্রুতি’-র মাধ্যমে। কোনো so called পুস্তকের ব্যবহার প্রথমদিকে একদমই ছিল না। লিপির সৃষ্টি এবং ভূর্জপত্রে বা তালিপত্রে লেখার প্রচলন তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক পরে এসেছিল। ব্যাসদেবের সময় থেকে বেদাদি শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাশ্ত্র লিপিবদ্ধ হবার কাজ শুরু হয়েছিল।
তখনকার দিনে পাঠদানের জন্য আচার্য্য বা শিক্ষকেরা বিভিন্ন সূত্রের ব্যবহার করতেন – যেমন ধরো ‘ব্রহ্মসূত্র’ ! এইসব নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের বা ছাত্রদেরকে এক একদিনের পাঠদান হিসাবে এক একটি সূত্রের উল্লেখ করতেন। শিষ্যরা বা ছাত্ররা সেটি শুনে মুখস্ত করে নিতো এবং আপন আপন কাজে চলে যেতো ! কিন্তু সারাদিন ধরে চলতো নিদিধ্যাসন। ছাত্রদের মেধার level অনুযায়ী এক একজনের এই চিন্তন চলতো একদিন, দুদিন বা তিনদিন পর্যন্ত। এরপর যে যেমনটা সেই সূত্রের অর্থ বুঝলো – সে তেমনভাবে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করে গুরুকে শোনাতো। অধিকারীভেদে গুরুও সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে কিছু কথা যোগ বা বিয়োগ করে পৃথক পৃথক ভাবে শিষ্যদেরকে পাঠদান করাতেন৷
এক একজনের এক একটা পাঠ সম্পন্ন হোলে – তার জন্য আবার থাকতো নতুন পাঠ – অর্থাৎ আবার তাকে দেওয়া হোতো নতুন চিন্তার খোরাক। এইভাবেই দেখবে– একই ব্রহ্মসূত্রের নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে। অথচ তোমরা যদি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ভাষ্য পাঠ করো – তাহলে মনে হবে সবগুলোই সঠিক। সব মতগুলিই পরম্পরাগতভাবে বহুকাল ধরে সমাজে প্রচলিতও রয়েছে। ব্যাসদেব-শুকদেব-শংকরাচার্য্য–শ্রীধরস্বামী-রামানুজ প্রমুখরা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করেছেন বা টিকা-টিপ্পনী লিখে গেছেন। একই সূত্রের ব্যাখায় আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, আবার সেই সূত্রের অন্য ব্যাখ্যা করেছেন রামানুজাচার্য্য ! তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দ্বৈতবাদ (বিশিষ্ট)।
যাইহোক, এইভাবেই প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরাম্পরাক্রমে জিজ্ঞাসা উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি চলতো।৷(ক্রমশঃ)