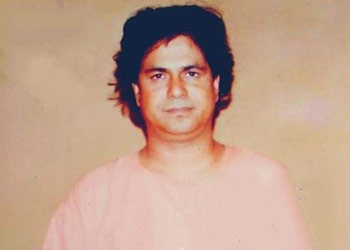সময় ~ ১৯৮৯, জুলাই ৷
উপস্থিত ব্যক্তিগণ ~ শেখর, গঙ্গাবাবু, এনাঙ্কবাবু, রত্না ইত্যাদি ।
জিজ্ঞাসু :— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মা-কে একবার বৃহস্পতিবারের বার-বেলায় দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য পুনরায় ফেরৎ পাঠান — যাত্রা পাল্টে আসার জন্য, তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে ঠাকুরও কুসংস্কারযুক্ত ছিলেন?
গুরুমহারাজ :— তিনি কি ছিলেন _আর কি ছিলেন না, তা তোমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি করে মাপবে বাবা! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই বলতেন — “চিনির পাহাড় দেখে একটা পিঁপড়ে খুব খানিক খেলো, তারপর হেউ-ঢেউ করতে করতে একদানা মুখে করে বাসার দিকে নিয়ে গেল, আর ভাবল পরের বার এসে পুরো পাহাড়টাই নিয়ে যাবে”। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও এই উদাহরণটা খাটে ! কোন তত্ত্বের যতটা সে বোঝে, ততটাই ঢেঁকুর তোলে — অর্থাৎ সমাজে উগরে দিয়ে তার মতামতটাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়_মানুষ। যেন সবাই শিক্ষক — ছাত্র হতে কেউ চায় না! এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানও হয় না। কারণ শাস্ত্রে আছে “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্” — শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞানলাভ হবে কি করে? নিজেকে বড় না ভেবে ছোট হতে শেখো — তুমি কতটা সিদ্ধান্ত দেবার অধিকারী তা বিচার করো — তবেই তোমার বিবেকের জাগরণ ঘটবে এবং অন্তরে শ্রদ্ধার উদয় হবে। তখন সেই বিবেক ও শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে যে জিজ্ঞাসার অবতারণা হবে, তার সদুত্তর তুমি নিশ্চয়ই পাবে। তখনই তোমার অন্তর্জগৎ ঠিক ঠিক সেইসব জ্ঞান ধারণ করার উপযুক্ত হবে_ অর্থাৎ তোমার ধারণা সঠিক হবে। অন্যথায় আজেবাজে ধারণা-প্রসূত জিজ্ঞাসা মনে উদয় হলে শুধু মনই বিক্ষিপ্ত হয়; কাজের কাজ কিছু হয় না।
যাইহোক, এখন কি বলছি তা মন দিয়ে শোন। দেখ স্বামী বিবেকানন্দ__ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন বুঝেছিলেন, তার থেকে তো তুমি বেশি বোঝনি? স্বামীজী একবার বলেছিলেন —” সমস্ত ভারতীয় ঋষি-মহাপুরুষগণের সম্মিলিতরূপ ভাবতে গেলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবতে হয়”। তোমার জিজ্ঞাসার ধরনটা খুব একটা শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ছিলনা বলেই এত কথা বলতে হোল। এবার তোমার জিজ্ঞাসায় আসি। সারদা মা বৃহস্পতিবারের বার-বেলায় দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছানোয় ঠাকুর তাঁকে যাত্রা পাল্টে আসার কথা বলেন একথা “শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে লেখা রয়েছে , সুতরাং ঘটনাটা সত্যি। এখন কথা হচ্ছে যে, মা-সারদা ছিলেন তৎকালীন গ্রাম্যবধূ, যখনকার সমাজ শুধু আচার আর বিধানসর্বস্ব ছিল। ফলে আচার-বিধান এগুলি কেউ না মানলে গ্রামে-গঞ্জে পাঁচজনে পাঁচকথা বলাবলি করত এবং খুবই নিন্দা রটত। তার উপর ছিল শিরোমণি, ন্যায়রত্ন ইত্যাদিদের ছিল আচার-ভাঙার বিচার। এছাড়াও ঐসময় ঠাকুরের হাত ভেঙে যাওয়ায়, ‘বারবেলার’ ব্যাপারটা শ্রী শ্রীমায়ের মনেও হয়তো রেখাপাত করে থাকতে পারে! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভাবজগতের রাজা, কারও ভাব তিনি নষ্ট করতেন না। অজান্তে একবার তিনি সারদামাকে ‘তুই’ বলেছিলেন বলে সারারাত ঘুমাননি — সকালে মায়ের কাছে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ জানিয়ে তবে শান্তি। সুতরাং এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কারো মনে সংশয় ছিল — অন্তর্যামী ঠাকুর সেটি বুঝতে পেরেই ঐরূপ বিধান দিয়েছিলেন! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ঘটা এরকম অনেক ঘটনা নিয়েই সমাজে সমালোচনা করা হয় কিন্তু সিদ্ধান্ত করতে যাওয়াটাই হলো চরম মূর্খামি। কোন ব্যাপারে সংশয় জাগলে সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসার দ্বারা, যিনি জানেন তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হয় — এটাই তো ঠিক পদ্ধতি। অকারণ সমালোচনা করে লাভ কি? আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষদের কোন কাজের সমালোচনা করার স্পর্ধাই-বা তোমাদের আসে কি করে? তারপর সেখান থেকে আবার মনগড়া এক একটা সিদ্ধান্তও করে বস তোমরা — এটা আরও হীনবুদ্ধির পরিচয়! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গবেষণা হতে পারে — সমালোচনা নয়। আর এটাও জেনে রেখো, মহাপুরুষদের নিয়ে সমালোচনা করলে কোন মহাপুরুষকেই খাটো করা যায় না, বরং যাঁরা সমালোচনা বা বিকৃত আলোচনা করেন_ তাঁদের চরম ক্ষতিসাধন হয়। আধ্যাত্মিক জগতের এমনই বিচিত্রবিধান।
জিজ্ঞাসু :— মহাপুরুষরা তো বিভিন্ন ভাবে চান সবাই এক হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও নানা সাধনা করে ‘যতমত ততপথ’ — বলে সকলকে একমতে আনার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু “মহামিলন” তো হোল না — তাহলে এটা কি অসম্ভব?
গুরুমহারাজ :— সবাইকে একমতে এনে কি একটা খিচুড়ি বানাবে নাকি? কালও তুমি Seminar-এ এই ধরনের কি যেন একটা জিজ্ঞাসা তুলেছিলে — কি বলতে চাইছ তুমি, পৃথিবীর সব মানুষ এক মতের হবে — মহামিলন হবে, এইতো?
শোনো, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণ দিয়ে তুমি বললে — তিনি বিভিন্ন আচার ও বিভিন্ন ধর্মমত অনুযায়ী সাধনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন মত হলেও সব ধর্মমতের মধ্যে দিয়েও সেই চরমলক্ষ্যে পৌঁছানো যায়!বেশ ভালো কথা_ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যে ধর্ম-মত রয়েছে সেগুলোর বিরোধ কোন মহাপুরুষ করেছেন কি? দেখবে,তাঁদের এই নিয়ে কোন মাথাব্যথাই নেই — তাঁরা জানেন সঠিক পথের সন্ধান, জীবন পথে এগিয়ে চলার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সুতরাং তুমি কোন্ মতের, সে নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাবেন কেন? যদি কোথাও_কোন মতবাদে বা কোন ধর্মগুরুর কথায় এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি তুমি পেয়েও থাকো, তাহলে জানবে — হয় তিনি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিই নন, অথবা ঐ ধর্মগুরুর দেহান্তের পর, পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যেরা নিজের মতামত চালিয়ে মূল বক্তব্যকে বিকৃত করেছে।
যে মাটিতে দাঁড়িয়ে তুমি পৃথিবীতে এতো ভেদ দেখছো —এই মাটি বা জমির অংশ ভাগ করে অথবা ‘আল’ দিয়ে শত-সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করেছে মানুষ! কিন্তু যদি তুমি অনেক উপর থেকে পৃথিবীকে দেখো, তাহলে আর এইসব ভেদ দেখতে পাবেনা। এবার যদি তুমি অন্য গ্রহ থেকে দেখো — তাহলে এই পৃথিবীকে সুন্দর উজ্জ্বল সবুজাভ একটি গ্রহ বলে মনে হবে। আধ্যাত্মিক জগতেও উন্নত অবস্থার ক্রম রয়েছে — নীচু তলায় মত-অমত, মতবিরোধ ইত্যাদি থাকে, উপর তলায় সবাই শান্ত_ সেখানে সবাই একই পথের যাত্রী। এইজন্যেই বলা হয়েছে — ‘চরৈবেতি’। মত-পথ নিয়ে অকারণ বিতর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট না করে যে মতেই আছো সেটাকেই পথ করে অগ্রসর হও — এটাই তো প্রাচীন ভারতের ঋষিদের শিক্ষা।
আর তুমি মহামিলন-টিলন কি সব বলছ? ওসব কখনই ছিল না, আর হবেওনা কখনও! কোন কোন Organization স্থানীয়ভাবে এইসব করতে চেষ্টা করে কিন্তু Successful হয় না। সুতরাং পৃথিবীব্যাপী সামগ্রিকভাবে তো কখনই সম্ভব নয়। এই সদা পরিবর্তনশীল মহাবিশ্ব_ ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের কম বেশি প্রকাশের তারতম্যে জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণীজগতে_ এত বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য বহির্জগতে যেমন_ তেমনি অন্তর্জগতেও কম নয়। সুতরাং এই মহাবিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত পৃথিবী গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রজাতি মানুষের সবাই বা এক রকম হবে কেন? গুণ এবং কর্মের বিভাগের তারতম্যে মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। ত্রিগুণের প্রকাশের ক্রম অনুযায়ী এবং কর্মের বিভাগ অনুযায়ী মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র এই চারটি বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। গুণ ও কর্ম বিভাগের পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটান যায়, এই ভাবে রূপান্তর হয় কিন্তু সবাই একই হয়ে যাবে এমন কখনই হবেনা। মা জগদম্বা যে খেলাঘর পেতেছেন, সে খেলাঘর তিনি নিজে না ভাঙলে, এমনিতে অন্য কোন ভাবে কি নষ্ট করা যায়? এই বৈচিত্র্য-আদি যা কিছু দেখছ, মত-পথ, বিরোধ-মিলন — সবই মায়ের খেলা বই আর কিছু নয়! মা যতদিন চাইবেন এরূপই চলবে। তবে একটা কথা, — বৈচিত্র্য আছে, আবার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যওরয়েছে। যদি বৈচিত্র্যের মধ্যে এক-কে ধরতে পারো, তাহলে বৈচিত্র্যের মধ্যেই আনন্দের আস্বাদন হবে, অন্যথায় ভেদদর্শন-জনিত যে ক্লেশ জন্ম-জন্মান্তর ধরে হয়ে চলেছে — তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না।
জিজ্ঞাসু :– যখন মাথার উপর Star-War, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার বিভীষিকা! –আমি জানিনা আমার তিন বছরের ছেলেটি আমার বয়স দেখতে পাবে কিনা, তখন আমরা আপনাদের কাছে ধর্ম-কর্মের গল্প শুনে শান্তি পাবো,এইরকম ভাবাটাই ভুল এবং আমার মনে হয় আপনি যে আধ্যাত্মিক গুরুর ভূমিকাটা পালন করছেন,_ সেটাও ভুল ! (ভদ্রলােক ইংরাজী এবং বাংলা মিশিয়ে রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করছিলেন।)
গুরুমহারাজ :– আপনি তাে বাংলা ভালােই বলতে পারেন, তাহলে অযথা ভুল-ভাল ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে আপনার বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করছেন কেন ? আপনি বলতে চাইছেন যে, মাথার উপরে যেখানে Star-war-এর হুমকি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা; সেখানে আপনি বা আপনার সন্তান বাঁচবে কিনা সন্দেহ—ইত্যাদিতো? তা সেই ভয়ে আপনি কি আহার, নিদ্রা মৈথুন ত্যাগ করেছেন নাকি ? নাকি আপনি আপনার চাকরির প্রমােশন নেবার জন্য অথবা ছেলেকে ভালাে স্কুলে ভর্তি করার জন্য ‘দাদা’ ধরছেন না ? অর্থাৎ বলতে চাইছি আপনি আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী তাে ঠিকই কাজ করে চলেছেন, আর আমি আমার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে চলেছি, তাহলে আপনি আমার কাজের বিরােধ করছেন কেন ? আপনার প্রকৃতিতে যদি ধর্ম-কর্ম করার অভ্যাস না থাকে, তাহলে আপনি আর যে সব কর্ম করছেন তাই নিয়েই থাকুন না—কে নিষেধ করেছে আপনাকে? অন্যকে আঘাত করার মানসিকতা কেন ?
দেখুন, কথায় আছে “বুদ্ধিমানেরা দেখে শেখে, আর বােকারা ঠেকে শেখে”। তাই বুদ্ধিমানেরা অতীতকে পর্যালােচনা করে সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করে, যাতে জীবন পথের পাথেয় হিসাবে অতীতের জ্ঞানী-গুণী মানুষদের জ্ঞানকে জীবনে কাজে লাগাতে পারে । এই জন্যই বলা হয়েছে ‘মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ’। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত দিয়ে বা ধনী-নির্ধন দিয়ে বােকা-বুদ্ধিমান বিচার করা হয়নি! যাঁরা মহাজনের পথ অনুসরণ করে জীবনপথে এগিয়ে যান _তাঁরাই ঠিক ঠিক চলেছেন লক্ষ্যের দিকে। তাই তাঁরা গতিশীল, তাঁরা জীবিত, আর যারা স্থূল জড়বুদ্ধিতে নিজেকে আটকে রাখে এবং এগিয়ে চলার পথ দেখতে পায় না, তারা গতিহীন, মৃততুল্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ‘Moving dead body’।
আপনি প্রতিদিন দুবেলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখুন_ আর নিজেকে বিচার করুন! যেসব কথা আপনি বলেন, তা কি নিজে পালন করেন? আপনার যা করা উচিৎ তা কি করেন—অথবা যা করা উচিত নয় তা কি করেন না ? কোন সিদ্ধান্তে অচল না থেকে বিশ্লেষণ করুন, দেখবেন নিজের দোষসমূহকেই প্রথমে খুঁজে পাবেন— এই ভাবে আগে আপনার আত্মশুদ্ধি হােক। এমনটা হোলে তখন আর কারও দোষ দেখতে পাবেন না। আপনি নিজে যত পরিষ্কার হবেন, ততই পার্থিব রহস্যসমূহ আপনা-আপনি আপনার নিকট উন্মােচিত হবে—পরিষ্কার হবে। মনুষ্যরূপ ‘জীবন’ যখন ধারণ করেছেন, তখন ‘জীবনের কলা’ মেনে জীবন কাটানােই তাে বুদ্ধিমানের কাজ। নচেৎ আহার-বিহার-নিদ্রা-মৈথুন এতেই মত্ত থেকে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে জীবন কাটিয়ে একদিন মরে যাওয়া—এতে বিশেষত্ব কি, আর বাহাদুরিই বা কি ! জীবিত অবস্থায় আপনার বাগাড়ম্বরের কথা কয়েকজন হয়ত কিছুদিন মনে রাখবে কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়_উত্তরকালের মানুষ মনে রাখে সেই সব মহাজীবনদের কথা, যাঁরা “জগৎ-জীবন ও ঈশ্বরের রহস্য” জেনেছেন ! তাঁরা নিজে মানুষের মনে বেঁচে থেকে, অপরদেরকেও বাঁচতে শিখিয়েছেন। যারা তাঁদের বিরােধ করেছে_তারা হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেই মহাপুরুষেরা মানুষের মনের মণিকোঠায়বহুকাল রয়ে গেছেন। দেখুন, আমি আপনাকে এই সব চিন্তার সূত্র দিলাম—গ্রহণ করবেন, দেখবেন উপকার পাবেন ।
জিজ্ঞাসু :— মানুষ কি নিজের চেষ্টার দ্বারা সেই “চরম লক্ষ্যে” পৌঁছাতে পারে?
গুরু মহারাজ :— কেন পারবে না — পৌঁছাতে তো হবেই, আজ না হয় কাল! আর প্রচেষ্টাই তো প্রধান। আরও শুদ্ধ ভাষায় একে ‘প্রযত্ন’ বলা হয়েছে। দ্যাখো, জীব-বিজ্ঞানীরা তো Evolution মেনেছে এবং ক্রমবিকাশের প্রধান শর্ত ধরেছে ‘প্রচেষ্টা’-কেই! Insecurity থেকে Secured হবার যে প্রচেষ্টা _তাকেই বলা হয়েছে ক্রমবিকাশের প্রধান শর্ত। মনুষ্যপ্রজাতি থেকে ঠিক ঠিক মানুষ হয়ে উঠতে আরও কত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়! আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রথম শর্ত আবার “মনুষ্যত্বম্”। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ‘মান’- ‘হুঁস’__ মানুষ ! এরপরের শর্ত “মুমুক্ষুত্বম্” অর্থাৎ মুক্তি পাবার ইচ্ছা।জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হোতে গেলে ‘প্রযত্ন’ একান্ত প্রয়োজন!”প্রযত্ন” কিন্তু individual নয়, এটা universal ! নিজের ভোগ-বাসনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে চেষ্টা_ সেটা individual কিন্তু ‘মুক্তি পাবার ইচ্ছা’ — ‘বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ’ হয়ে যাচ্ছে_ তাই এটি universal !এই অবস্থায় ‘ব্যক্তিঅহং’ যেহেতু নাশ হয়ে যায়, তাই ঐ ব্যক্তি শরীরে থাকলে তাঁর দ্বারা শুধু জগতের কল্যাণই হবে — কখনই কোন অনিষ্ট হবে না।
ব্রহ্মের বিবর্তবিলাসে মায়া আশ্রিত হয়ে বা অহং যুক্ত হয়ে সেই এক-ই বহু হয়েছিলেন। বেদ বলেছে “বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি”। বলা হয় ‘শিব’ মায়াযুক্ত হয়ে ‘জীব’ হলেন। আবার জীব যখনই মায়ার ‘য়া’-কে বাদ দিয়ে শুধু ‘মা’-কে আশ্রয় করেন তখন স্ব-স্বরূপে ফিরে যান অর্থাৎ ‘জীব’ ‘শিব’ হন। শাস্ত্রে বলেছে, “স্বভাবে শান্তি, আর স্বরূপে আনন্দ”। পরাশক্তি বা মাকে আশ্রয় করাই জীবের স্বভাব, তাই মায়াকে অতিক্রম করে মাকে আশ্রয় করলেই জীব শান্তি পায় — আর স্বরূপের বোধ হ’লে আনন্দের আস্বাদন লাভ করে। রহস্যটা ধরতে পারছো — নাম ও রূপের অভিমানবশতঃ যতক্ষণ সে নিজেকে পৃথক ভাবছে ততক্ষণই সে জীব, আর অহং মুক্তি ঘটলেই শিব। সেই অখণ্ডই তো আছে, সচ্চিদানন্দ সমুদ্র বলা হচ্ছে না! সেই সমুদ্রে জীব যেন অসংখ্য বুদবুদ। সৃষ্টি হচ্ছে, কিছুক্ষণ থাকছে আবার সমুদ্রেই মিশে যাচ্ছে।
আবার দ্যাখো, সমুদ্রে দুটো Current, একটা Surface Current অন্যটা Under Current! Surface Current-এ কিছু পড়লে সেটা ঢেউ-এর ধাক্কায় ধাক্কায় শুধু ফিরে ফিরে আসে কিন্তু Under Current-এ একবার পড়লে আর ফিরে আসেনা। অহং এবং অভিমানযুক্ত জীব যেন Surface Current-এ ভেসে রয়েছে_এই অবস্থায় একবার ডাঙায় পড়ে এবং একবার জলে পড়ে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে ঘুরে মরে। ৮৪ লক্ষ যোনি অতিক্রম করার পরও এই আবর্তন। তবে এক একটা জন্ম — এক একটা জীবন যেন অভিজ্ঞতা লাভের সিঁড়ি বা ধাপ। সেই সেই ধাপ বেয়ে বেয়ে চলেছে চেতনার অভিসার। এই প্রবাহ বা ধারা চলছে কল্প থেকে কল্পান্তরে, অনাদি এইধারা। এই ধারা-ই ‘রাধা’ হয় যখন প্রকৃত অভিসার শুরু হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের আরোহ লীলায় জীব যখন আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে। এই পথে চলাই চরৈবেতি। আর সে পথে একবার চলতে থাকলে আর পথ হারাবার ভয় থাকেনা! কারণ রাজপথ একবার পেয়ে গেলে অলি গলি পথ আর ভালো লাগেনা। এই ভাবেই জীবের পথচলা একদিন শেষ হয়। তখন সেই ‘জীব’ আর ‘জীব’ থাকেনা__ শিবস্বরূপ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণতঃ এই অবস্থা লাভের পর জীবের শরীর বেশিদিন থাকেনা। তবে জগতের কল্যাণে ভগবানের ইচ্ছায় আবার শরীর ধারণ করতে হতে পারে আর তারজন্য কোন কর্মফলে আর আবদ্ধ হতে হয়না।
সুতরাং এটা বুঝলে তো,মানুষ প্রচেষ্টা বা প্রযত্নের দ্বারাই Evolution-কে Revolution-এ পরিবর্তিত করতে পারে। ‘লক্ষ্যে’ যখন পৌঁছাতেই হবে তখন গতিকে ত্বরান্বিত করাই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ম্যাদাটে বুদ্ধি ভাল নয়, বুঝতে যখন পেরেছেন, তখন ঝাঁপিয়ে পড়ুন — দেখুন ফললাভ হয় কি না হয়।