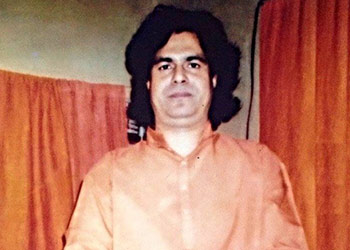স্থান ~ পরমানন্দ মিশন । সময় ~ ১৯৯২। উপস্থিত ব্যক্তিগণ ~স্বরূপানন্দ মহারাজ, জয়দীপ, সব্যসাচী মান্না, দেবীপ্রসাদ মুখার্জি, আশ্রমস্থ মহারাজগণ ও বহিরাগত ভক্তবৃন্দ ।
জিজ্ঞাসু :— মহারাজ, বহুপূর্বে প্রকৃতি দূষণমুক্ত ছিল এবং সেই সাথে জনসংখ্যাও কম ছিল বলেই কি মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল?
গুরুমহারাজ :— হ্যাঁ, এটাই তো কারণ। দেখোনা, এই সমস্ত অঞ্চল আগে বনজঙ্গলপূর্ণ ছিল। এখানকার ব্যাণ্ডেলের আগে যে আদিসপ্তগ্রাম স্টেশন, এটাই তো পূর্বের সপ্তগ্রাম বন্দর ! তখন সমুদ্র ওই স্থানের প্রায় কাছাকাছি ছিল। বর্তমানের কলকাতা তখন সুন্দরবনের লাগোয়া ছিল। কালীক্ষেত্র থেকেই তো কলিকাতা। বর্তমানের কালীঘাটই ছিল কালীক্ষেত্র। ঐ সমস্ত অঞ্চলে হিউয়েন সাঙ যখন ভ্রমণ করছিলেন সেইসময় স্থানগুলি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় — ওখানকার কাপালিকরা নাকি হিউয়েন সাঙকে ধরেছিল, তারপর কোন কারণে তাঁকে ছেড়ে দেয়। তখনও ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে নগরসভ্যতা ছিল বটে কিন্তু বেশিরভাগ অঞ্চল জলা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। লোকসংখ্যা কম থাকার জন্য মানুষের খাদ্যাভাব ছিল না। বিশেষত বঙ্গদেশে তো নয়ই। কারণ এখানে চাষ করলেই ফসল ফলে। প্রশস্ত ও অবারিত গোচারণ ভূমি থাকায় মানুষ সহজে গোপালন করতো। তাই তখন গোয়ালভরা গরু আর গোলাভরা ধান থাকত কৃষকের ঘরে ঘরে। আর বনের ফল, জলাশয়ের শাকসবজি এবং খাল-বিল-নদী-নালার মাছ ইত্যাদি দ্বারা বাঙালির জীবন সুখেই অতিবাহিত হোত — অন্যপ্রকার ভোগৈশ্বর্যের প্রত্যাশা তারা করতো না। বাঙালি গৃহস্থের চিরকালীন চাহিদা কবির ভাষায় ফুটে উঠেছে — “আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।” সমগ্র ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষই কমবেশি এই একই মানসিকতাসম্পন্ন! এটাকে বর্তমানে middle class mentality বলে হেয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে_কিন্তু এটাই সঠিক জীবন যাপন_simple living and high thinking!
গোটা বিশ্বে যখন ভোগ-বিলাসের প্রতিযোগিতা, যেখানে সে সব দেশে মুদ্রার মূল্য, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে হু হু করে কমে গেছে, সেখানে ভারতবর্ষের মুদ্রার মূল্য কিন্তু জিনিসপত্রের দামের তুলনামূলক হারে অতটা কমেনি! এটা পৃথিবীর অর্থনীতিবিদদের কাছে একটা বিস্ময়! এর কারণ কি বলতো, ঐ যে বললাম ভারতীয় মানসিকতা — ‘simple living…’!
যাইহোক যা বলছিলাম, তখনকার বঙ্গদেশ যেন প্রকৃত অর্থেই সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ছিল। প্রকৃতির উপর মানুষ যথেচ্ছাচার না করায় প্রকৃতিও ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক ঋতুর কাজ করে যেত। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এইরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোত কিন্তু কমই হোত। কোনরকম কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য উৎপাদন, ফসল উৎপাদন ইত্যাদি না হওয়ার জন্য মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের উপর খাদ্যজনিত কোন প্রতিক্রিয়া হোত না। যানবাহনের অভাব থাকায় মানুষকে পায়ে হেঁটেই দূর-দূরান্তে যেতে হোত।
তখনকার দিনে এইভাবে যাতায়াত করাটা খুবই কষ্টকর ছিল। এতে প্রচণ্ড সাহস এবং শক্তির প্রয়োজন হোত। কারণ রাস্তাই বা তেমন কোথায়? শুধু জলা এবং জঙ্গল আর তার মাঝ দিয়ে মেঠো পথ। কেঁদোবাঘ, গুলবাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি বন্যপ্রাণীরা প্রায়ই পথচারীদের আক্রমণ কোরতো। তখনকার দিনে প্রায়ই শোনা যেত কোন না কোন গ্রামে কেউ না কেউ খালিহাতে বাঘের মোকাবিলা করেছে! এখনকার কোন যুবক ছেলের সে সাহস আছে কি! আর তখন ছিল ফাঁসুড়ে, ঠ্যাঙাড়ে এবং ডাকাতের ভয়! ঠ্যাঙাড়েরা ছোট ছোট লাঠি ছুঁড়ে নিখুঁত লক্ষ্যে চলন্ত পথিকের পায়ে আঘাত কোরতো, এতে পথিক যেই পড়ে যেতো অমনি চারিপাশ থেকে ওরা ছুটে এসে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে তার সর্বস্ব লুঠ কোরতো। তখনকার দিনে জমিদাররাও লেঠেল পুষতো — ডাকাত পুষতো। ফলে সেই সময়কার মানুষদের প্রকৃতির সঙ্গে এবং জীবজন্তু ও দুষ্টপ্রকৃতির মানুষের সঙ্গেও সরাসরি physically সংগ্রাম করতে হোত। এইভাবে নাননভাবেলড়াই করে এবং নির্ভেজাল দূষণমুক্ত খাদ্য থেকে পুষ্টি পেয়ে মানুষের শরীরগুলি শক্ত-পোক্ত বা মজবুত হয়ে উঠতো।
আমরা ছোটবেলায় দেখেছি বাড়ির কেউ যখন দূর-দূরান্তে যাবার জন্য বের হোত, তখন বাড়ির মা তাকে এক গ্লাস দই-এর সরবৎ অথবা ঘোল খাইয়ে দিত। এর ফলে প্রচণ্ড পরিশ্রমেও ওই ব্যক্তির শরীর ঠাণ্ডা থাকত এবং গ্যাস-অম্বল হয়ে Sun stroke বা ওই ধরনের কিছু হোত না। পরবর্তীকালে অর্থাৎ এখন দই-এর অভাবে মায়েরা ছেলেরা বাইরে কোথাও গেলে দই-এর ফোঁটা দেয়। যে কোন অনুষ্ঠানে দধিমঙ্গল-এর পিছনে এটাই রহস্য। অনেক মাকে দেখেছি ছেলেরা বাইরে যখন কোথাও যাচ্ছে তখন এক গ্লাস বা এক কাপ গরম দুধ তাকে খেতে দিচ্ছে। এটা কিন্তু খুবই খারাপ। গরম দুধ খেয়ে ভিড়-বাসে বা ট্রেনে চলাচল করে দেখবে যে, শরীরে খুবই অস্বস্তি হবে -প্রচণ্ড ঘাম হবে- শরীর আনচান্ করবে অর্থাৎ গ্যাস-অম্বল হয়ে যাবে। হার্ট দুর্বল থাকলে হার্ট অ্যাট্যাকও হয়ে যেতে পারে! কিন্তু যদি এক কাপ দই-এর সরবৎ খেয়ে কেউ বের হয়_ তাহলে কোন অনিষ্ট তো হবেই না বরং শরীর শীতল থাকবে বা শরীরে একটা সাম্যভাব বজায় থাকবে।এসব কথা আমার বলার উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারছ — এখনকার মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে কিন্তু গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান জানে না। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাও জানে না। গোটাকয়েক বই মুখস্থ করে কি লাভ হবে যদি সেই শিক্ষা তার জীবনে নাম সই করা আর দোকানের হিসাব কষা ছাড়া অন্য কোন কাজে না লাগে! এখন তো বিশাল জনসংখ্যার চাপে দেশটা ধুঁকছে। স্বাধীনতার আগে কবি লিখেছিলেন _অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি। আজ অর্থাৎ ১৯৯০ সালে মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তা শুধু ভারতবর্ষেই ৯০ কোটিতে দাঁড়ালো। ভাবতো একবার কি সাংঘাতিক ব্যাপার! স্বাধীনতার আনন্দ কি শুধু এই একটা ব্যাপারেই পালন করল ভারতীয়রা! কি দেশপ্রেম এখনকার মানুষের আর কি সন্তানপ্রেম! গাদাগাদা সন্তান উৎপাদন করে দেশটাকে চরম সংকটে তো ঠেলে দিয়েছেই আর তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে গেছে একরাশ অন্ধকার! বেচারারা দিশেহারা, বুঝতে পারছে না কি করা উচিত। স্বাধীনতার সময়কালীন ওই লোকগুলির অবিমৃস্যকারিতায় ভুগছে এখনকার যুবসমাজ। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি শিক্ষিত বেকার পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারেরও চরম উদাসীনতা বেড়েছে এই ব্যাপারে। নানান সমস্যায় ভারতবর্ষের মানুষ আজ জর্জরিত। তবুও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির চেয়ে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে ভাল। আর এইটার জন্য তোমরা দুহাত তুলে জয় দাও তোমাদের পূর্বসূরি ঋষিদের উদ্দেশ্যে। যারা তোমাদের অস্থিতে মজ্জায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন সেই মহান শিক্ষা, ‘হে ভারত ভুলিও না তোমার আদর্শ সর্বত্যাগী শংকর’।
কিন্তু সমস্যা তৈরি হচ্ছে অন্য জায়গায়। যেখানে ২০টি ইঁদুরের থাকার জায়গা সেখানে ৮০টি ইঁদুর থাকলে যেমন হয় ভারতের জনসংখ্যার ঠিক সেই অবস্থা। আজ আর কোথায় জলা, কোথায় জঙ্গল, কোথায় বা কেঁদোবাঘ, গুলবাঘের দল? জঙ্গল কেটে জলা বুঁজিয়ে কৃষিজমি তৈরি করেও খাদ্যের সমস্যা মিটছে না। ফলে বাধ্য হয়ে উচ্চফলনশীল hybrid production-এর ব্যবস্থা করল কৃষি বিজ্ঞানীরা। ওরা আর কি করবে, পরিস্থিতির মোকাবিলায় ওদের এটাই করার ছিল! আর এল রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধাদি যা ওই hybrid শস্যগাছগুলিকে যথাক্রমে পুষ্টি জোগাবে ও রক্ষা করবে। এতেই ঘটে গেল বিপত্তি! প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা শরীরের D.N.A. বা জিন, হঠাৎ করে কৃত্রিমভাবে গঠিত জিনবিন্যাসযুক্ত খাদ্যকণার গুণাবলীকে ঠিকমত adopt করতে পারল না। ফলে এক জেনারেশনের মধ্যেই হু হু করে ভারতীয়দের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। আর তার সঙ্গে এসে গেল কঠিন কঠিন মারাত্মক ব্যাধিসমূহ। এইভাবেই ভারতীয়দের জাতীয় স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। তবে প্রকৃতিতে দেখা যায় তিন generation-এর মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং আগের প্রজন্ম, বর্তমান প্রজন্ম এবং হয়ত আরএকটা প্রজন্ম এই সমস্যা ভোগ করবে। তারপর কিন্তু দেখবে আবার natural way-তে ফিরে আসবে সবকিছু।জিজ্ঞাসু :– শালগ্রাম শিলায় নারায়ণ আছে – এরূপ বলা হয়। এর প্রকৃত রহস্যটা কি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন?
গুরুমহারাজ :—-কথাটা শালিগ্রাম, ‘শালি’ অর্থাৎ অনন্ত আর ‘গ্রাম’ অর্থে অবস্থান। অনন্তের যেখানে অবস্থান তাই শালিগ্রাম। সাধারণত হিমালয়ের পাদদেশে বুড়ীগন্ডক বা গণ্ডকী নদীর উৎসমুখে এক ধরণের বিশেষ শিলা পাওয়া যায় যেগুলির রঙ কালো, আর যেগুলিকে বজ্রকীট নামক একপ্রকার কীট কেটে কেটে খেয়ে তাদের জীবন-ধারণ করে! সেই পাথরগুলিকেই শালিগ্রাম বা শালগ্রাম শিলা হিসাবে মান্য করা হয়। ওগুলি নদীর উৎসমুখের পার্বত্যপথ বেয়ে চড়াই উতরাই ভেঙে প্রচন্ড গতিতে নীচে নামে, ফলে ছোট ছোট শিলাগুলি পাথরের সঙ্গে ঘর্ষণে ঘর্ষণে মসৃণ, গোলাকৃতি বা ডিম্বাকতি এবং চকচকে হয়। আর শালগ্রাম শিলার গায়ে যে বিশেষ চিহ্নগুলি থাকে সেগুলি বজ্রকীটে কাটার ফলেই সৃষ্টি। এই চিহ্নের আকার, আয়তন, অবস্থান অনুযায়ী এক একটি শালগ্রামের এক-একরকম নামকরণ হয়। কিছুদিন আগে একজন লোক আমার কাছে এসে বলল যে, তার শালগ্রাম শিলায় আগে নাকি তিনটে চক্র ছিল, এখন সেটায় চারটে চক্র দেখা যাচ্ছে। তাহলে সেটা আর রাখা ঠিক হবে কিনা – এই বিধান সে নিতে এসেছে আমার কাছে। এখানে জ্যাঠামশাই (দেবীবাবু) বসে আছেন, উনি ব্যাপারটা জানেন যে, শিলার গায়ে চক্রের অবস্থান এবং সংখ্যা অনুযায়ী নারায়ণের নামকরণ পৃথক হয়ে যায়। এখন আমি আর ওকে কি বলি! হয়ত এখনও শিলাটিতে কোন কীট রয়ে গেছে, ফলে নতুন করে দাগ কেটেছে অথবা হয়ত আগে থেকেই ভিতরটা কাটা ছিল_ পরবর্তীকালে উপরের অংশটা খুলে গিয়ে ঐরূপ হয়েছে !
শালগ্রাম শিলার প্রকৃত তাৎপর্য তোমাদের কাছে বলছি শোনো_ বৈদিক যে পঞ্চশাখা অর্থাৎ সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য - এদের মধ্যে বৈষ্ণবদের শালিগ্রাম শিলা পূজার বিধি রয়েছে, তেমন শৈবদের রয়েছে অনাদি শিবলিঙ্গ পূজার বিধি। ব্যাপারটা একই ! বর্তমানে বৈষ্ণব বলতে এখানকার(বাংলা) লোকেরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বোঝে। এখন আবার এখানে নতুন সংযোজন Iscon -পন্থী বৈষ্ণব !তেমনই উত্তর ভারতের রামানুজ পন্থী এবং দক্ষিণে নিম্বার্ক বা মধ্বাচার্য্য পন্থীদের বোঝায়(শ্রী বা রামানুজিয়,মধ্ব,নিম্বার্ক,গৌড়িয়_বৈষ্ণবদের এই প্রধান চারটি পরম্পরা রয়েছে।)। এদের সবার মধ্যে আবার শালগ্রাম শিলাপূজার রীতি অতটা নেই। এরা রাধাকৃষ্ণ অথবা লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা শুধুই নারায়ণের মূর্তি পূজা করে। বৈদিক পঞ্চশাখায় যে বৈষ্ণবদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের ছিল শালগ্রাম শিলাপূজার বিধান। প্রাক-বৈদিক যুগ, বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ এইভাবে যদি সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করো_ তাহলে দেখবে উপাসনার রীতিতে প্রাক-বৈদিক যুগে ছিল অনন্ত বা অমূর্তের উপাসনা, বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ ও প্রতীক উপাসনা এবং পৌরাণিক যুগে প্রতিমা বা মূর্তি উপাসনা। অনন্তকে যখন সাধারণ মানুষ চিন্তার জগতে, ধ্যানের গভীরে ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারছিল না তখন তৎকালীন চিন্তাবিদরা প্রতীকের মাধ্যমে তাদের কাছে অনন্তের রহস্যকে ধারণা করতে শিখিয়েছিলেন। সেই অর্থে অনাদি শিবলিঙ্গ, ওঁকার বা শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি প্রতীকগুলি সেই অনন্তকেই বোঝানোর প্রয়াস! এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, শুধুমাত্র গণ্ডকী থেকে প্রাপ্ত ঐ শিলাকে বেছে নেওয়া হল কেন? উত্তরে বলা যায় – এটা ভক্তিভাব আনয়নের ব্যপার। হিমালয়ের পূণ্যভূমি থেকে উৎসারিত শুদ্ধ গণ্ডকী নদী-উৎসমুখ তৎকালীন দূর্গমতম অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। ফলে ঐ শিলা সংগ্রহ করতে হলে মানুষকে শুধু পাহাড়-পর্বত ভাঙার কষ্টই নয় – বাঘ-ভাল্লুকের হাত থেকেও রক্ষা পেতে হবে। ওখানে পৌঁছাতে গেলে অনেক তীর্থদর্শন, অনেক ত্যাগ, অনেক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, অর্থাৎ এককথায় একটা মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া শালিগ্রাম শিলা এক বিশেষ ধরনের নরম এবং চকচকে পাথর _এটি গড়িয়ে গড়িয়ে গোল বা ডিম্বাকৃতি আকার ধারণ করে-যা এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক হিসাবে বোঝাতেও সুবিধা হয়! এইসব চিন্তা করেই হয়ত তখনকার দিনে সমাজবিদরা বুড়িগণ্ডকের উৎসস্থলে প্রাপ্ত এ বিশেষ শিলাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।
এইসব কথা বললাম বলে মনে কোরনা আমি শালগ্রাম শিলাপূজার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলছি। তোমরা এখানে যারা রয়েছ তারা বেশিরভাগই যুবক আর তাদের মনোজগতে দেখছি এইসব ব্যাপারে interest কম, তাই কথাগুলো বললাম।
আর তোমরা যারা এইসবে বিশ্বাসী রয়েছো_ তাদের যেন আবার ভাব ছুটে না যায় ! যার যাতে বিশ্বাস - তাতেই ফললাভ হয়। কোন বিরোধ নেই। এখনকার ছেলেরা সবেতেই কারণ খোঁজে, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা চায় তাই আমাকে তাদের মত করে বলতে হয়। যারা শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণজ্ঞানে পূজা করে_ তারা ঐটার মধ্যে দিয়েই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করবে। আর যাদের শালগ্রাম শিলা ভাল লাগে না তারা স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করুক। স্বামীজীকে আদর্শ করে জীবনপথে এগিয়ে চললেই তাদের সব হবে। এটা স্বামীজীরই আশীর্বাদ যা সমস্ত যুবসমাজের উপর সবসময়ই রয়েছে।