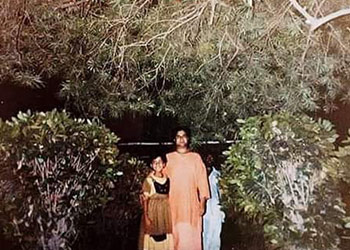স্থান ~ পরমানন্দ মিশন । সময় ~ ১৯৯৪-৯৫ সাল ৷ উপস্থিত ব্যক্তিগণ ~ কিছু বিদেশীভক্ত, নগেন, পঙ্কজবাবু, রবীন মালাকার ও আশ্রমস্থ ভক্তগণ ।
জিজ্ঞাসু :— হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা কেন?
গুরুমহারাজ :— কারণ ভারতবর্ষের বেশিরভাগ লোক হিন্দিভাষা ব্যবহার করে। তবে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হিসাবে যে হিন্দি রেডিও বা T.V-তে ব্যবহৃত হয় বা অল্প কিছু লোক কথা বলে — ওটা হিন্দিবলয়ে সর্বত্র চলে না। হিন্দিবলয়ে কমবেশি ৪০-৫০ ধরনের হিন্দির প্রচলন রয়েছে, এগুলি সবই ভুল হিন্দির অপভ্রংশ বা আঞ্চলিক হিন্দি। রেডিও টিভির হিন্দিটা “ঠাটি” হিন্দি। যাইহোক, রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হওয়ার পিছনে আর একটা কারণ হল — যেহেতু ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় দিল্লি ছিল ভারতের রাজধানী তাই ওখানকার ভাষায় কথা বলাটাই ছিল দস্তুর! তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় সব নেতারাই হিন্দি ভাষাতেই কথোপকথন এবং কাজকর্ম সারতেন! অন্যান্য রাজ্যের লোকেদের বা অন্যান্য ভাষা-ভাষী রাজনীতিকদেরও তাই হিন্দি ভাষা শিখে নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ! এসব কারণ ছাড়াও—পূর্ব এবং দক্ষিন ভারত ছাড়া বাকি প্রায় সব রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভাষাও ছিল হিন্দি অথবা হিন্দি ঘেঁষা কোন ভাষা!এইসব নানা কারণে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছিল।
ইংরেজরা যেহেতু কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত আগেই করেছিল, তাই ওরাও শেষের দিকে ভালোই হিন্দি শিখে নিয়েছিল। “হামি তুমকো গোলি করিয়া মারিবে” — হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে ইংরেজ সাহেবেরা এই ধরনের কথা বলতে পারতো।
আরও কারণ যদি জানতে চাও তাহলে বলতে হয় স্বাধীনতা পূর্ব ইতিহাস যদি ঘাঁটো তাহলে দেখবে যত movement-এর সূত্রপাত — তা এই বাংলা থেকে। যত আন্দোলন, নতুন চিন্তা, নতুন দিশা দেখাতো বাংলা। কিন্তু স্বাধীনতার Just পূর্ব মুহূর্তে বা বলা যায় আরও আগে থেকে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ, দিল্লিতে রাজধানী সরানো, নেতাজিকে অবমূল্যায়িত করার চেষ্টা, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় খানিকটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে বাংলা। এই সুযোগে হিন্দিবলয় বা উত্তরভারতের নেতৃবর্গ ভারতের রাজনীতিতে আসন পাকা করে নিয়েছিল। ফলে স্বাধীনতার পর যখনই এদের হাতে দিল্লির মসনদের ভার পড়ল তখন ওদের প্রস্তাব অনুযায়ী হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হলো না, কারণ তেমন কোন জোরালো প্রতিবাদই হলো না। তবে সেই সময়ে সবাই যে এটা মেনে নিয়েছিল তা যেন ভেবো না।ভারতবর্ষের পূর্ব আর দক্ষিণ অঞ্চল এটা মেনে নেয়নি। পরবর্তীকালে পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলি_এই ব্যাপারটাকে অনেকটা গা-সওয়া করে নিয়েছে কিন্তু দক্ষিণ এখনও পর্যন্ত মানতে গররাজি।
নেহেরু পারিবারিক সূত্রে 'ডোকরা' জাতির অন্তর্গত ছিল, ফলে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময় ডোকরিয়া (হিন্দির-ই এক কথ্য রূপ) -তে কথা বলত। মতিলাল, জহরলাল, ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত এই ভাষাই ব্যবহার করেছে। হিন্দির অনেক উপভাষা রয়েছে, এর মধ্যে ভোজপুরী, কুর্মালী, হিন্দুস্তানী, মৈথিলি, ছত্রিশগড়িয়া ইত্যাদি স্থানীয় ভাষাগুলিতে বহুসংখ্যক মানুষ কথা বলে। বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক বা দোহাতি হিন্দি শুনলে সাধারণ হিন্দির সঙ্গে ওইসবের কোন মিলই পাওয়া যায় না।তবে মনে কোরনা একমাত্র ভারতেই ভাষাবৈচিত্র্য রয়েছে ! একমাত্র চীন ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভাষার ভিন্নতা দেখা যায়। আর ভাষা সবসময়ই গতিশীল — কোন স্থানের ভাষা সবসময় একইরকম থাকে না — সংমিশ্রণ ঘটে। এইরকম এক ভাষার সঙ্গে একাধিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে গিয়ে হয়তো মূল ভাষাটিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। বহুদেশে বহু ভাষা এইরকম ভাবেই বদলে গেছে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে দুটো সংস্কৃতি প্রধান ছিল। একটা Aryan আর একটি Dravirian। স্থানবিশেষে এইজন্যই তোমরা শিল্প-সংস্কৃতি-ভাষা-লিপি ইত্যাদি সকল বিষয়েই আজও উভয় ধারার মৌলিক পার্থক্য দেখতে পাবে। যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকে বারবার এই দুই সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, ফলে উভয়েই উভয়ের শিল্প-সংস্কৃতিকে অনেকটাই গ্রহণ করে নিজের নিজের মৌলিকত্ব থেকে দূরে সরে এসেছে _তবু সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু আজও ভালোই চোখে পড়ে। প্রাচীন ভারতে আর্যদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। তবে তা আধুনিক সংস্কৃত নয় বৈদিক সংস্কৃত। পাণিনি সংস্কার করেছিলেন বলে বর্তমানে এর নাম হয়েছে সংস্কৃত। যাইহোক, ভারতের বর্তমান ভাষাসমূহে সংস্কৃতের প্রভাব সবচাইতে বেশি। লিপির বা উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটলেও যে মূল সংস্কৃত থেকে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার শব্দগুলি নেওয়া হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে যেটা বলছিলাম ভাষা যেন প্রবহমান নদীর মত। বহুকিছু এসে তাতে মেশে, বিভিন্ন ধারা মিশেই তো এক একটা বড় নদীর সৃষ্টি হয়। তেমনি মূল জননী কোন ভাষার সাথে যদি বিভিন্ন বিদেশী ভাষা বা সেই ভাষার শব্দরাজি মেশে তাহলে তা সমৃদ্ধ হয়। মূল সংস্কৃত তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে গিয়ে বিদেশি ভাষাকে নেয়নি বলেই dead language হয়ে গেছে, যেমনটা হয়েছে প্রাচীন ল্যাটিন বা গ্রীক ভাষাতেও। সে তুলনায় ইংরেজি নতুন ভাষা, শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষা গ্রহণযোগ্যতার জন্য অতিদ্রুত আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হয়ে গেল। ইংরেজি নতুন ভাষা বললাম কেন — তার কারণ ইংরেজদের ইতিহাসই বা ক বছরের — মাত্র কয়েক’শ বছর হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ওদের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন — ভারতবর্ষ যখন বিশ্বশান্তির যজ্ঞ করছে তখন ওদের পূর্বপুরুষরা বুনো ঘোড়া পোষ মানানোর চেষ্টা করছে। কেল্টিক, নর্মান, স্যাক্সন ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল আর জাতিটারও। প্রাচীন ল্যাটিন, গ্রীক শব্দও প্রচুর ঢুকেছে, তাছাড়া পরবর্তীতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ঔপনিবেশিকতার সময়ে যে কোন দেশের প্রচুর শব্দ ইংরেজির সঙ্গে মিশে ভাষাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। এই ভাবেই প্রবহমান নদী যেমন বিভিন্ন জলধারায় পুষ্ট হয় ভাষাও বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে পুষ্ট হয়ে ওঠে।
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও বহুকাল থেকে পারসিক, তুর্কী, গ্রীক, পাঠান, মোগলরা ভারতে এসেছে, এদেশের ভাষায় তাদের ভাষার প্রভাব পড়েছে। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ, স্পেনিয়ার্ড, ফরাসী, ইংরেজরা এসেছে — ইংরেজরা তো ১৫০-২০০ বছর রাজত্বই করে গেছে। ফলে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাংলাও বাদ যায়নি, বর্তমানে দেখা যায় বাংলার ৬০% শব্দ মূল সংস্কৃত থেকে নেওয়া আর বাকি ৪০% শব্দ বাইরের অর্থাৎ আরবি, ফার্সী, চীনা, পর্তুগীজ, ইংরেজি এইসব। উর্দু শব্দও প্রচুর রয়েছে — বিশেষত হিন্দি ভাষায়। উর্দু আবার কোন মৌলিক ভাষা নয় এটিও মিশ্র ভাষা। আরবি, ফার্সী, হিন্দি এসব মিলিয়ে একটা ভাষা, এটিকে বলা হত সেনা-ছাউনীর ভাষা। কারণ সেনা-ছাউনীতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকেরা থাকত, তাদের নিজেদের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে মোগল আমলে একটা মিশ্রভাষার সৃষ্টি হয় — এটাই উর্দু। পরবর্তীকালে মির্জা গালিব বা আরও কিছু সুফি সাধক উর্দু ভাষায় দোঁহা বা বিভিন্ন কবিতা লিখে ভাষাটিকে মর্যাদা দান করেছে।
যাইহোক, আমাদের কথা হচ্ছিল বাংলা ভাষা নিয়ে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছে যে, নেপালের রাজদরবার থেকে পাওয়া চর্যাপদ-ই প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন। এখন লিপি আকারে ঐগুলি যেহেতু পাওয়া গেছে, তাই মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয় ! ঐগুলি ছিল বৌদ্ধ সাধকদের গোপন তন্ত্রসাধনা, দেহসাধনা ইত্যাদির নথি। কিছু বর্ণনামূলক লেখা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সাংকেতিক ভাষায় বিভিন্ন তত্ত্ব লিপিত ছিল ওগুলিতে। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে বহু ওইরকম গ্রন্থ বা পুঁথি নেপালে বা তিব্বতের বিভিন্ন দুর্গম গুহায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তারই খানিকটা হয়তো নেপাল রাজা উদ্ধার করে রেখে দিয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যের যুগে বাংলা ভাষা অন্যরকম ছিল, তারপর এল বিদ্যাসাগরের যুগ। উনিই প্রথম বাংলা বর্ণমালা লিখে কিছু গ্রন্থ রচনা করলেন — বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও বিশেষ কোন বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেনি — বেশিরভাগ তৎসম-তদভব শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কোন বিদেশী নাম বা বিদেশী স্থান ছাড়া বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও প্রথমদিকে পূর্বসূরীদের প্রভাব ছিল। এসব লেখাগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্পদ হলেও সাধারণ আম-জনতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই বাংলা সাহিত্যে যখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগমন ঘটল তখন সাধারণ মানুষের আদরের ধন, নয়নের মণি হয়ে উঠলেন উনি। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, সাধারণ জীবনের আলেখ্য যখন কথ্যভাষায় পরিবেশন করলেন উনি তখন সেই লেখায় কোন শব্দ প্রয়োগ হয়েছে তা সাধুভাষা ও চলিতভাষা আর তাতে শব্দের প্রয়োগ দেশি না বিদেশি এই নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি মানুষ, আদরে গ্রহণ করেছিল যা আজও সমাদৃত।
এইভাবেই একভাষার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেলে ভাষা পুষ্ট হয়, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়। দ্যাখা গেছে বাংলাভাষা অন্যান্য ভাষাকে নিজের মধ্যে নিজের মতো করে ঢুকিয়ে নিতে পারে — এই লক্ষণটা খুব ভালো। তার মানে আগামী দিনে বাংলাভাষার উৎকর্ষতা আরও হবে, আর শুধু ভারতবর্ষ নয় হয়তো গোটা বিশ্বকেও এই ভাষা নিয়ে ভাবতে হবে। এমনিতেই বাংলাদেশ বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক সম্মান দান করেছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রসংঘে বা যে কোন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাভাষায় কথা বলে। পশ্চিমবাংলায় যতই মনীষী জন্মাক আর সাহিত্য রচনা হোক, বাংলাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করতে পারেনি, যেটা করেছে বাংলাদেশ। ভাষা-আন্দোলন করে ২১-শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবেও মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং ভাষার ব্যাপারে বিকৃত বাংলায় কথা বললেও বাংলাদেশ কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার চেয়ে এগিয়ে ৷জিজ্ঞাসু :– কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলি কি ?
গুরু মহারাজ :– ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যে কাজ বা কর্ম তাকেই ‘কাম’ বলা হয় ৷ শাস্ত্রে রয়েছে –
"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম"। – এখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা অর্থাৎ বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় কাজ৷ 'কাম'-কে আদি রিপু বা আদিম রিপু বলা হয়েছে। কারণ এখান থেকেই সৃষ্টি হয় বা এখান থেকেই অন্যান্য রিপুগুলি ক্রমানুযায়ী সৃষ্টি হয়। কাম অবদমিত হলে হয় ক্রোধ। কামবিকার অর্থাৎ কামবিকৃতি থেকেই ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ইত্যাদি রিপুগুলির উৎপত্তি, তাই আদিম রিপু কাম।অনিত্যের প্রতি আসক্তিই লােভ। নিত্য আর অনিত্য, যা আছে তার খোঁজ না করে যা বাস্তবে নেই বা মায়া (মনে হচ্ছে আছে কিন্তু নেই) তাতে আসক্ত হবার প্রবণতাই লােভ। অনিত্যের প্রতি এই আসক্তি থেকে মানবজীবনে আসে দুঃখ। তাই বলা হয় দুঃখের কারণ আসক্তি। মানুষ জানে অনিত্যের প্রতি আসক্তি থেকে দুঃখ আসে জীবনে তবু সে আকর্ষণে আসক্তি মুক্ত হওয়া যায় না তাই লােভ। ধনগর্ব, কুলগর্ব, যৌবনগর্ব এগুলিই অহঙ্কারের প্রকাশ আর এর প্রভাবে মদমত্ত হয়ে মানুষ অবিবেকী বা বিবেকহীন কর্মসকল করেথাকে, একে মদগর্বীতা বলে, তাই মদ এক রিপু। বাসনা মুঠিতে ভােগ্যবস্তুকে ধরতে যাওয়াই ‘মােহ’, আর এই মােহগর্তে আটকে গিয়ে কষ্ট পায় মানুষ। ভাবে সংসারই তাকে ধরে রেখেছে বা আটকে রেখেছে। মাৎসর্যরিপু-তাড়িত মানুষ যা নয় তাই হবার চেষ্টা করে, ঈর্ষাকাতরতা থেকে এটা আসে। ময়ূরপুচ্ছধারী কাক যেমন কখনই ময়ূর হয় না অযথা দুঃখ ভােগ করে, তেমনি মাৎসর্যরিপু-পীড়িতরা অযথা দুঃখ পায়। যােগীরা এই রহস্য জেনেছেন, তাই তাে তাদের সতর্কবাণী রয়েছে, “বনাে মৎ, বননে সে পিটাই হােগা।”
এবার কথা হচ্ছে এগুলি রিপু কেন ? কারণ এগুলি মানুষের জীবনে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বা শত্রু। মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। কিন্তু মায়া-মোহ-অজ্ঞানতার বেড়াজালে আটকে পড়ছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেমন উদীয়মান সূর্যকে দেখতে দেয় না তেমনি এগুলিও মানুষকে প্রকৃত স্বরূপকে জানতে দেয় না বাধা দেয়, তাই রিপু। কিন্তু কোন কোন মহাপুরুষ আবার বলেছেন যে, এরা তাে যাবার নয়, তাই এগুলির মােড় ঘুরিয়ে দিতে পারলেই এরা আর শত্রু থাকে না তখন বন্ধু হয়ে যায়। যেমন পরমাত্মার সঙ্গে আমার মিলন হােক—এই কামনা, আত্মসাক্ষাৎকার হবার পিছনে অন্তরায়গুলির প্রতি ক্রোধ, পরম স্থিতি বা পরমানন্দলাভের প্রতি লােভ, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার এই জীবনেই হবে, এই শরীরেই হবে– এই রােক্ বা অহঙ্কার, ভগবৎ নামে বা ভগবৎপ্রেমে মােহ। যেহেতু এই শরীরে ভগবৎ বিলাস হবে তাই তার যত্ন বা তাকে পরিষ্কার রাখা, সাজানাে গােছানাের প্রতি এই মােহকে ঘুরিয়ে দিলে তখন এগুলি আর শত্রু নয়, এগুলি অগ্রগতির সহায়, জীবনপথে মহান পাথেয় হয়ে উঠবে। সুতরাং দেখা গেল রিপুগণ থাকবেই কিন্তু তাদের সঠিক পথে channelise করতে হবে, তাহলেই তারা বন্ধু হবে। কিন্তু কি ভাবে করবে channelise? এরজন্য প্রয়ােজন সদ্গুরুর। তিনি ব্যক্তি বিশেষের লক্ষণ ও তার স্বভাব অনুযায়ী নির্ণয় করে ঠিক করে দেবেন—কার কি মন্ত্র, কার কি বিধান, কার কি খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সবকিছুই। এককথায় তার সমগ্র জীবনের ভার নিয়ে নেবেন সদগুরু–ইহকাল তথা পরকালের ভার। তাই গুরুই ভবের কাণ্ডারী, গুরুই হাত ধরে পার করে দেন ভবার্ণব। জীবের সাধ্য কি আপন শক্তিতে এই দুস্তর সাগর পার হয় !