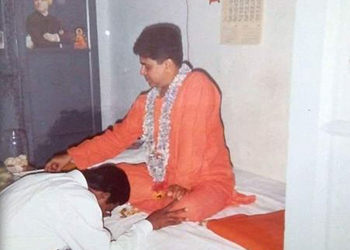জিজ্ঞাসু—ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ভারতে কোন এক সময় আর্য ও অনার্যের যুদ্ধ হয়েছিল এবং বিদেশী আর্যরা এদেশী অনার্যদের তাড়িয়ে দেশ দখল করে—এই ব্যাপারটি কতটা সত্য ?
গুরুমহারাজ—ঐতিহাসিকরা কি ঋষি নাকি, যে সঠিক তথ্য গুরুমহারাজ- দেবে ! একমাত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যথার্থ কালদ্রষ্টা। তাঁরা অতীতের গহ্বর থেকে সঠিক সত্যকে বের করে আনতে পারেন। আর ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকরা কি করেন—বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমান করেন। প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ বা প্রাচীন সাহিত্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, অনুমান করে বলেন যে, “এটা আনুমানিক এত হাজার বছরের পুরানো” অথবা “হয়তো এখানে এই রাজবংশ ছিল—সম্ভবত নিম্নলিখিত কারণে সেই বংশের পতন ঘটেছে।” এই কথা প্রসঙ্গে বলে ১০/১২টা কারণ উল্লেখ করে দিল। আবার পরবর্তীতে অন্য কোন পণ্ডিত এসে সেটার বিরোধ করে দু’একটা point কেটে দিল বা যোগ করে দিল। এইরকমই তো চলে।
ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে তৎকালীন সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি ও জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রুতি অর্থাৎ চারটি বেদ (উপনিষদ সহ), স্মৃতি অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিধি-বিধান নির্দেশ রয়েছে যে শাস্ত্র গুলিতে, আর পুরাণ বলতে বাছাই করা ১৮টি পুরাণকে একত্রে অষ্টাদশ পুরাণ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । এছাড়া রয়েছে রামায়ণ ও মহাভারত নামক দুটি মহাকাব্য। পুরাণগুলিতে সরাসরি বা রূপকাকারে বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন রাজবংশের আখ্যান, তৎকালীন সমাজজীবন ও ধর্মজীবনের বর্ণনা ও কথা, কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে। দুটি মহাকাব্য—দু’জন মহান পুরুষ ‘রাম’ ও কৃষ্ণ’-এর আখ্যান, এখানেও তৎকালীন বিভিন্ন রাজবংশ এবং সমাজজীবনের চিত্র পাওয়া যায়।
ভারতবর্ষের পুরাণগুলি এখনও সর্বজন স্বীকৃত ইতিহাস হিসাবে মর্যাদা পায়নি, তবু বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এগুলি থেকে প্রাচীন ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার —পৌরাণিক ঘটনা সমূহকে সত্য বলে প্রমাণও করছে। যেমন সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত দ্বারকানগরী যা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাবার কাহিনী রয়েছে, তার কিছু প্রমাণ মিলেছে। শ্রীলঙ্কা সরকার রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনার প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পেয়েছে—এমন দাবি করে। এমনকি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত লঙ্কানগরীর অবশেষ রয়েছে বলেও ওখানকার গবেষকরা আওয়াজ তুলেছে। যাইহোক পুরাণাদি শাস্ত্রগুলিকে যদি ইতিহাস হিসাবে ধরা হয় তো কোথাও এমন record নেই যে ভারতবর্ষে আর্যরা বাইরে থেকে এসে এখানকার অধিবাসী—যারা নাকি অনার্য তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের বনে-জঙ্গলে তাড়িয়ে দেশটা দখল করে নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বহু পূর্ব থেকেই বিন্ধ্যপর্বত ভারতবর্ষকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল—উত্তর দিকটি আর্যাবর্ত, দক্ষিণ দিকটি দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাবর্ত। দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতিকেই ভুল করে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা অনার্য বলে চিহ্নিত করেছে। ভুললে চলবে না ঐ সময় থেকেই বিন্ধ্যপর্বতের আশেপাশে গড়ে উঠেছিল আর একটি সংস্কৃতি, যার নাম ‘কোল সভ্যতা’। সুতরাং সুপ্রাচীন কাল থেকে আর্য সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা ও কোল সভ্যতাই ছিল ভারতবর্ষের সম্পদ। বহুকাল পর্যন্ত এই সভ্যতাগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য দিয়ে উন্নতিলাভ করেছিল এবং স্পষ্টও হয়েছিল। আর্যদের মহান অবদান ‘বেদ’ আর দ্রাবিড়দের উৎকর্ষতার সাক্ষী ‘তন্ত্র’। হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো ইত্যাদি সভ্যতা ছিল ‘কোল’-দের অবদান। বিন্ধ্যপর্বত তৎকালে এতই দুর্গম ছিল এবং মাঝখানে কোল-সাম্রাজ্য থাকায় আর্যাবর্তের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের যোগাযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে, কাজেই যুদ্ধ-বিগ্রহ করা তো দূর-অস্ত। মহামুনি অগস্ত্য তৎকালীন একজন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, তিনি প্রথম নিজস্ব প্রচেষ্টায় আর্যাবর্তের জ্ঞান নিয়ে দক্ষিণাবর্তে পৌঁছান এবং সেখানকার তন্ত্রাদিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিব্বতীয় মহাযোগী ‘সদাশিব’ বা ‘মহাদেব শিব’ দক্ষিণের তন্ত্র ও অন্যান্য সংস্কৃতিকে আর্যসম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সমস্ত বিষয়ের উপর অসাধারণ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম-বিচারধারাও সাধারণ মানুষের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয়তা তাঁর প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলেছিল ! তবু আর্যাবর্তের রাজা (প্রজাপিতা) দক্ষ তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি বলেই ‘দক্ষযজ্ঞ’ কাণ্ড বেধেছিল। এটাকেও যদি উভয় সংস্কৃতির মধ্যে যুদ্ধ বল, তাহলে যুযুধান দুই পক্ষই কিন্তু উত্তরের লোক। এইভাবে তখন থেকেই আর্যাবর্তে বেদ ও তন্ত্র দুটোই সমানভাবে আদৃত হয়ে আসছে আর সেই থেকে সদাশিব বা শিব হয়ে গেলেন দেবাদিদেব । তবে এমন কথিত রয়েছে যে, বেদসৃষ্টির বহু পূর্বেই তন্ত্র রচিত হয়।
এরপর রামায়ণের রাম-রাবণ বা রাম-বালীর যুদ্ধকে অনেকে আর্য-অনার্য যুদ্ধ বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু সেখানেও যুক্তি টেকে না। কেননা রামচন্দ্র কিন্তু অযোধ্যা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে কারও সাথে যুদ্ধ করতে যায়নি। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা এই তিনজনেই শুধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে কোন সেনাবাহিনী ছিল না। দণ্ডকারণ্যে গুহক চণ্ডালের সাথে রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয় সেখানে কোন যুদ্ধ বা ঝুটঝামেলা হয়নি। এইভাবে আর্যাবর্তের রাজপুত্র রাম কোলরাজের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এরপর কিস্কিন্ধাকাণ্ডে রামের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ’ল সেখানকার রাজকুমার বা রাজভ্রাতা সুগ্রীবের এবং তার সহকারীদের। যার মধ্যে অন্যতম হনুমান, জাম্বুবান ইত্যাদিরা। রাজা বালী সুগ্রীবের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্য রাম সুগ্রীবের সাহায্যে বালীকে হত্যা করলেন। কিন্তু দ্যাখো, এই ঘটনায় রাজ্যে কোন বিদ্রোহ হ’ল না। রাজাবদলকে শুধুমাত্র প্রজারাই নয়, বালীর পুত্র অঙ্গদ বা তার মা-(বালীর স্ত্রী)ও মেনে নিল। এমনকি অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হল এবং রামচন্দ্রকে ভগবান হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর হয়ে মরণপণ লড়াই করল। তাহলে কি করে বলবে যে, এটি ছিল আর্য-অনার্য যুদ্ধ বা এই ধরণের কিছু ?
এবার সুগ্রীবের সেনাবাহিনীর সহায়তায় লঙ্কা আক্রমণ বা রাবণবধ তো দ্রাবিড়দের সাথে রাক্ষসবাহিনীর লড়াই, আর্য-অনার্য theory খাটছে না তো ? আর রাবণকেই বা অনার্য বলার হিম্মৎ কার আছে ? যেমন বীর, তেমনি সুপণ্ডিত আর সম্পদে, প্রযুক্তিতে, সমর-সজ্জায় এত উন্নত যে, বাকিরা কোথায় লাগে ওর কাছে ! ওরই অস্ত্র ব্যবহার করে ওকে পরাজিত করতে হ’ল অন্যথায় রাবণের সাথে টক্কর দেওয়া যেতো কি ? রাবণের পুষ্পক রথ, মেঘনাদের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ—এসব কত উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ! তাই রাবণের দেশকে বর্বর, বুনো, অশিক্ষিত, অনার্য করার স্পর্ধা কোন ঐতিহাসিকের হবে না।
এইজন্যই বলছিলাম আর্য-অনার্য সংঘাত ইত্যাদি গল্প টেকে না। সদাশিবের পর থেকে দ্রাবিড় সংস্কৃতির বহু আচার-অনুষ্ঠান আর্যসংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়। একেই আর্যীকরণ বা আর্য-সমীকরণ বলা হয়। গণেশপূজা বা সন্তোষীমাতার পূজা এসেছে স্কন্দপুরাণ থেকে। আর পদ্মপুরাণ থেকে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য। মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঘটনাগুলি থেকেওঅনেকে আর্য-অনার্য গন্ধ পান। কিন্তু এগুলি সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সংস্কৃতি এবং তা থেকে শেষে উভয়ের মিলন। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগর উচ্চবর্ণের লোক, তিনি নিম্নবর্ণের লোকেদের পূজিতা দেবী মনসাকে মেনে নিতে পারছেন না। পরে বিভিন্ন ঘটনাচক্রে তাঁকে দেবী হিসাবে মেনে নিলেন। আর চণ্ডীমঙ্গলে দামোদর বা দামুন্যার অবহিকার জাতিদেরকে নিয়ে ঘটনা—বেশীরভাগ এরা সাঁওতাল, কোল বা শবর জাতির লোক। এদেরকে ব্যাধ বলা হয়েছে একটা ঘটনার নায়ক-নায়িকা ফুল্লরা কালকেতু। ওরা বনের পশু শিকার করে, তার মাংস ছাড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। ওদেরকে দেবী চণ্ডী (দুর্গার একটি রূপ) কৃপা করলেন, কালকেতু রাজা হ’ল ইত্যাদি। এই ঘটনাটি কিন্তু মনসামঙ্গলের উল্টো কাহিনী। এখানে উচ্চবর্ণের দেবী নিম্নবর্ণের কাছে গ্রহণযোগ্যা বা পূজিতা হলেন। এখনও ঐসব অঞ্চলের লোকেরা দামোদরকে গঙ্গার মতো পবিত্র বলে মানে।
এইভাবে ভারতবর্ষে কত মা ও বাবা বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন নামে পূজা পেয়ে চলেছে। পুরীর জগন্নাথ প্রকৃতপক্ষে শবর জাতির দেবতা। রামায়ণে শবর, তুর্বসু ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন মেক্সিকান দেবতার মূর্তির সাথে পুরীর জগন্নাথের মূর্তির মিল পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বৌদ্ধদের উপাসনাকেন্দ্র ও আরাধ্য হিসাবে ঐ মন্দির বা মূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথকে বিষ্ণু বা নারায়ণরূপে পূজা করা হয়। এও এক আর্যীকরণ।
সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘপূজা হয়, কালু রায়, বনবিবি এইসব ওখানকার দেবদেবী। এগুলি হিন্দু-মুসলিম ধর্ম সংস্কৃতির মিলন। সত্যনারায়ণ যেমন সত্যপীর হয়ে যায়—এও তেমনি। সুন্দরবন এলাকায় বনবিবি হচ্ছে বাঘেদের দেবী, আর দরিয়ার পাঁচপীর হিসাবে বিভিন্ন গাজীরা পূজিত হন, এঁরা সবাই ওখানকার স্থানীয় মৎস্যজীবী বা সাধারণ মানুষের দেবদেবী। ওখানে বসবাসকারীদের মধ্যে হিন্দু- মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই রয়েছে, সকলের আলাদা ধর্মাচরণও রয়েছে কিন্তু ঐ দেব-দেবীরা common । এসব থেকেই বোঝা যায় যে, ধর্মাচরণ ও দেব-দেবীকে মানুষই তার মতো করে নিয়েছে, ঈশ্বর কোন ধর্মমত করেনি। তবে মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর কথা যা হচ্ছিল তা পরবর্তীতে ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন নামে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে, পূজিত হয়ে আসছেন। চণ্ডীদেবীরও কত নাম ওলাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, সগড়াইচণ্ডী, ন্যাকরাইচণ্ডী ইত্যাদি নামে পূজিতা হয়ে আসছেন। আর মনসা–বিষহরি, জগদগৌরী ইত্যাদি নানা নামে পূজিতা হ’ন। এখন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষই এতে অংশগ্রহণ করেন। উচ্চ-নীচ বা আর্য-অনার্য এই নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না।
তিব্বতীরা আগে শৈব ছিল পরে বৌদ্ধপ্লাবনে ওরা বৌদ্ধ হয়ে গেল। এগুলো সবই আর্যীকরণ। আর্যজাতি-অনার্যজাতি আর তাদের সংঘাতের গল্প, ইংরেজদের সাজানো। যেহেতু ওরাও বাইরে থেকে এসে এদেশে রাজত্ব করছিল বলে ঐ ধরণের একটা গল্প চালিয়ে দিয়েছিল। যাইহোক তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ঢুকলেও ওখানকার সংস্কৃতি মিশ্র-সংস্কৃতি। কারণ তিব্বতীরা বুদ্ধমূর্তির নীচে নানান দেব-দেবীর মূর্তি রাখে, বুদ্ধের পূজায় বিভিন্ন পশু-পাখীর মাংস-ডিম পুজোর নৈবেদ্য হিসাবে দেয়, যেটা অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ আচারের সঙ্গে মেলে না।
তিব্বতী ধর্মগুরুদের লামা বলে। ওদের অনেকে সর্বদা তিব্বতী গরু বা ‘ইয়াক’-এর চিন্তা করে (ধ্যান) । ওদের ধারণা ভগবান বুদ্ধ ওদেরকে ‘ইয়াক’-বেশে দেখা দেবেন। তাই ‘ইয়াক’ চিন্তা করা মানেই ভগবান বুদ্ধ-চিন্তা। বহু পূর্বে একজন লামা তাঁর এক শিষ্যকে সর্বদা “ইয়াক” চিন্তা করতে বলে একটি গুহায় রেখে যান। ১২ বছর পর গুরুদেব ফিরে দেখেন শিষ্য সেখানেই বসে। বললেন “বেরিয়ে এস”। শিষ্য বলল শিং-এ আটকে যাবে যে ! গুরুদেব দেখলেন শিষ্যের পূর্ণতা এসে গেছে।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এই ধরণের indication দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে একাগ্রতা বা গভীরভাবে একই ভাবনার মধ্যে থাকলে স্থূলশরীরেরও পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনলে স্থূলেও পরিবর্তন ঘটতে পারে। তিনি হনুমান সাধনা করে দেখালেন যে তাঁর নিজের শরীরের pre-cocyx এক ইঞ্চি মত বেড়ে গিয়েছিল। যেহেতু তিনি লেজযুক্ত হনুমানের চিন্তা করেছিলেন তাই তাঁর এই লেজ বেরোনোর ঘটনা ঘটেছিল। পরে ভাবনার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর ঐ লেজটুকুও অবলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া নারীভাব বা রাধাভাবের সাধনের সময় তাঁর নারীদের মতো শরীরের অঙ্গাদির পরিবর্তন ঘটেছিল, এমনকি তাঁর প্রতিমাসে menstruation-ও হতো। ঠাকুরের শরীর নিয়ে এই যে research এটা হয়তো জীববিজ্ঞানীদের কাজে লাগবে, কারণ সূক্ষ্ম ভাবনার দ্বারা স্থূল শরীরের যে পরিবর্তন করা যায় তা কোন্ কোন্ শর্তে বা কিভাবে পরিবর্তন হয় তা তারা গবেষণা করে জানতে পারবে।
যাইহোক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া হচ্ছে। প্রকৃত প্রসঙ্গটা ছিল আর্যীকরণ নিয়ে। আশাকরি তোমরা ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারলে। ধারণা থেকেই ধ্যান হয়। তাই আগে ধারণা পাকা হওয়া প্রয়োজন।
জিজ্ঞাসু—নারী শরীর অপূর্ণ বলেই কি নারীশরীরে ভগবানের অবতরণ হয় না ?
গুরুমহারাজ—Semitic চিন্তাধারায় অর্থাৎ বিশেষত ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মমতে নারীশরীর অপূর্ণ বা পুরুষ শরীর থেকে নারী শরীরের সৃষ্টি এইরকম concept দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সনাতন ধর্মে এরূপ কোন কথা তো বলা নেই। জীবসকলকে ‘জীবাত্মা” বলা হয়েছে। আত্মায় তো লিঙ্গভেদ বা নারী-পুরুষ ভেদ নেই। Semitic দর্শনে রয়েছে যে, আদিমানব আদমের পাঁজর থেকে ‘ইভ’-কে সৃষ্টি করেছিল ঈশ্বর। তাই নারীর আত্মা নেই। গ্রীকদের আত্মা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা ছিল। ওদের আত্মার প্রতিশব্দ ‘আত্মস্’। এখান থেকেই ইংরাজীতে atmosphere শব্দটা এসেছে। অর্থাৎ আত্মার ব্যাপকত্ব বা সর্বব্যাপ্তি সম্বন্ধে ওদের একটা ধারণা ছিল। আবার একমতে আছে আত্মার কোন ওজন নেই অতএব এটি বস্তু নয়, এটি অবস্তু। আর প্রকৃতপক্ষে তো তাই-ই, আত্মা বস্তু নয়।
সে যাইহোক, ভারতীয় সনাতন ধর্মে নারীদের অনেক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মবেত্তা বা ব্রহ্মবাদিনী অনেক নারীরই বেদেরবিভিন্ন সূক্তের প্রবক্তা হিসাবে নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে দেবীসূক্তের প্রবক্তা হিসাবে পাওয়া যায় অস্তূণ কন্যা ‘বাক্’-এর নাম। ইনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিজের উপলব্ধ সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, নিজেকে শক্তি হিসাবে উপলব্ধি করেছেন। এছাড়া ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা-র নাম উল্লেখ রয়েছে বেদে। গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদিরাও ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। এরকম আরও অনেক নারীর উল্লেখ রয়েছে যাঁরা সেকালে নিজেদের গুণে সমাজে একটা মর্যাদার আসন তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন। বেদ পরবর্তী যুগে লীলাবতী বা খনা উল্লেখযোগ্য নারী ছিলেন। সুতরাং বোঝা গেল যে প্রকাশের ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষ ভেদ নেই। আত্মার কোন নারী-পুরুষ ভেদ নেই তবে জোর করে এসব কিছু করতে গিয়েই নানান বিকৃতি দেখা দিচ্ছে সমাজে যা একদমই কাম্য নয়। আত্মায় নারী-পুরুষ একই। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষ অপূর্ণতা থেকে পূর্ণত্বের দিকে এগিয়ে চলে। জন্মগ্রহণের সময় পূর্ব পূর্ব জন্মের অতৃপ্তি মেটাতে বা পূর্ব পূর্ব জন্মের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারটা মেটাতে গিয়ে কারও নারী শরীর, কারও পুরুষ শরীর হয়। কোন নারী শরীর যে কখনই পুরুষ শরীর লাভ করবে না এমন কোন কথা নেই। আবার পুরুষ শরীর চাওয়া-পাওয়ার অতৃপ্তি মেটাতে নারীশরীরও পেতে পারে। গানে রয়েছে “বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা”। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন জিনিসই নিত্য নয়, একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া। তাহলে নারী-পুরুষের শরীর কি করে নিত্য হতে পারে ? আজকাল তো operation করে ছেলে মেয়েতে পরিণত হচ্ছে বা উল্টোটাও হচ্ছে। তাহলে নারী বলেই সবসময় নারী অথবা পুরুষ মানেই সবসময় পুরুষ হবে এমনও কোন কথা নেই।
এবার তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছি–ভগবান কেন নারী শরীরে অবতরণ করে লীলাদি সংঘটিত করেন না বা নারী শরীরে তাঁর অবতরণ হওয়া সম্ভব কিনা ? হ্যাঁ, তা সম্ভব। বর্তমান যে পৃথিবীকে তোমরা দেখছ তার সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতি তো খুব প্রাচীন নয়। ইউরোপের ২০০০ বছরের বেশী পুরানো ইতিহাস নেই। এশিয়া মহাদেশের ২৫০০ বছরের, আফ্রিকা-আমেরিকার তো কয়েকশো বছরের ইতিহাস। তা এই স্বল্প জ্ঞানের পরিসরে মানুষ বিবর্তনের কতটুকুই বা জেনেছে ! বিজ্ঞানীরা বলছে যে, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে অন্তত ২০ লক্ষ বছর আগে, তাহলে বাকী দিনগুলোর ইতিহাস কি শুধু জঙ্গলে ঘোরা ও ফলমূল বা পশু-পাখি শিকার করে খাওয়া ? না তা নয়। আগেও এরকম সভ্যতা অনেকবার এসেছিল, আর তা ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় এক একটা মনুর রাজত্বকাল । এখন চতুর্দশ মনুর শাসন চলছে, এর আগে এইরকম সভ্যতা আরও অন্তত ১৩ বার এসেছে ও তা ধ্বংস হয়ে গেছে।
এখনকার সমাজ বিবর্তন যা দেখছ, এটি এখন পর্যন্ত পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় নারীদের দীর্ঘদিন ধরে সমাজে ইচ্ছা করে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হবে যে ইউরোপ, আমেরিকায় নারীরা স্বাধীন, তাদের অধিকার বেশী, কিন্তু ততটা নয়। সর্বত্রই লিখিত-অলিখিতভাবে পুরুষরাই প্রধান। ধর্মগ্রন্থগুলোও সেভাবে রচনা করা হয়েছে যাতে মানুষের মনে পুরুষের প্রাধান্যের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায়। এবার কথা হচ্ছে ভগবান যখন শরীর ধরে অবতরণ করেন—সে তো যুগ প্রয়োজনে। যুগোপযোগী শরীর নিয়ে জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদির নতুন বিন্যাস করে যান, ধর্ম-সংস্থাপন করেন। সুতরাং পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় তিনি বারবার পুরুষ শরীর ধরেই আসছেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ রূপে। যদি কখনো সমাজ ব্যবস্থা পাল্টায়, যদি দেখা যায় যুগ প্রয়োজনে নারী শরীরে এলেই মানবের মঙ্গল হবে, তাহলে তিনি নারী শরীরেই আসবেন। এখানে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তোমাদের চোখে নারী-পুরুষের যেমন ভেদ রয়েছে — ঈশ্বরের চোখে কি সেই একই প্রভেদ মনে করছ নাকি ? খেয়াল করে দেখবে যে কোন মানুষ ঈশ্বরকে বা যে কোন মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষকে, নিজের দৃষ্টি বা নিজের চেতনা দিয়ে বিচার করে। কিছুতেই বুঝতে চায় না যে, একটি ছোট ঘটি দিয়ে যেমন অনন্ত মহাসাগরের জল মাপা যায় না, তেমনি মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে অনন্ত মহিমাময়ের মহিমাকে কি করে মাপবে ?
যাইহোক এখনকার সমাজব্যবস্থার কথা হচ্ছিল। আমি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরি, ইউরোপের দেশগুলোতেও দেখেছি যে, বর্তমানে নারীরা কিন্তু এগিয়ে আসছে। এমনিতেই পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশী অন্তর্মুখী। তাই যে কোন সমাজব্যবস্থায় নারীরা যদি সুযোগ পায় তাহলে সর্বস্তরে তারা পুরুষদের চেয়ে তরতর করে এগিয়ে আসবে। ভারতবর্ষেই মেয়েরা সার্বিকভাবে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছে হয়তো ৬০/৬৫ বছর, প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও কম। কিন্তু এর মধ্যেই তারা সর্বস্তরে যেভাবে এগিয়ে আসছে, তাতে মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে তারা পড়াশুনার সমস্ত section-এ ছেলেদের সঙ্গে সমান টক্কর দেবে বা ছেলেদের থেকে এগিয়ে থাকবে। পশ্চিমের দেশগুলোতেও এই একই চিত্র। তাহলে দ্যাখা যাচ্ছে আগামী পৃথিবীতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন fields-এ নারীদের কর্তৃত্ব কায়েম হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এবার Spiritual field —এও নারীরা পুরুষের থেকে এগিয়ে। কারণ একজন নারী যত তাড়াতাড়ি মনকে concentrate করতে পারে—পুরুষ তা পারে না। অতএব বোঝাই যাচ্ছে ধ্যানের ক্ষেত্রে মেয়েদের সুবিধাই পুরুষের চেয়ে বেশী। এভাবে সমাজে নারীরা যখনই সর্বস্তরে এগিয়ে আসবে তখন দেখা যাবে ঈশ্বরের নারী শরীরেই অবতরণ হচ্ছে।
তবে সমাজে এখনও অনেকের ধারণা রয়েছে যে, পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ণ, পুরুষকে অবলম্বন করেই নারীর বিকাশ সম্ভব। এগুলি কিন্তু নারীকে অবদমিত করে রাখার জন্য পুরুষশাসিত সমাজনেতাদের কথা। কারণ ধারণাটা ভুল, প্রজনন ছাড়া একটা নারীর জীবনে পুরুষের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। জীবনের সমস্ত প্রয়োজন নারী নিজেই নিজে মিটিয়ে নিতে পারবে। একমাত্র যে সমস্ত নারীর সংসার-জীবনে আসক্তি রয়েছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা সন্তান কামনা রয়েছে তাদেরই পুরুষের সাহচর্য প্রয়োজন। কিন্তু যে সকল নারী এই জীবন চায় না, স্বাধীনভাবে মুক্ত হয়ে বাঁচার কথা ভাবে তাদের পুরুষের সাহচর্য কি প্রয়োজন ? হ্যাঁ, স্বাভাবিক নিয়মে পুরুষের গায়ের জোর বা সামর্থ্য নারীর চেয়ে বেশী তাতে কি হয়েছে ! এমন নারীও রয়েছে যে ৫টা পুরুষকে গায়ের জোরে হারাতে পারে। আমি ছোটবেলায় দেখেছিলাম সার্কাসে একটা মেয়ে বুকে পাটা লাগিয়ে একটা হাতির সমস্ত ওজনকে বহন করছে। যাইহোক কথা হচ্ছিল যে প্রজনন বা ঐ ধরণের ব্যাপার ছাড়া নারীর জীবনে পুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু পুরুষের জীবনে নারী অপরিহার্য, অবশ্য বিশুদ্ধ বাউল বা যোগীদের কথা বাদ দিয়ে বলছি। সাধারণ পুরুষরা যদি নারীর সাহচর্যে না থাকতো, তাহলে তারা কেউ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থেকে নোংরা, জবরজঙ্গ হয়ে থাকতো। এই যে দেখছ seating-এ সব বসে আছে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে, এদের জামা-কাপড় হয় মায়েরা কাচে না হয় স্ত্রীরা কাচে— পুরুষদের প্রায় কেউ কাচে না। আর যাদের স্ত্রী বা মা কাছে থাকছে না তারা জামা-কাপড় লণ্ডিতে দেয়, তাও ওনাদেরই জন্য, না হলে বাড়ীতে গালাগালি খাবে। একটা office-এর কোন section-এ যদি সবাই পুরুষ হয় তাহলে দেখবে লোকে সবদিন দাড়ি কাটে না, পোশাক সবদিন কাচে না, সবাই গম্ভীর মুখে থাকে। যেই না সেই section-এ একজন মহিলা-কৰ্মী এসে গেল, সে দেখতে যদি খুব ভালো নাও হয় তাহলেও দেখবে ঐ section-এর পুরুষ-কর্মীদের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে যাবে। পরের দিন থেকেই সবাই ফিটফাট্, পোশাকে ধোপদুরস্ত, ব্যবহারে অমায়িক, সবাই যেন হাসি হাসি মুখে কথা বলতে অভ্যস্ত —বিশেষত ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলার সময়। সবার টেবিলে কাগজ-পত্র, ফাইল এগুলি আর অগোছালো নয়—বেশ সুসজ্জিত ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজে পরিচ্ছন্নতা বা কাজে মন লাগানোর জন্য em- ployer-রা পুরুষদের এই psychology বুঝে এক একটা section-এ একজন বা দুজন female candidate রেখে দেন। তাই বলছিলাম —সাধারণভাবে পুরুষরা অগোছালো ও নোংরা। ঘরে ঘরণী না থাকলে ঘরগুলোর যে কি অবস্থা হয় সেটা বর্ণনা করা যাবে না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে যদি কোন অবিবাহিত পুরুষদের ‘মেস’ বা হোষ্টেলে যাও। ঘরে ঝাঁট পড়ে না, মাকড়সা, আরশোলা, টিকটিকির বাসা, ধুলোয়, আবর্জনায়, বিড়ি-সিগারেটের টুকরোয় তা ভর্তি। জামা- কাপড় যেখানে সেখানে এলোমেলো করে রাখা বেশীরভাগই না কাচা, ময়লা অবস্থায় ! যদি by chance সেখানে একটি মেয়ের যাতায়াত শুরু হয়—ব্যস্ অন্যচিত্র। সেই মেয়েটিই কোমরে কাপড় বেঁধে বাকী- দেরকে সঙ্গে নিয়ে জল ঢেলে ঘর ধুয়ে—জামা-কাপড়, বাক্স-প্যাঁটরা, বইপত্র গুছিয়ে সাজিয়ে ঘরের শ্রী ফিরিয়ে আনবে। বাসি জামা- কাপড় লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেবে অর্থাৎ এক কথায় সব নতুন করে সাজিয়ে দেবে। এইজন্যই নারীদের বলা হয় “ঘরের লক্ষ্মী” বা “ঘরণী”।
তোমরা পুরুষেরা যারা বসে বসে হাসছ ভেবো না যে তোমরা এর বাইরে আছ। আরে মেয়েরা না থাকলে তোমরা খিদে মেটাতে রান্না করতে ঠিকই, কিন্তু বাসনপত্র ঠিকমতো কখনই মাজতে না। তেল-কালি আর এঁটো শুকিয়ে সেসব বাসনপত্র ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার বাসা হয়ে থাকত। কেউ কেউ খাবার পর হাত ধোয়া বা মুখ ধোয়াও করত না। কুকুরে এসে চেঁটে চেঁটে হাত-মুখ পরিষ্কার করে দিত। হেসো না—আমি দু-একজনকে জানি যাদের স্ত্রীর অবর্তমানে এরকম দশা হয়। “শীতের সকালে মুখ ধোয়া কষ্ট, তার চেয়ে আপেল খেয়ে দাঁত পরিষ্কার করা ভালো” – আমাকে বলেছে একথা । দ্যাখো, আমার দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের কোন ভেদ নেই। সুতরাং ভেবো না যে, নারীর পক্ষ নিয়ে আমি কথাগুলো বলছি। যা সত্যি তাই বলছি। পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে strength আর নারীর সহজতা resistance। পাঁচজন ছেলে কোনস্থানে গল্প করলে দেখবে অবশ্যই সেখানে কোন নারীকে নিয়ে কথা হচ্ছে আর যদি পাঁচজন পুরুষের মধ্যে কথা হয় তবে হিরো-র গল্প হচ্ছে বা বক্তা নিজেই hero বা তার বাবা, কি তার কোন চেনা লোক কতটা ওস্তাদ, কি করতে পারে বা করেছে তার গাল-গল্প হচ্ছে, অর্থাৎ strength এসে যাচ্ছে। এটা শারীরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে কোন strength প্রদর্শন হতে পারে। তবে পাঁচটা young ছেলে এক জায়গায় থাকলে সাধারণত পাঁচকথার ফাঁকে মেয়েদের নিয়ে প্রসঙ্গ করে। আর পাঁচজন কমবয়সী মেয়ে এক জায়গায় থাকলে কোন না কোন ছেলে (পুরুষ) তা সে সিনেমার, উপন্যাসের বা পাড়ার যেখানকারই হোক না কেন—কোন hero-কে নিয়ে গল্প বেশী হয়। সেখানে আর একজন মেয়ে যোগ দিল প্রসঙ্গ পাল্টাবে না কিন্তু যেই একজন পুরুষ সেখানে গেল, তা সে যে বয়সীই হোক না কেন, দেখবে প্রথমেই মেয়েরা তাদের বসন ঠিকঠাক করে নিচ্ছে কথার প্রসঙ্গ পাল্টে দিচ্ছে—এটাই সহজাত resistance | পুরুষ জোর ক’রে—(strength), নারী বাধা দেয় (resistance) । পুরুষের জোরের কাছে যখন কোন নারীর resistance-এর বাঁধ ভেঙে যায় তখনই কোন নারী পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার আগে নয়। এটা দানবীয় ভাব—মানবীয় নয়। নারী যখন ভালোবেসে নিজেকে পুরুষের কাছে ধরা দেয়—সেটাই মানবীয়। এর ঊর্ধ্বে রয়েছে হর-গৌরী বা রাধা-কৃষ্ণ যেখানে সদা-সর্বদা পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরাই রয়েছে—strength-ও নেই, resistance-ও নেই।
আমার কাছে এলে পুরুষ তার strength হারায় আর নারী হারায় তার resistance। ফলে কোন পুরুষ আমার সাথে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারে। নারীও তাদের মনের কথা খুলে বলে। আমাকে এমন কথা অনেকে বলেছে – “এসব যা বললাম, একথা আমি আমার স্বামীকেও কখনও বলিনি।” নারীরা আমাকে তাদেরই একজন মনে করে, আবার পুরুষরাও ভাবে আমি তাদের একজন। Seating-এ বসার সময় আমি পুরুষ ও নারীদের আলাদা বসাই। কিন্তু দেখি জিজ্ঞাসা বেশী উঠে আসছে পুরুষদের দল থেকে। নারীদের চোখ দেখে বুঝতে পারি তারাও কিছু বলতে চায়—কিন্তু সামাজিকতা বজায় রাখতে গিয়ে অনেকে বলতে পারে না। তবে ঐ জিজ্ঞাসা ধরেই আমি তাদের মনের জিজ্ঞাসার সমাধান করে দিই। আমাকে কখনও একপেশে ভেবো না, আমি সকলকেই সম্মান দিই—তবে মেয়েরা বহুকাল থেকে সমাজে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, তাই নারীর দুঃখ-কষ্ট বা চোখের জল আমাকে বেশী ব্যথিত বা বিচলিত করে। নারীর চোখের জল আমার সহ্য হয় না—মনে হয় এখনই এর প্রতিবিধান করি। কিন্তু আমাকে সবচাইতে বিচলিত করে ভক্তের চোখের জল। এর চাইতেও বিচলিত করার জিনিস রয়েছে কি বলতো ? ভক্তের হৃদয় নিংড়ানো বেদনা। তাতে চোখের জল থাকে না হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়। তবে এসকলের ঊর্ধ্বে এখন আমাকে সহজেই বিচলিত করে আমার গর্ভধারিণী জননীর যে কোন ভাবনা।