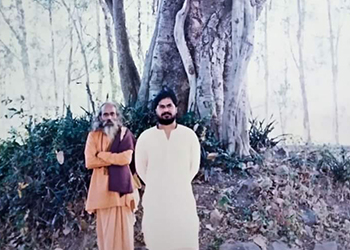জিজ্ঞাসু –ধর্ম কি ? ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা কি এক ?
গুরুমহারাজ—যা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রেখেছে —তাই ধর্ম—এটা সামগ্রিক অর্থে। আর individual-কে যা ধরে রেখেছে তাই individual-এর ধর্ম। Individual অর্থে জীব, জড় সবকিছুই হতে পারে, যেমন জলের ধর্ম সিক্ততা, আগুনের ধর্ম উত্তাপ, সেইরকম মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। মানুষের কোন আচার বা আচরণ যদি মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতো হয় বা যথার্থ সমাজের প্রতিকূল হয়, তখন বলা যায় ব্যক্তিটি অধার্মিক, সে তার যথার্থ ধর্ম পালন করছে না। আর আধ্যাত্মিকতা কি জানো তো – Art of Life, Art of Living অর্থাৎ বাঁচার কলা বা জীবনের কলা বা কৌশল, এটাকেই যথার্থ ধর্মাচরণ বলতে পারো। তোমার কোন আচরণ যদি অপরকে আঘাত দেয়, অপরের জীবনযাত্রার পরিপন্থী হয়, অপরকে ক্ষুণ্ণ করে তাহলে তার মধ্যে আর মনুষ্যত্ব থাকল না। প্রতিটি মানুষকে এইকথাটা মনে রাখতেই হবে যে, ধর্মের জন্য মানুষ নয়—মানুষেরজন্য ধর্ম। যেমন খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়—বাঁচার জন্য খাওয়া। তাই ধর্মের নামে বা ধর্মাচরণের নামে মানুষ হয়ে মানুষকে বুকে ছুরি মারা বা ঘরে অগ্নিসংযোগ করা—এগুলো মানুষের কাজ নয়, এগুলি অমানবিক। এরা কোন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ নয়—এরা অমানুষ।
দ্যাখো প্রকৃতপক্ষে insecurity-র feelings-ই মানুষকে অভিব্যক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রাণময় ও অন্নময় কোষের ক্রিয়ায় প্রথম সৃষ্ট জীবের যে অপূর্ণতা ছিল, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হ’তে হ’তে মানুষে এসে পূর্ণত্বলাভের উদ্দেশে মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে তা ক্রিয়াশীল হ’ল। কিন্তু এটাও শেষ নয় তাই মননশীল মানব পূর্ণত্বের সন্ধানে, পূর্ণত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে আনন্দময় কোষের উন্মেষের অপেক্ষায়। বাউলগানে আছে—‘আমি কোথায় পাবো তারে—আমার মনের মানুষ যেরে !” এই অন্বেষণ—এই সাধনা ৷ মানুষের আনন্দময় কোষ সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল হলেই মানুষ যথার্থ ধার্মিক হয়, মানুষ secured হয়। শাস্ত্রে বলেছে ‘পঞ্চকোশাঃ বিবেকভেদাঃ।”
ধর্ম সবকিছুকে ধরে রেখেছে—আমরা সকলেই ধর্মের আশ্রয়েই রয়েছি। তবু যারা মুখে বলছে, “আমরা ধর্ম মানিনা” এরা ভ্রান্ত অথবা মূর্খ বা আহাম্মক। জীবন এক যাত্রা—এই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে মানুষ তো সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে—কত রকমের ভয়, তারমধ্যে প্রধান মৃত্যুভয়। একমাত্র ধর্মকে আশ্রয় করলে, মানুষ ‘অভয়’ হয়। তবে কথা হচ্ছে—ধর্ম তো রয়েছেই, – একে আবার ‘আশ্রয় করা’ ব্যাপারটা কি ! এর অর্থ এটাই নিজ নিজ স্বভাবের অনুকূলে কাজ করা। এই অনুকূলে চলতে চলতে একদিন ঠিক সে তার গন্তব্যস্থলেপৌঁছবেই পৌঁছবে, অর্থাৎ অপূর্ণতা আর অজ্ঞানতা থেকে পূর্ণত্বে পৌঁছে যাবে। যা লাভের জন্য ৮৪ লক্ষ যোনি অতিক্রম করে এখানে আসা এবং আবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফাঁসা, তার অবসান ঘটবে।
জিজ্ঞাসু—দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনটি আগে আর কোনটি পরে এসেছে ?
গুরুমহারাজ—আগে পরে বলে কিছুই নেই। সবকিছুই একসাথে এসেছে, তোমার কাছে যখন যেটা আগে আসছে তুমি ভাবছ এটা আগে, ওটা পরে—ব্যাপারটা ঐরকম। সবকিছুই তো বিজ্ঞান। বিশেষভাবে জানাই তো বিজ্ঞান। তাহলে যে কোন ব্যাপারে তোমার যে জ্ঞানলাভ তা বিজ্ঞানেরই অবদান। সাধারণত দেখা যায় বিজ্ঞান পাঠের তিনটি stage রয়েছে। Hypothesis বা theory, observation এবং implementation । পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের মতো আরো রয়েছে মনোবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, যোগবিজ্ঞান। এমনই ধর্মবিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। ধর্মবিজ্ঞানে theory হচ্ছে philoso- phy, observation 2005 yoga, implementation 2 realization | সুতরাং philosophy বা দর্শন হচ্ছে ধর্মবিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের একটা part, first part. আর তুমি হয়তো physical science বা পদার্থবিজ্ঞানের সাথে philosophy-র তুলনা করছ। এটা ভুল ! Physics, chemistry এগুলো জড় বস্তু নিয়ে গবেষণা করে, life- science বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গবেষণা করে, আর অধ্যাত্মবিজ্ঞান এসবকিছুর সমন্বয় বা প্রকৃত ঐক্য নিয়ে গবেষণা করে। কোন কিছুর মধ্যেই বিরোধ নেই বৈচিত্র্য রয়েছে। সেই এক থেকেই যদিসবকিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে বিরোধ কি করে হয় ? সংস্কৃতে ‘দ্বন্দ্ব’-শব্দটির দুটি অর্থ ‘বিরোধ’ আবার ‘মিলন’ । এইটি বুঝতে হবে, এইজন্যই বললাম বৈচিত্র্য রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে ঐক্যও রয়েছে। জ্ঞানীরা এটা জানেন বলেই তাঁদের কোন ব্যাপারেই কোন হেলদোল নেই। মহানযোগী তৈলঙ্গস্বামী যখন শরীরে ছিলেন (প্রায় পৌনে তিনশো বছর ধরে ) তখন কি সমাজে দুর্নীতি, অপকর্ম ছিল না ? বৃটিশরা ভারতীয়দের উপর নির্যাতন করেনি ? তিনি কি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন না তাঁর যোগশক্তি, যোগবিভূতি প্রয়োগ করে তাদের সর্বনাশ করেছিলেন ? তিনি যেমন, তেমনি ছিলেন। অবতারকল্প মহাপুরুষরা অবশ্য সমাজের ঊর্ধ্বগতির জন্য কিছু কাজ করেন তাঁদের কথা আলাদা ! তাঁরা বিশেষ কাজ নিয়েই আসেন, ফলে সেটা সম্পাদন হলেই চলে যান। আবার অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁরা কোন সঙ্কল্প করে শরীরধারণ করেন, তাঁদের দ্বারাও সঙ্কল্প-সিদ্ধি হয় অর্থাৎ যে ব্রত নিয়ে তিনি এসেছেন সেই মঙ্গল কাজটি সিদ্ধ হয়। বিভিন্ন দেশপ্রেমিক বা সমাজ-সংস্কারক এইধরণের যোগসিদ্ধ জানবে। সাধারণ মানুষ আর সমাজের কাজ কতটুকু করতে পারে ? তাদের সে সামর্থ্য কোথায়! সমাজের ভালো বা ক্ষতি করতে গেলে তো সামর্থ্যের দরকার ! আর সাধনা ছাড়া সামর্থ্য আসে নাকি ? তাই সাধনা বা যোগমার্গ অবলম্বন না করলে মানুষের সামর্থ্য আসে না, আর সামর্থ্য না এলে তার দ্বারা কখনই কোন বড় কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই তোমরা যারা একথাগুলি বুঝছ, সাধনমার্গ অবলম্বন কর, যোগমার্গ অবলম্বন কর, সামর্থ্য অর্জন কর, তবে তো সমাজ ও মানুষের জন্য কিছু করতে পারবে !
জিজ্ঞাসু—অনেকে বলে ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়া ঠিক নয়, এ ব্যাপারে আপনি কি উপদেশ দেন ?
গুরুমহারাজ—দ্যাখ প্রথম কথা আমি কাউকেই উপদেশ দিই না, আমি জিজ্ঞাসার উত্তর দিই। তুই যদি উপদেশ লাভ করতে চাস –তাহলে কোন পাঠশালার গুরুমশায়ের কাছে যা। আর যদি তোর জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে চুপ করে বসে বসে শোন্। আচ্ছা, আমি যদি তোকেই জিজ্ঞাসা করি—এব্যাপারে তোর মত কি, তুই কি বলবি ? কিছু বলবি না, তাহলে শোন, দ্যাখ—যে ভিখারিকে ভিক্ষা দেয়, অতশত চিন্তা করে দেয় না, সহজভাবেই দেয়। আর যারা কোন needy person বা ভিখারিকে কখনো কিছু দেয় না, তারাই এইসব ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তোলে। খোঁজ নিয়ে দেখবি —যে তোকে এই কথাগুলো বলেছে সে নিশ্চয়ই খুবই স্বার্থপর এবং পারতপক্ষে সে কোনদিন কোন needy person-কে সাহায্য করে না। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরণের কৃপণ বা স্বার্থপররা কিন্তু প্রতারিত হয়। কাদের দ্বারা জানিস তো—কোন না কোন মাদুলীবাবা, হস্তরেখা বিশারদ, তন্ত্র-মন্ত্র জানা ব্যক্তিদের দ্বারা। এদের পিছনে ওরা গুচ্ছের অর্থ ঢালতে কসুর করবে না কিন্তু ৫ টাকা কি ১০ টাকা কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য কেনার জন্য দেবে না।
মানুষ কেন ‘মানুষ’ বলতো, অর্থাৎ অন্যান্য জীবসকলের চাইতে সে উন্নত কিসে ? না তার মধ্যে মানবিক গুণসমূহ রয়েছে, যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি, শুভকামনাইত্যাদি। এর উল্টোগুলো যার মধ্যে রয়েছে তার মানবশরীর হলেও সে দানব বা অসুর। তার অবগুণগুলি হ’ল–হিংসা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, ক্রুরতা, শঠতা, নীচতা ইত্যাদি। সুতরাং মানুষের চরিত্রের সদগুণের একটি দয়া-দাক্ষিণ্য বা ‘দান’। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ‘দয়া’ শব্দটির পরিবর্তে বললেন ‘সেবা’। এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট। দয়া বা দানে যেন একটু অহং ভাব আসে আর এ থেকেই ব্যক্তি আদর্শচ্যুত হতে পারে। কিন্তু সেবায় কোন অহংকার নেই। মা যেমন সন্তানের প্রতি অকৃপণ স্নেহশীলা হন, সেখানে যেমন মমত্ব থাকে কিন্তু অহংকারের কোন স্থান থাকে না, তেমনি প্রকৃত সেবাও নিঃস্বার্থ ও নিষ্কলুষ হয়। এরূপ সেবাকর্মে কোন কর্মবন্ধন তো হয়ই না বরং প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়।
তবে অবশ্যই আমি বলব – –কিছু না দেবার থেকে কিছু দেওয়া ভালো। সেই সাধুর গল্পে রয়েছে—একটি বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেলে বাড়ীর গৃহিণী বলেন, “তোকে ছাই দেবো।” সাধুটি সন্তুষ্টচিত্তে বলেন, “তাই দাও মা ! এই ছাই মুটি দিয়েই তোমার দেবার অভ্যাসটা শুরু হোক্ !” সুতরাং দেখা যাচ্ছে দান বা দেবার অভ্যাসটাও মানুষের একটা সদ্গুণ। আর এতে অহংকার নাশ হয়। দ্যাখো, অহংকার তো সহজে যাবার নয়। ফলে যশোলিসার জন্যও যদি কেউ দুঃস্থকে দান করে, অন্নহীনে অন্নদান করে, গৃহহীনকে আশ্রয়- দান করে, শীতার্তকে কম্বলদান করে, অভাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সরঞ্জাম দান করে তাহলে তারও মঙ্গল, সমাজেরও মঙ্গল হয়। শাস্ত্রে রয়েছে দানের ফল স্বর্গবাস। ফলে বুঝতেই পারছ দানের যে ফল তা জমা টাকার মতো ফুরিয়ে গেলে যে কে সেই। তাই দান বা দয়ার ভাবকে সেবার ভাবে উন্নীত করতে হবে। প্রকৃত সেবক হয়ে ওঠো, তাহলেই অধ্যাত্মরাজ্যের রহস্য তোমার কাছে উন্মোচিত হয়ে যাবে।
জিজ্ঞাসু—খাদ্যাভ্যাস পাল্টালে অর্থাৎ নিরামিষ জাতীয় খাবার খেলে কি ‘অহং’ নাশ হয় ?
গুরুমহারাজ—কই আর তা হয় বাবা! নিরামিষ আহার- কারীদেরও যথেষ্ট অহংকার রয়েছে, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, শঠতা, নীচতা এসবই রয়েছে। মীরাবাঈ অবশ্য অহংনাশ-এর কথা বলেননি কিন্তু ‘হরি’ পাওয়ার কথা বলেছিলেন, তৃণ (নিরামিষ) খেলে যদি হরি মিলত তাহলে গরু-মহিষ এরাই তা পেত, আর গঙ্গাস্নান করলে যদি হরি মিলত তাহলে জলের মাছ, ব্যাঙ এরাই তো মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হ’ত। কিন্তু এরকমটা হয় কি–হয় না। আমি তোমাদের বলছি—কি ঢুকছে তা বড় কথা নয়—কি বেরুচ্ছে সেটাই বড় কথা ? অর্থাৎ imput যা খুশি হোক—output ভালো হোক। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—নিরামিষ আহার করে কাম-কাঞ্চনে মতি রাখার থেকে গরু-শুয়োর খেয়ে যদি কারও ধর্মে মতি হয় সে-ই ধন্য।
তবে আহার পরিবর্তনে যে একদম কিছু কাজ হয় না, তা নয়, কিছুটা সাহায্য হয় বই কি ? তামসিক বা রাজসিক আহার অপেক্ষা নিরামিষ আহার (যদি শুদ্ধভাবে রান্না হয় তাহলে তা সাত্ত্বিক, ) বা সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে সত্ত্বগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়াটাও স্বাভাবিক। তবে শুধু আহারের কথা তো শাস্ত্র বলেনি, বলেছে আহার-বিহারেরপরিবর্তন। অর্থাৎ food habit and life-style, শুধু খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন নয় জীবন-যাত্রারও পরিবর্তন করতে হবে। Life-style- এ harmony আনতে হবে। জীবনের ছন্দ বা জীবনপথে চলার ছন্দ যদি মহাবিশ্ব প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে tune হয়ে যায় তাহলেই তোমার প্রকৃতি পরিবর্তন হবে। চেতনার উত্তরণ আর স্বভাবের উৎকর্ষ —এটাই আধ্যাত্মিকতা। একটা কথা আছে “স্বভাব যায় না মলে”। কথাটা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, জীবের স্বভাব একটা দারুণ শক্তিশালী ব্যাপার। কুল-মান, শিক্ষা-দীক্ষা, ধন বা পদ (post) এইরকম নানান কিছু পেয়েও মানুষ তার স্বভাব বদলাতে পারছে না। মানুষের বয়স পরিবর্তন হচ্ছে, অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে, স্থান পরিবর্তন হচ্ছে, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হচ্ছে, হয়তো আরও অনেক কিছু পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু বদলাচ্ছে না স্বভাব।
এবার যদি সাধন-ভজন ও মহাপুরুষ সংসর্গের দ্বারা কারও স্বভাব বদলে যায়, তাহলে সবই বদলে গেল, “এই জনমে ঘটালে কত জন্ম-জন্মান্তর । রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে গেল শুধু মাত্র স্বভাবের পরিবর্তনে। তাই বাহ্যিক পরিবর্তন যতই নিয়ে আস, তাতে কি হবে ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর পড়ে থাকে ভাগাড়ের দিকে অর্থাৎ মানুষের স্বভাব যদি না বদলায় সেই মানুষ যতই শিক্ষিত হোক বা ধনী হোক বা পদমর্যাদা পাক, তবুও সেই ব্যক্তি পূর্বের চেতনাতেই রয়ে যায়, চেতনার কোন উত্তরণ হয় না। আর চেতনার উত্তরণ না হলে পরবর্তী জন্মে আবার তাকে ঐ চেতনা থেকেই শুরু করতে হয়। তাই বদলাতে যদি কিছু চাও, তাহলে স্বভাব বদলাও, তাহলেই চেতনার উত্তরণ হবে, মানুষ দেবতা হবে, দেবতা ঋষি হবে আর এটাই উপনিষদের “চরৈবেতি”।
জিজ্ঞাসু—বস্তুবাদী বা Rationalist যারা, তারা বলে ধর্ম, অধ্যাত্ম এসব ভাববাদীদের মত, এগুলি অলীক ।
গুরুমহারাজ—তা বলতে পারে। নানা মুনির, নানা মত। তুইও কিছু মতামত দিয়ে দিতে পারিস, যদি গ্রহণযোগ্য হয়, কিছু মানুষ তোরও ভক্ত হয়ে যাবে—তৈরী হবে আর একটা নতুনবাদ। কিন্তু দ্যাখ এই যে বললি বস্তুবাদ, ভাববাদ—এগুলি সবই তো বাদ বা ism। কখনও কোন ‘বাদ’ দিয়ে কি সমস্যার সমাধান হয় ! ‘বাদ’ থেকে বিবাদ উপস্থিত হয় আবার নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই যে তুই বললি বস্তুবাদ, বস্তু থেকে এসেছে ‘বাস্তব’। তুই বল তো বাস্তবের সংজ্ঞা কি ? পারবি না তো—“বস্তুত যাহা আছে, তাই বাস্তব”। এবার বলতো—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ‘বস্তুত কি আছে ?” যদি বলিস এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আছে। কিন্তু এই বিরাটের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তো অনেক কিছুর সমষ্টি। সেগুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু দিয়ে সৃষ্টি। প্রতিটি পরমাণু আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নিয়ে গঠিত। এই কণা বা Particle-গুলি আবার sub-particle, কোয়ার্ক ইত্যাদিতে ভাঙা যাচ্ছে। তাহলে যা দেখছি বা ভাবছি এগুলো তো ঠিক ঠিক নয় তাহলে বস্তুর মূল কি ? ঠিক ঠিক কি আছে ? এটাই এখন বর্তমান বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা – What is reality ? পদার্থবিজ্ঞানের একটা শাখা particle-physics বা particle dynamics এই নিয়ে গবেষণা করছে। এখানে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও reality-র সন্ধান পায়নি। পেয়েছিলেন ঋষিরা, আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে। তাঁরা ঘোষণা করলেন, “ব্রহ্ম এক দ্বিতীয় বলে কিছু নেই”। ব্ৰহ্মই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু। ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ ‘প্রণব’, একে নাদব্রহ্ম বলা হয়। ইংরাজীতে এর প্রতিশব্দ হবে ‘Eternal Tune’, এই ‘প্রণব’ থেকেই এই বিশ্ব-সংসারের যাবতীয় বস্তুর প্রকাশ ঘটেছে, আর তা ঘটেছে ঐ tune-এর সৃষ্ট vibration- এর তারতম্য অনুযায়ী। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই একটি নির্দিষ্ট vibration-র দ্বারা সৃষ্ট, তাদের স্থিতিকালও একটা নির্দিষ্ট vi- bration-এ ঘটে চলেছে, আবার যে কোন বস্তুর বিনাশেরও একটি নির্দিষ্ট vibration রয়েছে। আর বস্তুর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তার vibration ঐ মূল vibration-এর সাথে মিশে যায়। বেদে একে বলা হয়েছে স্পন্দতত্ত্ব, vibration সংস্কৃতে স্পন্দন, তাই ইংরাজীতে বলা যায় vibration theory ৷
তাহলে কিবুঝলি—? Rationalist বলে কেউ নিজেকে জাহির করলো—আর তুই তার কথা মেনে নিলি ! Rationalist মানে যুক্তিবাদী, কি যুক্তি আছে তাদের ? এই তো বেদের তত্ত্ব বললাম, এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেবে ? তুই যদি ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে দু-চারটি খিস্তি-খেউড় দিয়ে গালাগালি দিস বা বিশ্রী কটু কথা বলে দিস তাহলে দেখবি সে আর যুক্তিবাদী থাকবে না। হয় ভীষণ রেগে গিয়ে তোকে আক্রমণ করবে আর দুর্বল হলে সেখান থেকে উঠে পালাবে। তাহলে যুক্তিবাদী আর থাকল কই ? ওসব অনেক দেখেছি—বুঝলি ! বস্তুবাদ এসব article লেখায় কিংবা বক্তৃতায় চলে, gossiping-এ চলে, কিন্তু practical ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না। একটু আগে কথা হচ্ছিল ‘ভিক্ষা দেওয়া’ নিয়ে। কার্লমার্কস তার বই-এ লিখেছিল ভিখারিকে ভিক্ষা দিলে তার ওটাই অভ্যাস হয়ে যায়, ফলে সে আর খেটে খেতে চাইবে না সুতরাং ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। এই কথার প্রেক্ষিতে অনেকে ভিক্ষা দেয় না বা ঐ ধরণের কথা বলে। কিন্তু কথা হচ্ছে সামর্থ্য থাকতে, অর্থ থাকতে, উপায় থাকতে কে চায় বলতো চেয়ে-মেগে খেতে ? সাধারণত অভাবেই মানুষ ভিখারি হয়, স্বভাবে ভিখারি খুবই কম, percentage-ই আসবে না।
তাছাড়া বেশীর ভাগ মানুষের স্বাভিমান বোধ রয়েছে, আত্মমর্যাদা চায়, এদের সকলেই চায় যে, সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে খেটে-খুটে রোজগার করে স্বাধীনভাবে বাঁচবে, মাথা উঁচু করে চলবে। কিন্তু শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানান প্রতিবন্ধকতায় হয়তো কেউ কেউ পেরে ওঠে না, তাকে মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে হয়। এদের করুণা করো, এদের প্রতি স্নেহশীল বা শ্রদ্ধাশীল হও—কখনও ঘৃণা করো না, অমর্যাদা করো না, আর তা করলে এটা নিজেরই অমর্যাদা, মানবজাতির অমর্যাদা। পৃথিবীর সবদেশেই ভিখারি রয়েছে, ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতেও ভিখারি, চোর, পকেটমার, কেপমার সবই রয়েছে।
‘গ্লাসনস্ত’, ‘পেরেস্ত্রৈকা’-র আগে যখন আমি রাশিয়ার, মস্কো বিমানবন্দরে বা তার বাইরে ঘুরছি, তখনও ভিখারি দেখেছি। আমি রাশিয়ায়, যুগোশ্লাভিয়ায় ভিখারিকে ভিক্ষাও দিয়েছি—দুটোই তখনও communist country ছিল। তবে ইউরোপের ভিখারিরা আমাদের এখানকার মতো থালা নিয়ে বসে থাকে না। ওদের ভিক্ষা চাওয়ার পদ্ধতিটা ভিন্ন। বুকে-পিঠে ব্যানার লাগিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে অথবা ঘুরে বেড়ায়। ‘পয়সা দাও’ বলে চ্যাচায় না। কদাচিৎ কারুকে approach করে। এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় প্রধানত ভারতীয় উপমহাদেশে ভিখারি একটা সমস্যা। এখানে সুস্থদেহী যুবক, কিশোর বা মহিলারাও ভিক্ষা করে। তবে আমি বলবো এটা সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি, রাজনীতি আর রাজনৈতিক নেতাদের ত্রুটি। যে দেশে সুস্থদেহী যুবক কাজের অভাবে পেটের দায়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে, চুরি-চামারি করে, সেটা সেই দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মানব তো সম্পদ ! ভারতবর্ষে মানব-সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকও রয়েছে। তারা কাজটা কি করে কেউ জানতে পারে না। মানব যদি সম্পদ হয়, তাহলে শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা শেষ্ঠ সম্পদ ! তাদেরই এই হাল ! সত্যই কি বিচিত্র ভারতবর্ষ !
জিজ্ঞাসু—আপনি ইউরোপে গিয়েছিলেন, ওখানকার ডেয়ারি-শিল্প নাকি খুবই উন্নত, বিশেষত হল্যাণ্ডে ?
গুরুমহারাজ—হ্যাঁ, হল্যাণ্ডে ডেয়ারি খুবই রয়েছে তবে সে আর কতটুকু ? Scandinavian দেশগুলো বিশেষত সুইডেন গোটা বিশ্বের dairy product-এর চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কি বিশাল বিশাল farm, আর তেমনি নিখুঁত arrangement এবং security-র ব্যবস্থা। এক একটা farm-এ ধরে নাও দশ থেকে বারো হাজার গরু রয়েছে। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে farm I প্রধানত plain land কেই dairy farm-এর জন্য বেছে নেওয়া হয়। বা প্রাধান্য দেওয়া হয়। ওখানে ওরা বিভিন্ন ধরণের ঘাসচাষ করে, তারমধ্যে ঔষধি গাছও থাকে। ঐ বিশাল অঞ্চলের পুরোটাই কাঁটাতার বা এমনি তার দিয়ে ঘেরা থাকে এবং সেখানে ১০/১২ volt current সর্বদা প্রবাহিত করা হয়, যাতে গরু-ভেড়ারা বেড়া ডিঙিয়ে পালাতে না পারে। Practically ঐ current লাগার ভয়ে ওরা বেড়ার গায়েই যায় না। Current রাখার আর একটা সুবিধা হল উল্টো দিক থেকে নেকড়ে, হায়না বা বাঘ-ভালুকরাও চট্ করে বেড়ার মধ্যে ঢুকতে পারে না। ঐসব জায়গার farm house-গুলো পশুপ্রেমীদের বেড়ানোর জায়গা হিসাবে সহজেই বিবেচিত হতে পারে। এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর এত সাজানো-গোছানো যে, এখানকার যে কোন লোক অবাক হয়ে যাবে। আর গরুগুলোর প্রতি কি যত্ন ! Farm-house-এর মধ্যেই কর্মচারী বা কেয়ার টেকারদের কোয়ার্টার, পশুচিকিৎসকের কোয়ার্টার, সুন্দর জলের ব্যবস্থা আবার sanitation ব্যবস্থাও চমৎকার। খাদ্যভর্তি লরি একেবারে farm-এর ভিতর ঢুকে যায়, আবার লরি- ভর্তি dairy-product বাইরে চলে যায়। গরুরা যাতে চরে বেড়াতে পারে তারজন্য বিভিন্ন পুষ্টিকর ঘাসের চাষ করা হয়। আবার মাঝে মাঝে shade রয়েছে সেখানে ওরা বিশ্রাম করতে পারে আবার সেখানে বাইরে থেকে আনা পুষ্টিকর খাদ্য তাদেরকে খাওয়ানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবার খাদ্য দেবার আগে পশু-চিকিৎসক তা পরীক্ষা করে নেয়, পরীক্ষার পর তবেই তা দেওয়া হয়। এক-একটা দুধেল গাই দৈনিক ৭০-৮০ লিটার দুধ দেয়। গাই দোহানোর লোক নেই। সব মেশিন-এর সাহায্যে। বড় বড় নল লাগানো রয়েছে একবারে tank-এর সঙ্গে। দোহানো মেশিনে automatic sucking হয়ে চলেছে আর দুধ চলে যাচ্ছে বড় বড় tank-এ বা direct দুধের গাড়ীতে। কেউ কেউ অন্য কোম্পানিকে সরাসরি দুধ বিক্রি করে, নিজেরা কোন product বানায় না। আর যারা নিজেরা চীজ, পনির, বা দুধের অন্যান্য সামগ্রী বানায়, তারা ঐ দুধকে processing করতে থাকে।
যে কোন দুধেল গাই-এর বয়সকালে যদি দুধ কমতে কমতে ৫০ লিটারে নামে, তাহলে আর ঐ গরুটিকে ওরা বাঁচিয়ে রাখে না, গুলি করে মেরে দেয়। কারণ ঐ গরুটার পিছনে যা খরচ তার চেয়ে গরুটি থেকে প্রাপ্ত আয় কম হচ্ছে। কোম্পানী কোনরকম loss বরদাস্ত করে না। এই কথা শুনে তোমাদের অনেকেরই দেখছি মনে দুঃখ লাগল। অত ভালো গরুগুলোকে জ্যান্ত মেরে ফেলে ! তাইতো ? কারণ তোমরা বল, “গো হামারা মাতা হ্যায়” আহা কিই বা তোমাদের মায়ের দশা ! আমাদের এখানে বাড়ীর সমস্ত জায়গার মধ্যে সাধারণত গরুর গোয়াল—সবচাইতে নোংরা জায়গা, অন্ধকার স্যাঁতসেতে, দুর্গন্ধ আর সেইখানে গরুকে থাকতে দেওয়া হয়, খেতে দেওয়া হয় নোংরা খাদ্য আর নোংরা জল। গো-মাতা মুখে বলছ – পারবে নিজের মাকে ওই গোয়ালঘরে রাখতে আর ঐভাবে খাওয়াতে ? ওরা গরুর প্রতি যত্ন করে। গরু থেকে আয় কমে গেলে গরুটাকে ওরা মেরে ফেলে, মাংসের চাহিদা রয়েছে market- এ। বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ-য় চলে যায় মাংস, চর্বি চলে যায় বিভিন্ন food কোম্পানিতে। হাড়, চামড়া, লিভার এগুলো সবই পৃথক পৃথক কারখানায় বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়ে যায়। ঐ সব দেশে dairy শিল্প একটা অন্যতম অর্থকরী শিল্প, ফলে লোকসানের দিকটা তো ওরা দেখবেই।
গরু বা ভেড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওরা একদল কুকুর পোষে। Trained কুকুর, সারাদিন-রাত সুন্দর পাহারা দেয় ওদের। বিশেষত গরু বা ভেড়ার বাচ্ছারা ছুটে ছুটে বেড়ায়, দল-ছুট হয়ে যায়—ওরা ঘাড়ে ধরে আবার ঠিক জায়গায় নিয়ে আসে। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ায় ‘কুয়োমিন’ নামে একরকম জন্তু আছে যারা বেড়ার ফাঁক গলে farm-এর ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং ভেড়া বা বাছুরদের গলা ফুটো করে রক্ত খায়। এতে বাছুর বা ভেড়াটি আহত হয় বা মারাও যেতে পারে। কুকুরের পাল ওদের হাত থেকে বাছুর বা ভেড়াদের রক্ষা করে। যাইহোক ব্যবস্থা গ্রহণে ওদের ত্রুটি নেই, ওরা প্রচণ্ড সচেতন আর ভীষণ hygienic । আমাদের এদেশেও তো মহিষ বা গো-পালনের জন্য “খাটাল” রয়েছে। সেখানে গরু-মোষ- গুলোর স্বাস্থ্য দেখো তো একবার। হাড় জিরজির করছে—সব T.B রোগ হয়েছে। ঐ দুধ ফুটিয়ে না খেলে মানুষেরই T.B রোগ হয়ে যাবে। আর ওদের দুধ কাঁচা খাওয়া হয়, frozen milk, cold milk বাজারে বিক্রি হয়। আমাদের দেশে “বাটার অয়েল” পাওয়া যায় যা ভেজাল-মেশানো নকল। সয়াবিনের তেলের সাথে অন্যকিছু মিশিয়ে butter-oil বলে চালায়। ও সব দেশে কিন্তু যে কোন dairy-prod uct একেবারে pure এবং pasturised, sterlised, Cheese, butter, milk নিয়ে বিভিন্ন dairy product-এর বড় বড় দোকান। হবে না কেন—ইউরোপীয়ানরা প্রায় সব খাবারের সঙ্গেই হয় butter নয় cheese মিশিয়ে খায় যে !
আসলে সুইডেনে আমি বিভিন্ন farm house-এ গিয়ে সবকিছু দেখে এসেছি বলেই তোমাদের dairy সম্বন্ধে এত কথা বললাম, এগুলো শোনাকথা বা বই-এ পড়া নয়।
জিজ্ঞাসু—গরুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কারখানায় যায় বললেন, এগুলো থেকে কি ধরণের by-product হয় ?
গুরুমহারাজ—এগুলো আবার জিজ্ঞাসার কি আছে ? এখানেও তো গরুর হাড় থেকে সার হয়, চামড়া চলে যায় tannery- তে। গরুর লিভার যায় ঔষধ তৈরির কারখানায়, বিভিন্ন লিভারটনিক তৈরী হয়। ডেয়ারিগুলিতে শুধুমাত্র গরুর liver supply করার জন্যও ওখানে গো-পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। গরুগুলোকে ওরা ছোট থেকেই এমন কিছু হরমোন injection দেয় যাতে গরুগুলোর লিভার প্রচণ্ড বড় হয়ে যায়, আর গরুটা খুব খায়। এতে করে গরুটার পেটটাও মোটা হয়ে যায় আর লিভারও বিরাট বড় হয়। এবার ওরা যখন বুঝতে পারে যে লিভারটি matured হয়েছে তখন পশুটাকে কেটে লিভারগুলোকে ওষুধের কারখানায় পাঠিয়ে দেয়। কুকুরের লিভার থেকেও ‘টনিক’ তৈরী হয়। গরু, কুকুর, শুয়োর এসব প্রাণীর লিভার খুবই storng, তাই লিভারটনিক তৈরীতে এদের লিভারের ব্যবহার করা হয়। কুকুর ভাগাড় ও পচা-গলা জন্তু- জানোয়ারের মাংস-হাড় খেয়ে হজম করে। শেয়াল, কুকুর ইত্যাদিপ্রাণীর পায়খানা পরিমাণে বেশী হয় না, এছাড়া এদের মলে অজীর্ণ থাকে না। এসব দেখে বোঝা যায় এদের হজম ক্ষমতা কত বেশী। শেয়ালের পায়খানাও চুন-চুন, লোমশ প্রাণী অর্থাৎ ইঁদুর ইত্যাদি খেলে শুধু লোমগুলো পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসে—সাংঘাতিক হজম ক্ষমতা !