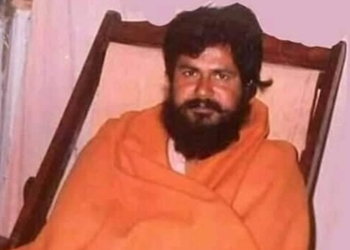জিজ্ঞাসু—শেয়াল-কুকুর কি একই প্রজাতি ?
গুরুমহারাজ—কুকুরের থেকেও শেয়াল জীব-বিবর্তনের অনেক আগেকার প্রাণী। নেকড়ে থেকে কুকুরের উদ্ভব। জীববিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জেনেছে যে, নেকড়ে আর শেয়ালের Cross-breed হয়ে কুকুর প্রজাতি এসেছে। নেকড়ে মাংসাশী অথচ শেয়াল আমিষাশী হয়েও কিন্তু নিরামিষ আহার পছন্দ করে। পাকা ফল, কৃষকের জমির ফসল এসব শেয়ালের প্রধান খাদ্য। আখ, পাকা কাঁঠাল এসব তো শেয়াল খুবই খায়, এগুলো ওদের পছন্দের খাবার। ইংরেজরা এদেশে এসে শেয়ালের কাঁঠাল খাওয়া দেখে কাঁঠালের নামই দিয়ে দিল Jackal-fruit বা jack fruit । শেয়াল এমনিতে অবশ্য ছোট ছোট পোকামাকড়, কাঁকড়া, মাছ ইত্যাদি খায়। কিন্তু দেখা গেছে শেয়াল যদি আঙুরক্ষেত বা আখ-জমি পায় সেদিন সে আর কাঁকড়া শিকারে যাবে না। নলেন গুড় বা খেজুর গুড় হয় যে রস থেকে, সেই খেজুর-রস শেয়াল খায়। ছোট, বাঁকা হেলানো খেজুর গাছে খেজুর-রসের হাঁড়ি টাঙানো থাকলে লাইন দিয়ে শেয়াল সেই গাছ থেকে রস চুরি করে খায়। অর্থাৎ একটা শেয়ালের রস খাওয়া হয়ে গেলে সে গাছ থেকে নেমে আসতেই পরের জন গাছেউঠে রস খেতে শুরু করে। গাছের মালিক ভাবে বুঝি কোন দুষ্টু ছেলে রস-চুরি করে খাচ্ছে কিন্তু সে বুঝতেই পারে না যে, শেয়ালে রাতের পর রাত খেজুর রস খেয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় আমি যখন রাত্রে বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াতাম তখন এসব দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি। তবে শেয়ালকে কুকুরের সাথে “ভাগাড়” খেতেও দেখেছি।
জিজ্ঞাসু—শেয়াল কি জল থেকেই মাছ বা কাঁকড়া ধরে ?
গুরুমহারাজ—হ্যাঁ জল থেকেই ধরে। মাছ আবার ডাঙায় এসে বসে থাকে নাকি ? ওরা জলাশয়ের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়, ডাঙার কাছাকাছি যেসব মাছ ঘোরে তাদেরকে ওরা ধরে খায়, আর কাকড়া লেজের সাহায্যে গর্ত থেকে টেনে বের করে খায়। মাছের কাটা, কাকড়ার ছিবড়ে এসব মাঠের পুকুরের ধারে পড়ে থাকে, তাছাড়া সাদা রঙের শেয়ালের পায়খানা—এসব দেখে বোঝা যায় যে, সেই অঞ্চলে শেয়ালের উপদ্রব আছে। তবে জল থেকে মাছ ধরার expert হ’ল ভোঁদড়। এরা শেয়াল প্রজাতির নয় কিন্তু এক একটা পূর্ণবয়স্ক ভোঁদড় দু’ থেকে আড়াই কেজি ওজনের মাছ জল থেকে তুলে আনতে পারে। আর আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ওরা এমন বিশেষ কায়দায় মাছটাকে ধরে নিয়ে আসবে যে মাছ একটুও আহত হবে না আবার ওরা যতক্ষণ ধরে থাকবে ততক্ষণ মাছ নড়াচড়াও করবে না। ওরা যেই ডাঙায় এসে মাছটাকে ছেড়ে দেবে তখন মাছটি দফা-দফাঙ্ করে লাফাতে থাকবে, তার আগে একটুও নড়বে না। আসলে মাছের মাথার দু’পাশে এমন কোন piont রয়েছে, যেখানেচাপ দিয়ে ধরলে মাছের ঐ অবস্থা হয়, ঐ piont-টা ভোঁদড়েরা জানে, আর সেইখানেই চাপ দিয়ে ধরে ওরা মাছটাকে ডাঙায় তোলে। ২৪ পরগণায় বড় বড় মাছের ভেড়ি রয়েছে—ওখানকার মালিকেরা ভোঁদড় পোষে। ৪/৫ টা ভোঁদড়ে খুব তাড়াতাড়ি ১ কুইন্টাল মাছ ধরে দেবে। এক একটা দু’ থেকে আড়াই কেজি মাছ ডাঙায় তুলে আনলেই ওদের মনিব বকশিশ হিসাবে একটা করে ৫০–১০০ গ্রাম সাইজের বাটা মাছ ওদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। যা খেয়েই ওরা ফের জলে নামে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঐ সাইজের আর একটা মাছ ধরে আনে। তবে এখনকার আইনে ভোঁদড় পুষতে গেলে lisence করাতে হয়। এদের দিয়ে মাছ চুরি করা যায় বলে—এই আইন হয়েছে। জলাশয়ের ধারে কোন কাঁটা বা পায়খানা দেখে শেয়াল রয়েছে কিনা বোঝা যায়, আর জলাশয়ের ধারে ভোঁদড় রয়েছে বোঝা যায় মাছের মাথা পড়ে থাকতে দেখলে । কারণ ভোঁদড় জল থেকে মাছ তুলে মুড়োটা কেটে ফেলে দিয়ে ধড়টা খেয়ে নেয়। অনেক জায়গায় ভোঁদড়কে উদবেড়াল বলে। তবে শীতপ্রধান অঞ্চলে বিশেষত তুন্দ্রা অঞ্চলে ভোঁদড়ের মতই দেখতে একটা অদ্ভুত প্রাণী রয়েছে এদের ‘বিয়র’ বলে। এরা সাধারণত বার্চ গাছের ছাল খায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, একটা দলের সর্দার দুই-আড়াই ফুট ব্যাসার্ধের একটা ৪০-৫০ ফুট উঁচু বার্চ গাছকে ২-৩০–৩ মিনিটের মধ্যে কেটে দেবে, দাঁতের এত তীব্র ধার আর জোর। এবার গাছটা পড়ে যেতেই অমনি পুরো দলটার শুরু হয়ে গেল মহাভোজ। এদের বাসস্থান জলের উপরে। ভালুকের মুখের মতো খানিকটা দেখতে এদের মুখ। এরা mammal, জলের মধ্যে ডালপালা দিয়ে খুব সুন্দর করে ঘর বানায়। পাড় থেকে যাওয়া-আসার জন্য ডালপালা দিয়ে bridge বানায় ঘর পর্যন্ত। ডালপালা কেটে আনাটা তো ওদের কাছে সামান্য ব্যাপার। লম্বা লেজের সাহায্যে সাঁতারও কাটতে পারে আর বিপদ বুঝলে ‘সিস্’ দিয়ে সকলকে সতর্ক করে ভুস করে ডুবে পড়ে। খুব মজাদার প্রাণী। ওদের নানারকম শত্রুদের মধ্যে মানুষ অন্যতম। কারণ ওদের গায়ের ছাল থেকে সুন্দর fur-coat হয়। তাই ওরা বাজারে খুব ভালো দামে বিকোয়। সুতরাং লোভী মানুষ কি আর ওদের না মেরে থাকতে পারে— সুযোগ পেলেই নিরীহ প্রাণীগুলিকে মেরে বিক্রি করে প্রচুর পয়সা কামিয়ে নেয়।
এইভাবেই দেখা যায় প্রাণীজগতে যে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম রয়েছে, যেমন অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম, আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম, পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামাদিতে যারা বেঁচে রয়েছে তারাই fittest, তাদেরই অভিব্যক্তি হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীতে সকল প্রাণীকেই মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে সবচাইতে বেশী। মানুষের লোভরিপু, হিংসাবৃত্তি ইত্যাদি এমন সব বদগুণ রয়েছে, যত নগণ্য প্রাণীই হোক বা যত হিংস্র প্রাণীই হোক মানুষের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। গভীর সমুদ্রে চোরা তিমি শিকারীরাও রয়েছে। হনু-বাঁদর, পাখি, বেড়াল কি না শিকার করে মানুষ ! হয় তাদের মাংসের লোভে অথবা চামড়ার লোভে, না হয় দাঁত বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ বিক্রি করে পয়সা পাওয়ার লোভে, মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। বিষধর প্রাণীদেরও নিস্তার নেই—তাদের বিষই কাল। কারণ এই বিষ থেকে নানান ওষুধ তৈরী হয়, তাই বিষের জন্যই বেচারারা মারা পড়ে।
যাইহোক কি কথায় এসব কথা এসে গেল, আসলে সমস্তপ্রাণীর প্রাণের ব্যথা আমার প্রাণকে স্পর্শ করে—তাই ব্যথাতুর হয়ে কথাগুলো বললাম।
জিজ্ঞাসু—কোন একজন আশ্রমিক নাকি সম্প্রতি বিবাহ করেছে ?
গুরুমহারাজ—হ্যাঁ করেছে। এরপর তুমি জানতে চাইবে এমন কেন হ’ল—ইত্যাদি। দ্যাখো, যদি কেউ নিজের দুরাগ্রহ নিজে ডেকে আনে তাহলে তোমার কি করার আছে আর তার জন্য দায়ীই বা কে হতে পারে বল ? এর আগেও তো এমন ঘটনা ঘটেছে তার থেকে তো শিক্ষা নিতে হবে। তা যদি কেউ না নেয় তার জন্য কর্মফল তাকেই ভোগ করতে হবে। আমার ভূমিকা নিয়ে যদি প্রশ্ন করো, তাহলে আমি বলব আমি কারও ভাব নষ্ট করি না। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ আমি বলে দিই এবার তুমি কোনটা গ্রহণ করবে —সেটা তোমার choice. আশ্রমিকদের তো একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে চলা উচিত—এখানে তেমন লিখিত নিয়ম না থাকলেও তো আশ্রমের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে। সেটা না মেনে যদি কেউ স্বাধীনভাবে চলতে চায়, নিজের মতে চলতে চায়, তাহলে তাকে গৃহে ফিরে যেতে হবে, গৃহস্থ হতে হবে। যাইহোক এ ব্যাপারে একটা গল্প বলি শোন :
এক বুড়ির কয়েকটি ছাগল ছিল, আর ওর বাড়ি ছিল সমুদ্রেরধারে। প্রতিদিন সকালে ঐ বুড়ি লম্বা দড়ি দিয়ে ছাগলগুলিকে একটা শক্ত খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতো। অন্য লোকেদের ছাগলগুলো খোলা চরে বেড়াতো। ফলে বুড়ির ছাগলেরা ভাবতো, তারাও যদি খোলা থাকত, ছাড়া থাকত তাহলে কি ভালোই না হ’ত, কি স্বাধীনভাবেই না তারা ঘুরে বেড়াতে পারত ! হঠাৎ একদিন সমুদ্রের বুকে ঝড় আছড়ে পড়ল। বড় বড় ঢেউ প্লাবিত করতে লাগল উপকূলকে। আর সেই প্লাবনে সমুদ্রের তীরবর্তী যা-কিছু সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু প্লাবন থামলে লক্ষ্য করা গেল যে, বুড়ির ছাগলগুলিই কেবল ঠিক আছে। সমুদ্রের জলে নাকানি-চোবানি খেয়েছে কিন্তু ভেসে যায়নি। ঐ শক্ত খুঁটি আর লম্বা-দড়ির বাঁধন তাদের বাঁচিয়ে দিল।
আশাকরি গল্পের তাৎপর্যটা ধরতে পেরেছো। গুরু জানেন শিষ্যের কতটা স্বাধীনতা দরকার। তাই তিনি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন, কাজের বা সাধন পদ্ধতির ভিন্নতা করে দেন। গুরুবাক্য ঠিক-ঠিক মেনে চললে শিষ্যের নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে, কিন্তু গুরুবাক্য লঙ্ঘন করলে ভেসে যাবে। তবে এখানেও একটা কথা রয়েছে সমুদ্র যা নিয়ে যায় তা নাকি আবার ফেরতও দেয়, তবে জীবিত অথবা মৃত। জীবিত হলে ভালো নাহলে কি গুরু তাকে রক্ষা করবেন না ! গুরুর কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা রয়েছে। সঞ্জীবনী প্রয়োগ করে গুরু মৃতকেও জীবিত করতে পারেন। তাই বিপদে পড়লে মানুষ ‘গুরু রক্ষা করো’ বলে প্রার্থনা করে। কারণ সে জানে বিপদের ত্রাতা হ’ল গুরু। আবার ভুল বা অন্যায় করলে গুরুর কাছে অকপটে স্বীকার করা যায়। কারণ গুরু যেমন মাতা বা পিতা, তেমনি গুরু সখা বা বন্ধুও বটে। তাই ভুল করলে ভুল শুধরে গুরু আবার তাকে কোলে টেনে নেন। ঐ জন্য সদা-সর্বদা গুরু ধরে থাকতে হয়। শাস্ত্রে বলেছে, “গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।” গোবিন্দ ত্যাগ করলেও গুরু ত্যাগ করেন না, আবার গুরু রুষ্ট হলে গোবিন্দও তার কিছু করতে পারে না। গুরুতত্ত্ব বড় সাংঘাতিক তত্ত্ব। উন্নত, উচ্চকোটির সাধকেরাও এইজন্য গুরু হতে চান না বা ঠিক ঠিক সদগুরু হতে পারেন না। শিষ্যের ভার নিতে হয়, ইহজন্মের ও পরজন্মের। “গুরুভার” – কথাটা এখান থেকেই এসেছে। সমুদ্রে জাহাজে অনেক লোক-জন একসাথে পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনেকগুলি ডুবন্ত মানুষকে জাহাজ রক্ষা করতে পারবে না। তখন কি করা হয়—ছোট বোট বা কাঠের পাটাতন ফেলে দেওয়া হয় জাহাজ থেকে, যা ধরে ঐ ডুবন্ত মানুষগুলো সাময়িকভাবে রক্ষা পায়। পরে রশি ঝুলিয়ে বা শেকল ঝুলিয়ে দিলে সেগুলি ধরে মানুষগুলো জাহাজের উপরে উঠে আসে। গুরুই হচ্ছে ঐরকম বাহাদুরি কাঠ। বিপদে পড়ামাত্র যিনি শিষ্যকে immediate রক্ষা করেন। গুরুশক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি বা ভগবৎশক্তি। গুরু ছাড়া জীব উদ্ধার পেতে পারে না। কি করে পারবে ? এই মহামায়ার জগতে রূপ-রসাদি নানান প্রতিবন্ধকতা রয়েছে— জীবের সাধ্য কি এসব অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে এগিয়ে যায় ! কোনদিনই পারবে না, কল্প থেকে কল্পান্তর লেগে যাবে, জীব যেখানে ছিল চেতনার জগতে প্রায় সেইখানেই থেকে যাবে। এখানেই গুরুশক্তি কাজ করে, করুণাবশত ভগবৎশক্তিই গুরুশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে পঙ্কিলাবর্ত জগৎ থেকে কাদামাখা জীবসকলকে ধরে ধরে পাড়ে তুলে দেন, সযত্নে পরিষ্কার করে দেন। এমন বন্ধু জগতে আর কে আছেবলোতো ?
এই যে কথাগুলো বললাম এগুলি ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। কিন্তু গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করলেই মুস্কিল, তখনই মানুষ দুরাগ্রহের শিকার হয়, সুতরাং গুরু ধরে থাকো, সর্বদা গুরুর কৃপা প্রার্থনা করো—“গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্, গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্, গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।”
জিজ্ঞাসু—বহু গুরুপরম্পরায় বহুরকম বিরোধ হয়— এতে কি গুরুবিরোধী কার্যকলাপ হয় বা গুরু রুষ্ট হন ?
গুরুমহারাজ—গুরু পরম্পরা বলছ—গুরুর জীবদ্দশাতেই কতরকম কাণ্ড হয় ? যীশু, ভগবান বুদ্ধ এদের জীবদ্দশাতেই তো শিষ্যেরা গুরুর বিরোধ করল বা গুরুকে মেরে ফেলতে সাহায্য করল। কিছুকাল আগের দুই বিখ্যাত বৈষ্ণব মতাবলম্বী গুরুদের কথা যদি ধরো, তাহলে দেখবে যে, কোথাও তাঁর ছেলেরা, কোথাও তাঁর শিষ্যেরা জীবদ্দশাতেই ওদের গুরুকে মৃত বলে ঘোষণা করে দিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের পুরীতে শরীরত্যাগের ব্যাপারেও নানা কথা শোনা যায়। স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীর কলকাতার শিষ্যরা এখনও গুরুদেবের কনকপুরে মৃত্যুর ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি, রহস্যের গন্ধ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষ তার স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করে, আর সেই অনুযায়ীই চলে। গুরুদেব আধ্যাত্মিক মানুষ, তিনি সৎ ওসুন্দরের পূজারি ছিলেন, সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করে জীবদ্দশায় উপস্থিত জনের মঙ্গল চিন্তায় জীবন কাটিয়েছেন। উত্তসুরিরা হয়তো অত উন্নত নয়, তারা গুরুদেবের তৈরী করে দেওয়া জায়গাকে কাজে লাগিয়ে হয়তো অন্য কিছু করতে চায়।
একমাত্র ভগবানই অবিচল থাকতে পারেন। তিনি কখনও কারও দোষ দেখেন না বা কারও দোষ ধরেন না। কারণ তাঁর সৃষ্ট জগতের রহস্য তিনি জানেন। জীবসকল নিজ-নিজ কর্ম অনুযায়ী ফললাভ করে থাকে। একমাত্র তিনিই নিষ্কলঙ্ক, ক্ষমাশীল, দোষমুক্ত, পবিত্র থাকতে পারেন। তাই যখন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হ’ল তখন ওখানে উপস্থিত শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে ম্যাগডালিন ও কয়েকজন মিলে যীশুকে কিছু (অলৌকিক বা ঐ ধরণের কিছু) করার জন্য কাতর অনুরোধ করেছিল। কিন্তু যীশু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বললেন—“হে ঈশ্বর, ওরা জানে না যে ওরা কি অপরাধ করছে, ওদের তুমি ক্ষমা করো।” আমিও চিন্তা করে দেখেছি ভগবান শরীর নেন জীব-কল্যাণের জন্য, আর জীবসকল বিশেষত মানুষই তাঁর উপর সবচাইতে বেশী আঘাত করে, অত্যাচার করে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের মেরেও ফেলে। তাহলে ঈশ্বরের অবতার হয়ে পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর মানুষদের উদ্দেশ্যে ভগবান ছাড়া ঐ কথাগুলি আর কি বলতে পারেন ! সত্যিই তো মানুষ জানে না যে সে কি করছে, জানলে কি করতো ?
তবে সাধারণভাবে দেখা যায় মানুষের ভালো-মন্দের বোধ রয়েছে। তবু হয়তো সে মন্দটাই করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিয়েছিলেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়া। রক্তাক্ত হয় তবু খায়। মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ রয়েছে, অন্যায় করলে কর্মফল ভোগ করতে হয় –হয়তো তাও জানে, তবু করে বসে। তাই সাধারণ জ্ঞান হলে হবে না, জ্ঞানের পরিপূর্ণতাতেই বোধ আসে, আর বোধে বোধ হলে তার দ্বারা আর কোন অন্যায় কর্ম হয় না।
জিজ্ঞাসু—তাহলে মহাপুরুষদের যাদের আমরা ঠাকুর বলি, তাঁদের মৃত্যুর জন্য তাঁর সন্তান বা শিষ্যরাও দায়ী হতে পারে ?
গুরুমহারাজ—হবে না কেন ? মহাপুরুষরাও তো মানুষ, কিন্তু মানুষবেশী ঠাকুর। তবে মানুষ হলেও সবাই একরকম হয় না আর তার শিষ্য বা সন্তানরাও মানুষ। তাই মানুষ সমাজে যা করে ওখানেও তাই হয়। আমি সবাইকেই ঠাকুর দেখি—এটা আমার স্বকীয়তা বা নিজস্বতা। তেমনি প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বকীয়তা বা নিজস্বতা রয়েছে। তবে একটা কথা জানবে যে, বংশ পরম্পরায় আধ্যাত্মিকতা অনুসৃত হয় না। ভারতীয় আর্যঋষিরা বা কোন মহাপুরুষ—অবতারপুরুষ একথা কখনও বলেন নি। রামচন্দ্রের পুত্র লব-কুশ, কৃষ্ণের পুত্রগণ, বুদ্ধপুত্র রাহুল এরা কখনই ভগবানের উত্তরসূরি ছিলেন না। ভগবান অবতীর্ণ হন স্বকীয় চিদাভাসের দ্বারা। তিনি জন্ম নেন না আবির্ভূত হ’ন। ভগবানের আবির্ভাবের জন্য কোন backing বা কোন con- dition-এর প্রয়োজন হয় না। অমুকের পুত্র হতে হবে অমুক বংশে জন্মাতে হবে ইত্যাদি কোন শর্ত সেখানে কাজ করে না।
সাধারণ মানুষ কি বিচারশীল ? তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতে অনেক পাবে, কিন্তু বিবেক পরিচালিত বুদ্ধির প্রয়োগ ক’জন করে ? যারা করে তারাই বিচারশীল মানব। এদের খুব একটা বড় ভুল হয় না, বাকী সব মানুষ তো গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোর দলে। গদরসিং-এর গল্প বলেছিলাম না তোমাদের—বেশীরভাগ মানুষ ঐ গদরসিং-এর দলে। লক্ষ লক্ষ শিষ্য বা ভক্ত রয়েছে—এই দিয়ে আধ্যাত্মিকতা নয়।
আধ্যাত্মিকতা হল quest ! Quest for truth and quest for eternal bliss, পরম সত্য ও পরম শান্তির অন্বেষণ। মঠ-মিশন, মন্দির-মসজিদ, গীর্জায় লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে, এদের তুমি religious বলতে পারো কিন্তু এরা spiritual নয়। ওরা কোন না কোন religious sentiment-এর মধ্যে রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান পালন করে, নিয়ম করে ধর্মস্থানে বা গুরুধামে যায়। ভাবে এতেই তার বা তার পরিবার পরিজনদের মঙ্গল ঘটবে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বা spirituality এটা নয়। জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার সেখানে স্থান নেই। নিজেকে জানতে পরমতত্ত্বে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যে চলা—তাই spirituality, যা মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অবশেষে পৌঁছে দেয় পূর্ণত্বে। এই চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়ে মানব মহামানবে রূপান্তরিত হয়, মানব মাধব হয়। তাই বলছিলাম ঠাকুরই মানুষ হয় আবার মানুষ-ই ঠাকুর হয়, কথাগুলো বুঝতে গোলমাল কোরো না গোলের মধ্যেই ‘মাল’ রয়েছে সেইটা ধরে থেকো।
জিজ্ঞাসু—১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে কি বন্যাপ্রবণ বৎসর ? এবার আগাম বর্ষা, তাছাড়া আসামে বন্যা শুরু হয়ে গেছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি ?
গুরুমহারাজ—এই আগাম জানার মানসিকতা মানুষের খুবই প্রবল। এইজন্যই মানুষ জ্যোতিষীদের কাছে যায়, তাবিজ-কবজ- মাদুলি পরে, কোষ্ঠী বানায় আরও কতকি যে করে তার ইয়ত্তা নেই। আমি কি গণৎকার নাকি যে, পাঁজি-পুঁথি খুলে গণনা করে তোকে বলে দেব—এবার কত বৃষ্টি, কত বন্যা ! আমি science-টা বলছি শোন্—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর আগমনে বাংলায় বর্ষার সূত্রপাত হয়। ভারত মহাসাগর থেকে ৭টি পৃথক পৃথক সময়ে এবং পৃথক পৃথক track-এ ওখান থেকে মৌসুমীবায়ু ছুটে যায় ভারতবর্ষের স্থলভাগের দিকে। কাছাকাছি 10 th may থেকে প্রথম প্রবাহটা স্থলভাগের দিকে ছোটে। এটাই উপকূলীয় সমভূমি—পূর্ববঙ্গ, আসাম, হিমাচলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ আমাদের এই দিকটায় তৃতীয় প্রবাহটি আসে 20th june বা তার কাছাকাছি সময়ে। এবার সমগ্র বর্ষাকালের মধ্যে কোন্ প্রবাহটি কতটা strong, তার উপরেই নির্ভর করছে সেই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত। যে প্রবাহটি strong সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত, যে weak সেদিকে খরাপ্রবণ এলাকা অর্থাৎ বর্ষায় বৃষ্টিপাত ভালো হয় না।
তবে এখন তো দেখছি বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপজনিত বৃষ্টিপাত বেশী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গে। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমীবায়ু পশ্চিমবঙ্গে শীতের প্রাক্কালে বৃষ্টিপাত বেশী ঘটাতে পারে, ওটাও বঙ্গোপসাগর থেকে আগত জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু। মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে যে বৃষ্টিপাত হয় তা ফসল-উৎপাদনের উপযোগী, তা ছাড়া এই বৃষ্টিপাতে রবিশষ্য ভালো হয়। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমীবায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্টি হয়ে কোনাকুনি কাশ্মীর পর্যন্ত যায় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়, এটি সমগ্র অঞ্চলে রবিশষ্যের উপকার করে। তবে বঙ্গদেশে খরিফ মরশুম বা বর্ষাকালের ফসলের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়। এই রাজ্যের বেশীরভাগ মানুষই কৃষিজীবী। তাই খরিফ মরশুমে ধান, পাট ইত্যাদি মুখ্যফসল ভালো না হলে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং মানুষের নিদারুণ অর্থকষ্ট হয়। ভালো বৃষ্টি না হলে অথবা অতি বৃষ্টির ফলে বন্যা হলে মানুষের খুবই কষ্ট হয়। ১৯৭৮ সালে দামোদরের বন্যায় অসহায় মানুষগুলোর কষ্ট আমি নিজে চোখে দেখেছি। গ্রামের পর গ্রাম মানুষের কাঁচাবাড়ি সব পড়ে গিয়েছিল ঐ বৎসর। জমির ধান, গোলার ধান, ঘরে মজুত খাবার সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কি অসহায় অবস্থা বাবা-মায়েদের! ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েদের মুখে একটু অন্ন দিতে পারছে না। আর সরকারী সাহায্য—তার কথা না বলাই ভালো। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য পৌঁছানোর দু’দিন পর সরকারী সাহায্য এসে পৌঁছাল। আমরা কয়েকজন মিলে একটা স্কুলবাড়ীতে সারাদিন রুটি বানিয়ে মানুষকে খেতে দিয়েছিলাম। জানি সবাই পেটভরে পাবে না, তাই বরাদ্দ হল শিশু বা বাচ্ছাদের এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রথমে, তারপর মহিলাদের, তারপর যুবকদের দেওয়া হবে। তখন দেখেছিলাম বাচ্ছার বরাদ্দ রুটি লুকিয়ে লুকিয়ে মা আধখানা খেয়ে নিচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালায় মা নিজের অস্তিত্ব রক্ষাটাই বড় করে ভাবছে।
যাইহোক ১৯৭৮ সালের বন্যা পশ্চিমবঙ্গে একটা বীভৎস প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল। কত মানুষ আর গবাদি পশু যে ঐ সময় মারা গিয়েছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান করা যায় নি। ঐ সময় আমাদের বনগ্রাম আশ্রম তৈরি হয়েছিল। বনগ্রামে আমার আসার কথা ছিল পূজার সময় বা তার আগে। কিন্তু প্রলয়ঙ্করী বন্যা আর মানুষের কষ্ট দেখে আমি দামোদরের তীরবর্তী গ্রাম চক্ষণজাদীতে আটকে গিয়েছিলাম, বন্যাদুর্গত মানুষের সঙ্গে তাদের কষ্ট share করছিলাম। এমন সময় এখান থেকে ন’কাকা-(শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী)র চিঠি গেল। ন’কাকার চিঠি পেয়ে আমি বনগ্রামে এলাম এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা হ’ল, এখন এইসব কাজ হচ্ছে। তবে আমি দেখেছি যে, ঐ ১৯৭৮ সালের পর আর কিন্তু অমন প্রলয়ঙ্করী বন্যা আর হয়নি। এরপর থেকেই কিন্তু নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষেরা নতুন করে কাঁচা মাটির বাড়ি আর করেনি, কষ্টেসৃষ্টে ইটের পাকাবাড়ি করে নিয়েছে, যাতে করে বন্যায় আর ঐরকম হৃতসর্বস্ব না হতে হয়। আর আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নতি, গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন —সব এরপর থেকেই। ১৯৭৮ সালের বন্যা এবং তার করাল গ্রাস যেন একটা সীমারেখা। এর ওপারের চিত্রটা গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। কিন্তু এপারের চিত্রটা যদি দেখো দিনদিন গ্রামীণ অর্থনীতি উপরদিকে উঠে আসছে। গ্রামীণ অর্থনীতির এই উন্নতির পিছনে ইন্দিরা গান্ধীর ‘সবুজ বিপ্লব’ নীতি অনেকাংশে কার্যকরী। উচ্চফলনশীল বীজ আমদানি, সেচের সুবিধা, কীটনাশক ও রাসায়নিক সার এবং কৃষির অন্যান্য উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার এসবের জন্যই গোটা ভারতবর্ষ সহ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে ব্যাপক উন্নতিসাধন হয়েছে। আর এরই ফলস্বরূপ গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন এসেছে। এরপর যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে গ্রামের কৃষিজ সম্পদ সরাসরি শহরের বাজারগুলিতে পৌঁছাতে পারছে গ্রামের মানুষ। ফলে মাঝখানের middleman-এর আর প্রয়োজন হচ্ছে না। এটিও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতির আর একটি বড় কারণ। সর্বোপরি গ্রামীণ ব্যাংক, কো-অপারেটিভ সংস্থা এগুলি থেকে কৃষকেরা স্বল্পসুদে ঋণ পাচ্ছে, অনেক সময় অনেক ঋণ মকুবও হয়ে যাচ্ছে, ফলে গ্রামের মানুষ দুটো পয়সার মুখ দেখছে। এখন গ্রামগুলিতে শিক্ষার হার যথেষ্ট ভালো এবং মানুষের বিশেষত বর্ধমান জেলার মানুষের কথা বলছি – এখানে আলসে-কুঁড়ে অথবা রোগগ্রস্ত ছাড়া না খেতে পেয়ে কেউ মারা যায় না। এসব দেখে আমার খুবই আনন্দ হয়।