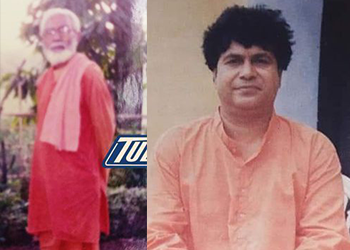জিজ্ঞাসু—তীর্থস্থানে গেলে পুণ্য হয়—এমনকি বিভিন্ন মহাপুরুষগণও তীর্থ-দর্শনে যেতেন শোনা যায়, এগুলির পিছনে রহস্যটা কি ?
গুরুমহারাজ—সাধারণ সংসারী সামাজিক মানুষ, সংসারের নানান ঝামেলার মধ্যে সারাজীবন কাটাতে বাধ্য হয়। সংসার মানেই তো Problem—সমস্যা, মানুষের নানান সমস্যা – দেহ নিয়ে সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, পারিবারিক বিবাদজনিত সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার সমস্যা – এইরকম হাজার সমস্যা রয়েছে। সেইসব ঝামেলা মেটাতে মেটাতে মানুষের ফুরসৎ বের করে একটু-আধটু বাইরে ঘুরে আসাটা যেন গুমোট আবহাওয়ায় এক ঝলক দমকা হাওয়ার মতই স্বস্তিদায়ক। বাইরে ঘোরা বা যে কোন ভ্রমণের কথা বললাম শুধু তীর্থদর্শনের কথা বললাম না। তবে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থানগুলিকেই ভারতবর্ষে তীর্থস্থান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন অবশ্য over population, তাই তীর্থস্থানগুলোর পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা তো নেই-ই বরং আরও নোংরা ও বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। আজ থেকে ১০০ বছর আগেও হরিদ্বার, পুরী আজকের মতো এত জনাকীর্ণ আর নোংরা ছিল না–পরিচ্ছন্ন ছিল। বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি আর একটা কারণে great, সেটা হচ্ছে এগুলোর অবস্থান। এখানকার natural view এত ভালো যে, মানুষ ঐসব স্থানে গেলেই যেন একটু অন্যরকম হয়ে যায়। আমি দেখেছি—প্রথম সমুদ্র দেখে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাও কেমন যেন বালক-বালিকার ন্যায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। বিশালতার স্পর্শ পেয়ে মানুষ যেন তার উৎসে ফিরতে চায়, তাই একটু অন্যরকম হয়ে যায়—এটা কম কিছু নয়, বিশাল সমুদ্র, বিরাট হিমালয় মানুষের মনোজগৎকে পরিবর্তন করতে পারে। কত চোর, ডাকাত, খুনি, বদমাস—এই সব স্থানের প্রভাবে— এখানে থাকতে থাকতে জীবনটার পরিবর্তন করে ফেলেছে। তাই স্থান-মাহাত্ম্য রয়েছে বইকি ? তাছাড়া এই সমস্ত স্থানে অনেক উন্নত চেতনার মানুষ, ভালো মানুষ সাধন-ভজন করেন—তাঁদের প্রভাবেও মানুষের মনের পরিবর্তন হয়।
তবে মহাপুরুষরা তীর্থে যান অন্য কারণে। তাঁরা তীর্থ দর্শন করতে যান না তাঁরা তীর্থের মহিমাকে বাড়াতে যান। তীর্থস্থানগুলিতে হাজারে হাজারে সাধারণ সংসারী মানুষ যায়। যাদের হয়তো তেমন সাধন-ভজন নেই, তবু দ্যাখা যায় তাদের সেখানে গিয়ে কিছু উপকার হোল। এটা হয় কারণ মানুষ তো তীর্থদর্শন করাকালীন সাময়িকভাবে হলেও তার জাগতিক বা সাংসারিক মোহকে উপেক্ষা করে, ভক্তিভাব আশ্রয় করে। আর ঠিক তখনই ঐসব স্থানের যে সঞ্চিত ভাবরাশি তা তাকে help করে। ফলে অনেকেরই ভাবজগতে নানা পরিবর্তন হয়। কেউ কিছু দর্শন করে, কারও মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকারের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। এইরকম অনেক কিছু হয়। সেইরকম ব্যাকুলতা বা পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন- ভজন থাকলে কোন সাধকের জীবনে এই পরিবর্তিত ভাব দীর্ঘস্থায়ী বা স্থায়ী হয়ে যায়। শোনা যায় যে, অমুক তীর্থদর্শন করতে গিয়ে আর ফেরেনি। সাধু হয়ে সেখানেই থেকে গেছে। তবে ঐ যে সঞ্চিত ভাবরাশির কথা বললাম ওটার সঞ্চয় করে দেন বিভিন্ন সাধু- সন্ত আর সর্বোপরি মহাপুরুষেরা। তাই ধর্মকেন্দ্রে, তীর্থস্থানে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক field-এ সাধু-সন্তের বিরাট ভূমিকা থাকে। এই যে তাঁরা দিনের পর দিন একান্তে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন-ভজন করে আত্মদর্শনের পথে এগিয়ে চলেছেন, এটা কি কম নাকি ? সেই বিরাট-তত্ত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র-আমি তত্ত্বের যোগাযোগের ক্রিয়া চলছে সেখানে। ফলে যে কোন সাধক সেখানে সাধনা করুক না কেন—তিনি সেখানকার বাতাবরণে Positive ভাবরাশি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। হয়তো কেউ নিভৃতে নিরালায় সাধন করছেন, কেউ ধর্মালোচনা করছেন প্রকাশ্যে। এভাবেই আধ্যাত্মিক ভাব বা Positive ভাবসমূহ সেখানকার পরিবেশকে সমৃদ্ধ করছে। ফলে যে কোন মানুষ সেখানে প্রবেশ করলেই তার মধ্যে negativity গুলো neutralise হতে থাকবে। কোন Positive field-এ বেশিদিন থাকলে বা ঘন ঘন যাওয়া-আসা করলে একজন নিজেই এর সত্যতা বুঝতে পারবে। এইজন্যই যখন শিষ্য প্রণাম করে বিদায় নেয় তখন গুরুদেব বলেন “আবার এস।” দেরি করে এলে বলে— ‘কি গো, এত দেরি করে আসতে হয় ?’
তাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে তীর্থস্থানগুলি যেন এক একটা Power-station। ঈশ্বরের মহিমা যেমন জগৎ-ব্যাপী, তাকে সাধনের দ্বারাই উপলব্ধি করতে হয়, তেমনি ঈশ্বরের করুণাও জগতে পরিব্যাপ্ত জীবসকলকে সাহায্য করার জন্য। তীর্থস্থানে যেন ঈশ্বরের করুণালাভের জায়গা, অন্যস্থানেও পাওয়া যায়—এখানে যেন অনায়াস- লভ্য। মহাপুরুষগণ তীর্থস্থানে গেলে তাঁর নিজস্ব positivity থেকে ঐ স্থানকে charged করে দেন—যার সুফল সাধারণ তীর্থযাত্রীরা পায়। এখানে যে সাধকগণ থাকেন তাঁদের সাধন-ভজন ঐ field- কে পুষ্ট করে। ফলে জ্ঞানে-অজ্ঞানে এঁরাও মানব-কল্যাণকারী। তবে মজার ঘটনা হল কোন তীর্থস্থানের সঞ্চিত positive charge আবার কোন উপযুক্ত আধারকে দিয়ে দেওয়া হয়—এটা নিয়ন্ত্রণ করেন আধ্যাত্মিক গুরুকুল। সে এবার এটাকে গ্রহণ করে মানবকল্যাণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তা বিলিয়ে দেন। মায়ের জগতে কোন কিছুই নষ্ট হয় না। সংসারেও দেখবে আদর্শ গৃহিণী বা জননী কোন কিছুই সহজে নষ্ট হতে দেন না। তরকারির খোসা দিয়েও একটা ভালো চচ্চড়ি বানিয়ে ফেলবেন অথবা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে একটা সুন্দর কাঁথা বানিয়ে ফেলবেন। আর বিশ্বজননী কোন কিছু ফেলবেনই বা কোথায় —সব কিছুই তো মা-ময়। সমাজের উন্নত ভাবরাশি সৃষ্টিকারীসাধকদের মধ্যে দার্শনিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীরাও আছেন আবার সাধু- সন্ত-সাধকগণও রয়েছেন। কোন কোন সময় কোন স্থানের atmo sphere-এ উন্নত ভাবরাশির সঞ্চয় হয় আবার কোন সময় কোন উপযুক্ত আধার সেই সঞ্চিত ভাবকে গ্রহণ করে সমাজের কিছু কল্যাণসাধন করে যান। যেন স্থানীয় ব্যাঙ্ক বা দেশের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে গ্রাম বা শহরের উন্নয়ন করা। কিন্তু যেমন মাঝে মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক বা IN.F থেকে টাকা ধার নিয়ে দেশের কোন বিরাট project-এর রূপ দিতে হয়, তেমনি অনেকসময় বহির্জাগতিক ক্ষেত্র থেকে শক্তি আনার প্রয়োজন হয় পৃথিবীগ্রহের কল্যাণের জন্য। এবার এই শরীরে কাজ করার জন্য শতভিষা নক্ষত্র থেকে শক্তি আনার প্রয়োজন হয়েছিল।
তবে সাধারণ মানুষের তীর্থদর্শন আর মহাপুরুষদের তীর্থদর্শন এককথা নয়। মহাপুরুষদের তীর্থগমন তীর্থোদ্ধারের নিমিত্ত, তীর্থের মহিমাকে বাড়ানোর নিমিত্ত, সাধারণ মানুষ যাতে তীর্থদর্শনের ফললাভ করতে পারে তার নিমিত্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা-মা, শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন তীর্থস্থানে গিয়ে সেই স্থানের মাহাত্ম্যই বাড়িয়েছেন। আমি অমরনাথে গিয়ে মনঃসংযোগ করে অতীতের vibration কেমন ছিল তা জানলাম—স্বামী বিবেকানন্দ যাবার আগে ওখানকার Positivity ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। স্বামীজী পুনরায় ওখানে আধ্যাত্মিক ভাবরাশি বাড়িয়ে দিলেন, স্থানটিকে charged করে দিলেন। ওনার আগে তো মানুষজন এত যেতো না। এখন প্রতিবছর অত কষ্ট করেও লক্ষ লক্ষ মানুষ অমরনাথ দর্শনে যায়। তবে জানবে যে, কোন বস্তু বা বিষয়ের দুটো মেরু থাকে। একটা পরমাণুর মধ্যেও দুটো বিপরীতমুখী ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তাই যে স্থান যত ভালো সেই স্থান ততটাই খারাপ, তীর্থস্থানগুলিতেও দেখবে পাণ্ডাদের আর দালালদের অত্যাচার, চুরি, ছিনতাই, পকেটমারের অত্যাচার, রাত্রিবাসের জন্য হোটেল বা লজগুলিতে থাকাও ব্যয়বহুল – ইত্যাদি নানান অসুবিধা রয়েছে। তবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ‘যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।’ তাই যদি শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাও তাহলে লজে থাকো, স্ফূর্তি করো—চলে এস আর তীর্থের সুফল পেতে হলে অন্তরে ভক্তিভাব আনো—আকুল হয়ে তীর্থনাথের কাছে প্রার্থনা করো –সেখানকার ভাবরাশির সন্ধান নিশ্চয়ই পাবে। আমার গুরুদেব রামানন্দ অবধূতজী বলতেন তীর্থস্থান যেন ব্যাঙ্কের এক একটা শাখা। যদি তোমার কিছু জমা থাকে তবে তো তুমি অন্য কোন শাখা থেকে তা তুলতে পারবে। তোমার কাছে চেক্ বা ড্রাফট্ থাকতে হবে তো ! (এখন উন্নত প্রযুক্তিতে যে কোন শাখা থেকেই টাকা তোলা যায়)। প্রয়োজনে তুমি যেমন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারো তেমনি ওখান থেকে তুমি loan বা সাহায্যও পাবে, যদি তোমার কিছু থাকে। আর negative field-এর লোকেরাও সাহায্য পাবে। যেমন ধরো কেউ কাশী গেল, ওখানে কাশীশ্বর বিশ্বনাথ রয়েছেন, কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণাও রয়েছেন। ভক্তিভাব নিয়ে যদি কেউ ওখানে সাধন-ভজন, প্রার্থনাদি করে তো মহাদেব বা মহাদেবীর কৃপা অবশ্যই পাবে। কিন্তু এই কাশীতেই সাট্রা-জুয়ার বিরাট ঠেক্ রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোক কাশী যায় শুধু সাট্টা-জুয়া খেলতে। আবার দ্যাখো, যেহেতু বেনারস-কাশী বিশাল জনবসতিপূর্ণ শহর তাই ওটা ভালো business centre। বহু ব্যবসাদার কাশীকে বেছে নিয়েছে ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে। এবার বলো এদের সবার কি কাশীবাসের ফল একই হবে ? “যাদৃশী যস্য ভাবনা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।”
এই কারণেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন “যার হেথায় আছে তার হোথায় (সেথায়) আছে, যার হেথায় নেই—তার কোথাও নেই।” আবার রামপ্রসাদ বলেছিলেন “তীর্থ দরশন, মন-উচাটন”। যেহেতু তীর্থস্থানে নানারকম ব্যাপার আছে, মন positive ছেড়ে negative- এর দিকে চলে যেতেও পারে, মন-চঞ্চল হতেই পারে। তাই সাধক কবি বললেন, “আপনাতে আপনি থাকো মন, যেও নাকো কারো ঘরে।” কোথাও ঘুরে না বেড়িয়ে নিজের জায়গায় বসে অন্তর্মুখী হয়ে ধ্যানের গভীরে, জ্ঞানের গভীরে, প্রেমের গভীরে অথবা সেবার গভীরে ডুবেও অমৃততত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আর অমৃততত্ত্ব লাভ করেছেন এমন কোন সাধককে কেন্দ্র করে আবার একটা পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। মধুর লোভে—সুগন্ধে মত্ত অলিকুল বা ভ্রমররা যেমন পুষ্পের চারিদিকে গুঞ্জন করে বেড়াতে থাকে, তেমনি যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে বা যাঁর মধ্যে অন্তত প্রেমের সঞ্চার হয়েছে, তাঁকে কেন্দ্র করে কিছু ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠবেই। এই পবিত্র মানুষটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে সেই স্থানের ভূমিও পবিত্র হয়ে উঠবে উত্তরসূরিদের কাছে। এইভাবে জন্ম নেয় নতুন নতুন তীর্থক্ষেত্র ধরণীর বুকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনভূমি দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী আজকের মানুষের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। তাই ক্ষেত্র নয় ক্ষেত্রজ্ঞই মহান। সেই সব সচল তীর্থস্বরূপ মহান মানুষদের নমন্ করি।
জিজ্ঞাসু ——ঈশ্বর কি ? ঈশ্বর কি আছে ?
গুরুমহারাজ—তোমার স্বরূপই ঈশ্বর। তাই ঈশ্বর আছে কি নেই বাইরে কোথাও না খুঁজে তুমি তোমাতেই খোঁজ। কারণ আর কিছু না থাক তুমি তো আছ। এটাই “অস্তি”। উপনিষদে রয়েছে “অস্তি-ভাতি-প্রিয়” বা সৎ-চিৎ-আনন্দ-ই ঈশ্বর। তাই তুমি আছ এটাই সৎ বা অস্তি। এবার তুমি খোঁজ তোমার মধ্যে। গুরুকরণ করে সাধনার গভীরে প্রবেশ করো। ঈশ্বরতত্ত্ব তোমার কাছে প্রকাশিত হতে থাকবে—এটাই ‘চিৎ’ বা ‘ভাতি’। এবার ক্ষুদ্র ‘আমি’র বিরাট ‘আমি’তে সংযুক্ত হওয়া, ক্ষুদ্র জলাশয়ে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা খেলার যে হিল্লোল-কল্লোল সেটাকে তো পার্থিব কোন আনন্দ দিয়ে বোঝাতে পারবে না, সেটা প্রকৃত ‘আনন্দ’, এটাই উপনিষদের ‘প্রিয়’। তাহলে কি বোঝা গেল ঈশ্বর সৎ-স্বরূপ, ঈশ্বর চিৎ-স্বরূপ এবং ঈশ্বর আনন্দ- স্বরূপ। আনন্দ-স্বরূপ অর্থাৎ তোমার স্বরূপে আনন্দ। দ্যাখো, প্রতিটি মানুষ বা জীবজগৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই আনন্দকেই তো পেতে চাইছে। পাচ্ছে না বলেই তো এত হাহাকার! প্রতিটি জীব সেই permanent আনন্দকে পেতে চাইছে, আনন্দই খুঁজছে। তার মানে যেহেতু সে আনন্দস্বরূপ, সেহেতু সে কি তাঁকেই খুঁজছে না ? তাহলে মানুষের এই হাহাকার, জ্বালা-যন্ত্রণা আনন্দ না পাওয়ারই তো জ্বালা ।
এখন দেখতে হবে তাহলে ভুলটা কোথায় হল — খুঁজছি অথচ পাচ্ছি না কেন ? এর কারণ আমার স্বরূপই যে আনন্দ, অথবা আমিই যে আনন্দস্বরূপ সেকথা বিস্মৃত হয়েছি। বিস্মৃত হয়েছি সেইজন্য আনন্দকে খুঁজছি বাইরে, আনন্দ পেতে চাইছি ব্যক্তিতে, বস্তুতে, বিষয়ে। তাই জ্বালা—তাই যন্ত্রণা—তাই হাহাকার। কস্তুরী মৃগ যেমন তার দেহাভ্যন্তরে যে সুগন্ধের উৎস, এটা না জেনে, না বুঝে আহার ত্যাগ করে সারা বন ছুটে ছুটে বেড়ায় আর সুগন্ধের উৎসের অনুসন্ধান করে, তার পা ব্যথা হয়ে যায়, শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়, অবশেষে অনেক সময় মারাও যায়—মানুষও তেমনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে ছুটে ছুটে বেড়ায় আর আনন্দের অন্বেষণ করে বস্তুতে, বিষয়ে, ব্যক্তিতে। এর ফলে বাসনা-কামনা-মোহাদির শত সহস্র বন্ধনে নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে হাহাকার করে, মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু কে খুলে দেবে সেই বন্ধন—নিজেকেই খুলতে হবে। সদগুরু শুধু খোলার কায়দা শিখিয়ে দেবেন—খুলতে কিন্তু নিজেকেই হবে। বাঁধনের দড়িটা একটু অল্প চাপ হলেই যেমন খানিকটা মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি সাধকের জীবনে কখনও কখনও সেই অপার্থিব আনন্দের touch বা স্পর্শ পাওয়া যায়। এতে সাধক পূর্বসূরিদের কথিত সত্যের প্রমাণ পায় কিন্তু তাতো স্থায়ী হয় না তাই আবার জ্বালা, আবার কষ্ট, আবার হাহাকার। যতক্ষণ এই জ্বালা ততক্ষণই জীব। আর যেই মুহূর্তে জ্বালার অবসান অমনি জীবের জীবত্ব ঘুচে গিয়ে শিবত্ব। যে জীবের অর্থাৎ মানুষের আর কোন জ্বালা নেই, আর বাসনা নেই, কামনা নেই, মোহাদি নেই তিনিই শিব। এই ধরণের মহাত্মার সঙ্গ করলেও অন্তরে শান্তি আসবে, ইন্দ্রিয়াদি সংযত থাকবে। এঁদের সংস্পর্শ পেলেই মানুষ শান্তি পাবে। দ্যাখো এইখানেই এসে গেল জ্বালার কারণ। কামনা-বাসনা- মোহাদিই জ্বালার কারণ। বাসনা আছে যার সেই জীব, আর নির্বাসনাই শিব। ভক্তিশাস্ত্র একেই বলেছে নির্বাসনা। গোপীদের বস্ত্রহরণ বা নির্বসনা ব্যাপারটা স্থূল নয় প্রকৃত রহস্য এটাই—তাঁরা সাধনার দ্বারা নির্বসনা হয়েছিলেন। তাই নির্বসনা, অর্থাৎ মলবিক্ষেপ-আবরণ মুক্ত, তুরীয় অবস্থা। ভক্তিতত্ত্বের প্রকৃত রহস্য জানতে গেলে মাদিভাব নিয়ে চোখের জল ফেলে “বস্ত্রহরণ” পালা কীর্তন শুনলে হবে না, জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে তবেই ভক্তিতত্ত্বের রহস্য জানা যাবে। নাহলে ভক্তিতত্ত্বের রস অন্তঃসারশূন্যরূপ ফুটো মালাই দিয়ে পড়ে গিয়ে সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রযত্ন বা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধনের দ্বারাই জীব নির্বাসনা হতে পারে। আর নির্বাসনা হতে পারলে তবেই স্বরূপের বোধ হয়। জীবের বোধ হয় যে, “জীবই শিব”, অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তার সঙ্গে একীভূত হয়। যেমন তুমি বিশ্বসংসারের সঙ্গে আবরণ দিয়ে ঢাকা আছ, এবার আবরণ উন্মোচিত হলে তুমি কি আর পৃথক থাকবে ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে একটা খড় দিয়ে কিছুটা জল পাড়ের সঙ্গে আলাদা করে দেখালেন। তারপর ভক্তদের বোঝালেন খড় দ্বারা আবৃত জলটা যেন ব্যক্তি- অহং আর খড় সরিয়ে নিলেই সব একাকার। তবে জীববুদ্ধি থাকতে ঈশ্বরতত্ত্বের ধারণা করা যায় না। তাই যারা সাধনায় ব্রতী হয়েছে তাদের কর্তব্য কোনদিকে না তাকিয়ে গুরুর বলে দেওয়া পথকে নির্দিষ্ট করে সাধন করে যাওয়া। বাকী যা কিছু সেগুলো আপনা-আপনি হবে, যদি না মাঝখানে অহং এসে বাসা বাঁধে। সাধনা করতে করতেই সিদ্ধি আসবে। হয়তো কাউকে বলে দিলে—তাফলে গেল, কিছু পাবার চিন্তা করলে—সেটা লাভ হয়ে গেল। সেই ধর্মব্যাধের বকভস্মের গল্পটাও এই শিক্ষাই দিয়েছে। কিছু শক্তিলাভ হলেই সাধকের পতনের পথ তৈরী হয়ে গেল। তারপর যখনই পাঁচজন মান্যগণ্য করতে লাগল—তখনতো আর কথাই নেই, একেবারে গুরুদেব বনে বসল। কি বিপদ বলোতো—নিজেরই সঞ্চয় হোলনা তো অপরকে কি দেবে! ঢোঁড়ার ব্যাঙ ধরার মত গিলতেও পারেনা —উগরাতেও পারেনা, দু’জনেরই কষ্ট। তাই সাধক সর্বদা সাবধান, অহংরূপ শত্রু যেন তোমাতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। সর্বদা জপ করবে শরণাগতোহহং, শরণাগতোহহং, শরণাগতোহহং, শরণ্যে ।
জিজ্ঞাসু—স্বপ্ন দেখে মানুষ, অনেকের স্বপ্ন নাকি মিলে যায়, অনেকে স্বপ্নে দীক্ষা পায়—এগুলি কি সঠিক না গাঁজাখুরি ?
গুরুমহারাজ—এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করছ কেন ? সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসারই আমি উত্তর দিই—জিজ্ঞাসার মধ্যে শ্রদ্ধা না থাকলে উত্তর দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে তোমার কোনই মঙ্গল হবে না। তবে এখানে অনেকে শ্রদ্ধাবান রয়েছে বলেই বলা যায়, তুমি একা থাকলে তোমার কথায় চুপ করে থাকতাম্। তুমি হয়তো জানো না শাস্ত্রে বলা আছে, “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।”
যাইহোক স্বপদেখা আর স্বপ্নে দীক্ষা হওয়া ব্যাপারদুটো কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার । প্রথমক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজে কর্তা আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সদগুরু যিনি সূক্ষ্মে বা কারণে দীক্ষা দেবার অধিকারী তিনি কর্তা, ব্যক্তি এখানে অকর্তা, কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সাধারণত মানুষ সারাদিন যা করে বা অতীতে যা করে এসেছে, এমনকি পূর্ব পূর্ব জীবনের সংস্কার রাশির print থাকে মানুষের অবচেতন মনে। মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনের তিনটি অবস্থার কথা বলেন—চেতন, প্রাক-চেতন ও অবচেতন। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের চেতনমন যখন ক্রিয়া করে না তখন প্রাক-চেতনমন অবচেতন মনকে দিয়ে সেগুলিকে নিয়ে ক্রিয়াশীল করার চেষ্টা করে। তখনই মানুষ স্বপ্ন দেখে। বাস্তবে সে যা পারছে না তখন সে অনায়াসেই সেটা করতে পারে, বাস্তবে যেটা কখনই ঘটেনি—সেইটা ঘটতে চলেছে এইরকম নানান কিছু দেখে। পাশ্চাত্যমনো বিজ্ঞানী ফ্রয়েড এইসব ব্যাপার নিয়ে অনেককিছু ব্যাখ্যা করেছে।
কিন্তু শক্তিশালী মহাপুরুষ বা সদগুরুগণ —নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, মনের উপর কর্তৃত্ব করতে পারেন তাঁরা, যে কোন individual mind-এর প্রাকচেতন স্তরে যোগাযোগ করতে পারেন। সেই ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন ঘুমন্ত অবস্থায় অর্থাৎ তার চেতন মন ক্রিয়াশীলতা বন্ধ করলেই যোগাযোগ করা যায়, এমনকি তার চেতন মন ক্রিয়াশীল থাকলেও বা ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থাতেও যোগাযোগ করা সম্ভব। এখানে বসে টেলিফোনে দিল্লী, বোম্বাই অথবা লণ্ডনে ‘ডায়াল’ করার মতো সাধারণভাবে ব্যক্তির ঘুমন্ত অবস্থাতেই এই ধরণের যোগাযোগ হয়। মানুষের তিনটি অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির মধ্যে সুষুপ্তিতেই মানুষের প্রকৃত বিশ্রাম হয়। মহাপুরুষের যোগাযোগের সময় ব্যক্তিটি গভীর সুষুপ্তিতে চলে যায় । সেইসময় তার বিভিন্ন দর্শন, আলাপন, এমনকি দীক্ষাগ্রহণও হতে পারে। সাধারণ স্বপ্নের সঙ্গে এর মূল পার্থক্য এই যে, অন্য স্বপ্ন মানুষ প্রচুর দ্যাখে কিন্তু ঘুম ভাঙলে মনে থাকে না—মনে পড়লেও ভাসা-ভাসা। আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রের দর্শনটি তার সম্পূর্ণ মনে তো থাকেই, যেন মনে হয় সবচাইতে উজ্জ্বল স্মৃতি। অন্য স্বপ্নের স্মৃতি থাকলেও যেন তা এলোমেলো কোনটার সঙ্গে কোনটার জুড়ে দিয়ে কেমন যেন ছন্নছাড়া। আর এই দর্শন যেন সম্পূর্ণ একটা অধ্যায়। যা অপরকে বলে আনন্দ পাওয়া যায় আবার অপরকে আনন্দ দেওয়াও যায়, আর স্বপ্নের ঘটনাটি যখনই স্মৃতিতে আসুক তা নিজের ভিতরেও একটা অদ্ভুত আনন্দের হিল্লোল তোলে।
জিজ্ঞাসু—পারলৌকিক ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধাদি কর্ম কি সর্বত্র একইভাবে সম্পন্ন হয় ?
গুরুমহারাজ—তা হবে কেন ? Semitic মতাবলম্বী অর্থাৎ খ্রীষ্টান, ইহুদি, মুসলিম এদের যেমন মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা আলাদা তেমনি পারলৌকিক অন্যান্য ক্রিয়াও আলাদা। মুসলমানদের মৃতদেহের দফন-কাফন হয়, এদিকে একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা চলতে থাকে। তারপর সকলে মিলে শবাধার কবরস্থানে বয়ে নিয়ে যায় এবং একটা বিশেষ ‘নমাজ পড়া হয়। এরপর কবর খোঁড়া হয়ে গেলে মৃতদেহকে কবরে শুইয়ে পুত্র বা উত্তরাধিকারী প্রথমে আড়াই আঁজলা মাটি দেয়। তারপর সকল আত্মীয়-বন্ধুরা মাটি দিতে থাকে, শেষে পুরো মাটি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয়। যাদের সামর্থ্য আছে তারা হয়তো পরে মিস্ত্রি ডেকে উপরটা বাঁধিয়ে দেয়—সমাধিমন্দির তৈরি করে। আর সাধারণ মানুষ একটু মাটি দিয়ে উঁচু করে দেয়। “ইসলাম” যেহেতু আরবদেশ থেকে চলেছে, আর ওদেশের বালিয়াড়ির ভূমিরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলায় তাই ওখানে বালিয়াড়িতে কবর দেবার পর স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য স্থানীয় একমাত্র খেজুর গাছের পাতা পুঁতে দেওয়া হোত। সেই রীতি এখানেও মানা হয়, অনেকে কবরের উপরে খেজুর পাতা গুঁজে দেয়। এরপর কয়েক সপ্তাহ পরে (৪০ দিন ) কিছু লোকজন খাইয়ে দেওয়া হয়।
হিন্দুদের মধ্যেও পারলৌকিক ক্রিয়ার ভিন্নতা দেখা যায়, স্থান-কাল-পাত্রে সবকিছুরই অবশ্য ভিন্নতা হয়। South India-র বিভিন্ন স্থানে পিতা-মাতার মৃত্যুর দিনেই পুত্র মাথা ন্যাড়া করে নেয় এবং ১২দিন পর কিছু লোকজন খাওয়ারও অনুষ্ঠান করে। বিহার- উত্তর প্রদেশেও এইরকম সব আলাদা আলাদা নিয়ম। ইন্দিরা গান্ধী মারা গেলে রাজীব গান্ধী কি মাথা ন্যাড়া করেছিল না “কাচা” পরেছিল ? বাংলায় রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধান, অন্যান্য প্রদেশের বিধান অন্য স্মার্তকারের। এবার যদি বলতে চাও এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি বা সঠিক ক্রিয়াটি কি – তাহলে আমি বলব – কায়মনোবাক্যে মৃত পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটাই শ্রাদ্ধ । এবার যে সন্তান পিতামাতার জীবদ্দশাতে তাদেরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করল না সে যতই ঘটা করে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করুক না কেন কি ফল হবে ? তবে তুমি হয়তো বলবে যেহেতু সমাজে রয়েছে—সমাজের অনুশাসন তো মানতেই হবে। সুতরাং কাজ হোক বা না হোক পুরোহিত ডেকে কাজও করতে হবে। তবে আমি দেখেছি এখানকার শ্রাদ্ধাদিকর্মের যে বিধান সেটা বেশ ভালোই। ১০/১২ দিন বা ১৫ দিন দু’খণ্ড শুদ্ধ ‘কাচা’ কাপড় পরে, ফলমূল হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে থাকতে হয়, অল্প শয্যায় শুতে হয় এককথায় ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন-যাপন করতে হয়। এতে পুত্র বা কন্যার সমূহ মঙ্গল হয়। কারণ প্রথমত শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ, সংযমাদি পালনে শরীর ও মনের সুস্থতা আসে। এতে সাময়িক শোক সহ্য করার ও মাথায় সংসারের বোঝা চাপার যে চিন্তা তা গ্রহণ করার ক্ষমতা জন্মে। দ্বিতীয়ত ১০/১২ দিন বা তার বেশী একটা বিশেষভাবে ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন-যাপন করায়, ঐ অবস্থাটাই তাকে তার মৃত পিতা বা মাতাকে সদাসর্বদা স্মরণ করায় উভয়েরই মঙ্গল হয়। এছাড়া আরও অনেক কারণ আছে যেমন কমপক্ষে ১০/ ১২ দিন পরে শ্রাদ্ধ করা হয় কেননা দূর-দূরান্তের আত্মীয়-কুটুম্ব- বন্ধুরা শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থেকে তাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বা মৃতব্যক্তির পারলৌকিক শান্তি প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানাতে পারে। বহু লোক একত্রিত হলেই একটা বড় খাওয়া-দাওয়া বা ‘ভোজ’-এর ব্যাপার থাকে। এর প্রয়োজনীয় কেনাকাটা বা প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যও অন্তত এই সময়টা দরকার। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান অঞ্চল, পিতামাতার পর সাধারণত ভাইভাই পৃথগন্ন হয়ে যায়। শ্রাদ্ধবাসরে বিভিন্ন বয়স্ক বা মাননীয় অতিথি-আত্মীয়রা একত্রিত হয়ে সেগুলিরও একটা সূক্ষ্ম মীমাংসা করতে পারেন। এভাবে বহুবিধ সুফল পাওয়া যায় এই ধরণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। তাই আঞ্চলিক ভিত্তিতে অবশ্য পালনীয় যে কর্তব্যগুলি রয়েছে সেগুলি করাই মঙ্গলের।