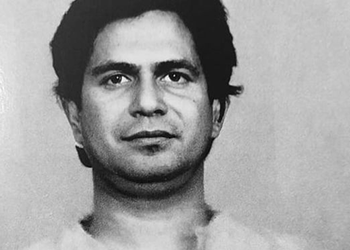জিজ্ঞাসু — আপনি বলেছিলেন প্রারব্ধবশত জন্ম হয় অর্থাৎ কেউ সুস্থদেহে ভালো পরিবারে, কেউ অসুস্থ হয়ে বা নোংরা পরিবেশে জন্মায় কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছে মায়ের অপুষ্টি বা গর্ভকালীন আঘাত থেকে শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়। তাহলে বাহ্যিক কারণেই তো অসুস্থ শিশুর জন্ম—এখানে প্রারন্ধের স্থান কোথায় ?
গুরুমহারাজ—মায়ের ঐরূপ অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্তি বা গর্ভকালীন মায়ের খ্যাদ্যাভাবজনিত কারণে বা অন্য কারণে অপুষ্টি → —এগুলোও তো প্রারব্ধবশত ? তবে বাহ্যিক কারণ হিসাবে যে দুটি কারণ বললে ঐগুলি ছাড়াও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর পিছনে বিজ্ঞানীরা দায়ী করছেন বিভিন্ন contraceptive বা অন্যান্য drug-এর reac tion-কে। এছাড়া বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার Phenomenal disturbance এর জন্য দায়ী।
শিশু বিকলাঙ্গ হবার নানান scientific কারণ রয়েছে, সেটা না হয় জানা গেল, কিন্তু দ্যাখা গেছে যে, বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন প্রকার রোগ হবার tendency নিয়েই জন্মায়। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার রোগ- প্রবণতা জিনেই রয়েছে, এর বিজ্ঞানসম্মত কারণ কি ? যদি বল মাতা বা পিতার জিনে ছিল, জাইগোট গঠনের সময় বা crossing- over-এর সময় এসে গেছে, অনেক সময় কিন্তু তাও মেলে না। যদি কোন শিশু হাসপাতালে যাও, তো দেখবে ছোট ছোট শিশু কি ভয়ানক ভয়ানক রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত !
সুস্থ সন্তান জন্ম দেবার ব্যাপারে পিতা ও মাতা উভয়েরই সাংঘাতিক ভূমিকা থাকে। পিতা ও মাতার ক্রোধপ্রকাশ, ঝগড়াঝাঁটি, উদ্বেগ, দুঃখ, ঈর্ষা ইত্যাদি যে কোন প্রকার স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটে যাবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি concieve হয় তবে পিতা মাতার vibration ভ্রূণের normal vibration-কে ব্যাহত করে, আর ge- netic রোগের এটাই উৎস। আগেকার দিনে গর্ভাধান পাঁজি দেখে নিয়ম করে করা হোত। আর মুনি, ঋষি বা বড় বড় পণ্ডিত ডেকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল, যাতে সুস্থ-সবল-সৎ চিন্তাযুক্ত সন্তান উৎপাদন হয়। কিন্তু আর্য-সমাজবিজ্ঞান বর্তমান সমাজ থেকে চলে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তো আর এসব শিক্ষাই নেই। গর্ভোপনিষদ পাঠ করে কে আর গর্ভ-উৎপাদন করে বল দেখি ! যাইহোক বোঝাই যাচ্ছে যে বর্তমানে কতিপয় পিতা বা মাতা কদাচিৎ এ ব্যাপারে জ্ঞাত বা যৌনজীবনে সংযত, বেশীর ভাগই নয়। তাই একেবারে সুস্থ নীরোগ শিশু আর জন্মগ্রহণ করছে না। তবে এটা জেনে রাখবে, যে কোন রোগ কিন্তু বংশপরম্পরায় বাহিত হবেই—এমন কোন মানে নেই। কোন রোগগ্রস্ত পিতা বা মাতাও যদি সন্তান উৎপাদনের প্রাক্কালে সুস্থ চিন্তা, সুচিন্তা বা পবিত্র চিন্তার মধ্যে থাকে, তাহলে শরীর দুর্বল হলেও সেখানে সুসন্তান হবে।
তবে গর্ভে সন্তান প্রবেশ করার পর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বা ভূমিকা মায়ের। গর্ভধারণের অন্তত ১৬ সপ্তাহ মাকে যে কোন প্রকার স্নায়বিক উত্তেজনা মুক্ত থাকতে হবে। এই ব্যাপারে আর্যবিধি হ’ল concieve- এর পর আর স্বামী সহবাস নয়, বিভিন্নভাবে ধর্মচিন্তা বা অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। মা বিভিন্ন প্রকার ধর্মমূলক বই বা মহাপুরুষদের জীবনী পড়বে, সাধুসঙ্গ-সৎসঙ্গ করবে অর্থাৎ এমনভাবে থাকবে যাতে মায়ের মন প্রফুল্ল থাকে, চিন্তামুক্ত উদারভাব বজায় থাকে, সাংসারিক খিটিমিটির মধ্যে না থেকে গর্ভবতী মা যেন সদা-সর্বদা নির্ঝঞ্ঝাটে ও নিরুদ্বিগ্ন মনে বাস করে। গর্ভকালীন অবস্থায় রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়েছিলেন বলে তার অনেক অখ্যাতি রয়েছে বটে কিন্তু লব-কুশের ন্যায় মহান শিশুর জন্মদানের জন্য ঋষি আশ্রমে বাস করাটা সীতামার প্রয়োজন ছিল।
Concieve-এর সময়কালীন পিতা বা মাতার মানসিক উত্তেজনা সন্তানের উপর কেমন প্রভাব ফেলতে পারে, শাস্ত্রাদিতে তার উল্লেখ রয়েছে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মবৃত্তান্তে দেখা যায় যে বিচিত্রবীর্য ( নামেই বোঝা যায় যে তিনি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ছিলেন)-র স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভসঞ্চার করেছিলেন তাদের ভাশুর ব্যাসদেব। কিন্তু ব্যাসদেবের রঙ খুবই কালো ছিল, এছাড়া দীর্ঘ জটা ইত্যাদি থাকায় তিনি কুৎসিত-দর্শন ছিলেন। গর্ভসঞ্চারকালে ব্যাসদেবকে দেখে অম্বিকা-অম্বালিকা এই দুই বোনের একজন ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিলেন তাই তার পুত্র হয়েছিল জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। আর অন্যজন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিলেন তাই তার সন্তান হয়েছিল পাণ্ডু, জীবনবিজ্ঞানের ভাষায় অ্যালবিনো, এখনও এদের দেখবে সমাজে, গোটা গায়ের রঙ সাদা এমন কি মাথার চুল বা ভ্রূর চুল সব সাদা, এগুলো degenerative disease, crisis of pigment, হয় এদের সন্তান হয় না অথবা হলেও বিভিন্ন genetic disorder নিয়ে জন্মায়। তাই পাণ্ডুর ঔরষে কিন্তু সন্তান হয়নি, পরবর্তীতে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে বিভিন্ন দেবতার ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করানো হয়েছিল। আমরা পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসছি। আজকের সমাজে যে অবক্ষয়, হিংসা, ঈর্ষা, ধৈর্যহীনতা, সহ্যহীনতা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে আবার মানবিক গুণসমূহ যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদির অভাব দেখা যাচ্ছে, এর কারণ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ শিশু জন্মাচ্ছে না। নানান সমস্যা নিয়েই একটা শিশু জন্মাচ্ছে। তাহলে সে বড় হয়ে কি করে সমাজের সমস্যা, দেশের সমস্যা, মানুষের সমস্যা দূর করবে, এবার প্রশ্ন, তাহলে কি ভারতবর্ষ বা পৃথিবী এইরকমই চলবে, না তাও নয়। এইখানেই মহাপুরুগণের ভূমিকা। তাঁরা মাঝে মাঝে এসে এই গড্ডালিকাপ্রবাহের রাশ টেনে ধরছেন। বাধ্য করছেন মানুষকে তার দিকে মুখ ঘোরাতে। ছবিতে দেখবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন আর গাভীগুলি ঘাস খাওয়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এখানে জীবসকল যেন গাভী, ‘কৃষ্ণ’ কথাটি এসেছে ‘কৃষ’ ধাতু থেকে যার অর্থ অকর্ষণ করা। তবে মহামানবের এই গুণটি থাকে, তিনি যে কোনভাবে তার কাছাকাছি আসা মানুষকে সহজেই তাঁর দিকে আকর্ষণ করতে পারেন। আর একবার আকর্ষিত হলে তিনি এমন নেশা ধরিয়ে দেন—যাতে ব্যক্তিটির যমুনার উজানে যাতায়াত বা ‘অভিসার’ শুরু হয়। তাই সাধারণ মানুষকে সঠিক পথ দেখাতেই মহামানবের আগমন। এইজন্যই তাঁদেরকে বলা হয় “অবতার”, কারণ তাঁরা অবতীর্ণ হন বা অবতরণ করেন। তাই তোমাদের অতটা চিন্তা নেই—যতটা তাঁদের দায় বা দায়িত্ব। শুধু তাঁর বা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, তাঁদের নির্দেশ মেনে জীবনপথে এগিয়ে চল। দেখবে ‘চরৈবেতি’-‘চরৈবেতি’ করতে করতে একদিন ঠিকই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।
জিজ্ঞাসু —ইউরোপীয় দার্শনিক ফ্রয়েড যে তত্ত্ব দিয়েছে সেটি ভারতীয় দর্শনের বিরোধী কি ?
গুরুমহারাজ—ইউরোপে পরিভ্রমণ করাকালীন ফ্রয়েড-তত্ত্বের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাকে । এখানে সব্য তুমিই বোধহয় প্রথম ফ্রয়েড নিয়ে আলোচনা করছে। আর ওদেশে বেশীরভাগ ছেলে-মেয়েরা, যারা আমার সাথে দেখা করতে আসত, সুযোগ পেলেই বিভিন্ন দর্শন নিয়ে আলোচনা করত। বিশেষত Sex- education এদেশে চালু নেই, কিন্তু ওদেশে ছেলে-মেয়েরা এই ব্যাপারে খুবই খোলামেলা। তাই ফ্রয়েডের ‘লিবিডো’ তত্ত্ব নিয়ে খুবই আলোচনা হয়েছে।
তবে আমি বহুবার বিভিন্নভাবে বলেছি যে, একমাত্র আর্য্যঋষিরাই চিন্তার জগতে সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, semitic বা অন্যান্যদের Perfection কোথায় ? সেই হিসাবে ফ্রয়েড তত্ত্বও অসম্পূর্ণ। ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে যাকে ‘আদিরস’ বলা হয়েছে ফ্রয়েড এটাকেই ‘লিবিডো’ বলতে চেয়েছে। সাংখ্যদর্শনে কপিলমুনি যে ভাবে জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যা তুমি পাবে কোথায় ? “লিবিডো তত্ত্ব” দিয়ে কপিলের সাংখ্য-মতকে প্রতিষ্ঠাও করা যায় না বরং এর বিরোধ করা যায়।
ফ্রয়েড বলেছে নর-নারীর যে সম্পর্ক তার মূলে রয়েছে “লিবিডো”, এমন কি মা-ছেলের মধ্যে যে স্নেহবন্ধন সেটিরও মূল লিবিডো ? ফ্রয়েড কামশক্তিকেই ‘লিবিডো’ বলতে চেয়েছে। ফলে কি দাঁড়াচ্ছে – যে নর-নারীর মধ্যে কামজ সম্পর্ক, ভাই-বোনের মধ্যে নিষ্কাম সম্পর্ক অথবা মা-ছেলের মধ্যে সহজ স্নেহের সম্পর্ক—সবেরই উৎস ঐ লিবিডো। দ্যাখো সব্য ভারতীয় ঋষিচিন্তার কাছে এইসব আজে বাজে যুক্তি টেকে না, আমি ইউরোপের ছেলে-মেয়েদের কাছে যুক্তি দিলাম যে, দ্যাখা গেছে যে, একটি গাভী কিংবা একটি মা হরিণী তার বাছুরকে রক্ষা করতে শিং উঁচিয়ে বাঘ বা সিংহকে তাড়া করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ সে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সন্তানকে রক্ষা করতে চাইছে। আবার অপর পক্ষে mating-এর সময় যদি আচমকা বাঘ বা সিংহ সেখানে উপস্থিত হয়, তখন ঐ স্ত্রী হরিণী বা গাভীটি প্রাণভয়ে পালাচ্ছে পুরুষকে ফেলে রেখে, তাহলে “লিবিডো তত্ত্ব” খাটছে কোথায় ?
শিলমাছ জলে থাকে কিন্তু বাচ্ছাপাড়ার সময় ডাঙায় ওঠে। ঐ বাচ্ছার লোভে মেরুশৃগাল, ভাল্লুক, নেকড়েরা সেখানে আসে। মা শীলমাছের লড়াই করার মত দাঁত বা নখ কিছুই নেই, তবু সে তাদের সাথে লড়াই করে করে সন্তানকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, অনেক সময় মারাও যায়। মানুষের ক্ষেত্রে তো এর ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে কর্তব্যের খাতিরে বা দেশের প্রয়োজনে নিজের সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে মা অপরের সন্তানকে রক্ষা করেছে। জীবজগতে এই যে মায়ের ভূমিকা—এটি স্নেহের প্রকাশ, একে কোন লিবিডোতত্ত্ব দিয়ে বিচার করা যাবে না।
প্রেম বা ভালোবাসাকে সাংখ্যদর্শন কত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এখানে বলা হয়েছে প্রেম বা ভালোবাসার organic দিকটার ভাব একই হলেও এর তিন ধরণের প্রকাশ ঘটে। এগুলি হল যথাক্রমে স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতি। স্নেহ সততই নিম্নমুখী অর্থাৎ বড়রা বা senior-রা ছোটদের প্রতি যে ভালোবাসা বা প্রেম দেখান, সেটিই ‘স্নেহ’ । শ্রদ্ধা ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ছোট বা junior-রা, senior-দের প্রতি যে প্রেম বা ভালোবাসা অর্পণ করে –তাই শ্রদ্ধা, আর প্রীতি সমানে-সমানে, বন্ধুভাব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই প্রীতিকেই “পীরিতি” বলা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :
“আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।”
তাহলে এখানে দ্যাখা যাচ্ছে প্রীতিকে দুইভাগে ভাগ করা হচ্ছে—নিজের সুখ, নিজের পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে এগুলি কামজ, কিন্তু বহুজন হিতায়— বহুজন সুখায় যে প্রীতি তা প্রেমজ। সাধারণ নর-নারীর ইন্দ্রিয়লিপ্সা চরিতার্থের জন্য পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ এটি কামজ। কিন্তু ভগবান বা ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষগণের আপামর জনগণের প্রতি যে প্রত্যাশাবিহীন ভালোবাসা এটিই প্রকৃত প্ৰেম ।
যাইহোক কথা হচ্ছিল প্রীতি তিন প্রকারের। স্নেহ, শ্রদ্ধা এবং প্রীতি। মজার ব্যাপার কি জানো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ভালোবাসা এই তিনভাবে প্রকাশিত হতে দ্যাখা যায়। স্বামী হয়ত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বয়স্ক আর স্ত্রী সেখানে ঠিক। opposite অর্থাৎ কমশিক্ষিত, un-smart, বয়সেও কম, সেখানে স্বামী, স্ত্রী-কে domi nate করবে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর ভাবটি হবে স্ত্রীর প্রতি স্নেহের আর স্ত্রীর ভাব হবে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার। এর উল্টো চিত্রও দেখতে পাবে যেখানে স্ত্রী স্থূলকায়া, দজ্জাল, অথবা উচ্চশিক্ষিতা,চাকুরীরতা, বাপের বাড়ীর দেমাক রয়েছে—কিন্তু স্বামীটি নিরীহ, গোবেচারা, ভদ্র-সভ্য, শরীরে কমজোরী সেখানে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহের ভাব আর স্বামীর স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব। দেখবে স্ত্রী কথায় কথায় বলে “ও কিছু বোঝে না, যা বলার আমাকে বল।” আবার প্রথম ক্ষেত্রের স্বামীরা কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথাও স্ত্রীর সাথে আলোচনা না করেই নিয়ে নেয়, পরে বলে “ও-আর কি বোঝে তাই ওকে কিছু বলিনি।”
কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি সমান-সমান মনোভাবাপন্ন হয় তখন বলা হচ্ছে প্রীতি। প্রীতি আবার তিন প্রকারে আসতে পারে (১) সঙ্গজ প্রীতি—সঙ্গজ অর্থাৎ কারও কাছাকাছি বা সংস্পর্শে থাকতে থাকতে তার প্রতি একপ্রকার প্রীতি জন্মে যায়, এটি সঙ্গজ প্রীতি। সঙ্গছাড়া হয়ে গেলেই এই প্রীতি আর টেকে না। ইংরাজীতে বলে out of sight, out of mind, অনেক ছেলে-মেয়ে অল্প বয়সে ভাব-ভালোবাসা করছে, বাড়ীতে জানাজানি হলেই বাড়ীর guardian ছেলেটিকে বা মেয়েটিকে দূরে মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী কোথাও কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এরমধ্যে যদি যোগাযোগ না হয় তাহলে এই ধরণের ভালোবাসা ৬মাস বা ১ বছরের মধ্যেই কেটে যায়। শাস্ত্রে এর উদাহরণ কুব্জার প্রেম। যেখানে কৃষ্ণসুখ বড় কথা নয় আত্মসুখটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়, ফলে বাসনা চরিতার্থ করতে বারবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফিরে ফিরে আসতে হয়। (২) গুণজ প্রীতি—নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ তৈরী হয় উভয়ের মধ্যে কারোর কোন না কোন গুণের জন্য। অর্থাৎ মেয়েটি ভালো গান গায় বা নাচে, ছেলেটি ভালো খেলে বা কবিতা লেখে বা ছবি আঁকে অথবা ছেলেটিই ভালো গান গায়—এইসব গুণের জন্য একজন অন্যজনের প্রেমে পড়ে গেল—এটিই গুণজ প্রীতি। এই প্রীতি প্রথমটির থেকে qualitative, এটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ীও হতে পারে—তবে যে গুণের জন্য এই প্রীতি সেটির ব্যত্যয় ঘটলে বা অন্য আরও কোন গুণীব্যক্তির সংস্পর্শে প্রথম প্রীতিটি কেটে যেতেও পারে। সাধক জীবনে এর উদাহরণ কৃষ্ণমহিষীরা। যারা কৃষ্ণের গুণমুগ্ধ হলেও যাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সম্ভোগেচ্ছা ছিল। এই প্রীতিতে সাধকের মুক্তিলাভ হয়, বৈকুণ্ঠস্থিতিলাভ হয় কিন্তু ভক্তিলাভ হয় না।
(৩) সবচাইতে শ্রেষ্ট প্রীতি নৈসর্গিক। প্রকৃতির সৌন্দর্য— যেমন পর্বতের গাম্ভীর্য, আকাশের অসীমতা, সমুদ্রের গভীরতা— উচ্ছলতা, অরণ্যের তন্ময়তা যখন কাউকে মুগ্ধ করে, তখন এগুলির প্রতি কারও যে নিবিড় অনুরাগ সেটিই নৈসর্গিক প্রীতি। এই প্রীতিই মানুষকে ঈশ্বরমুখী বা অধ্যাত্মমুখী করে তোলে। বিশালতার প্রতি প্রীতি থেকেই মানুষ ‘বিরাটের’ স্পর্শ পায়, এরপর হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর সন্ধানের প্রতি যাত্রার জন্য ‘গুরু’ এসে তার হাত ধরেন। সাধকজীবনের শেষ সোপানে এই প্রীতির আবির্ভাব ঘটে। তখন শুধুই কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, নিজ সম্ভোগেচ্ছা বর্জিত অবস্থা, মহাভাব অবস্থা, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ্লাদিনী-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা।
বৈষ্ণবগণ সঙ্গজ, গুণজ ও নৈসর্গিক প্রীতির নামকরণ করেছেন— সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা বা মধুর। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম মধুর অবস্থার চরম উৎকর্ষতার উদাহরণ। জয়দেব-পদ্মাবতী, চণ্ডীদাস-রজকিনী এঁদের প্রেমও চিরন্তন প্রেমের আদর্শ। এগুলি ছাড়াও অমর প্রেমকাহিনী হয়ে রয়ে গিয়েছে লায়লা-মজনু, বীর- জারা, হির-রঞ্ঝা ইত্যাদির কথা। অতি অবশ্যই জানবে এগুলির পিছনে রয়েছে বিশাল বিশাল আত্মত্যাগ। “আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা” নিশ্চয়ই নেই, তাই এগুলি কালের বুকে ঠাঁই করে নিয়েছে। চণ্ডীদাস লিখেও রেখে গেছেন, “রজকিনীর প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।” তবে কথা হচ্ছে কি জানো, ঠিক ঠিক ‘প্রীতি’ অবস্থায় দম্পতির যদি সন্তান হয় তাহলে সুসন্তান হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম প্রীতির সম্পর্ক না থাকলে মহাপুরুষের জন্ম হয় না। বিভিন্ন উচ্চ-উচ্চ আদর্শের ব্যক্তি যাঁরা জগৎকল্যাণের জন্য শরীর নিতে চান, তাঁরা অপেক্ষা করেন ঐ ধরণের দাম্পত্যজীবন-যাপনকারীদের জন্য। তাই যে কোন সমাজে যদি এই ধরণের নর-নারী বা দম্পতি প্রচুর থাকে যেখানে তাদের মধ্যে সমান-সমান ভাব বা চরম প্রীতির অবস্থা বিদ্যমান, তাহলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন এবং সেই সমাজের, দেশের তথা পৃথিবীর কল্যাণসাধিত হবে।
শাস্ত্রে বলেছে অক্ষয় সরোবর, প্রেম সরোবর, মানস সরোবর এবং কাম সরোবরের কথা। সাধারণ মানুষ বা জীবকুল কাম সরোবরের রস পায় এটি “রসাভাস”। এখানে প্রকৃত রসের একটু- আধটু ছিটেফোটা তাতেই জীবকুল মত্ত। এতটাই মত্ত যে, এতেই প্রাণ চলে যাচ্ছে তাও হুঁশ নেই। আর মানস বা প্রেম সরোবরে যেসব সাধকগণ রয়েছে তারা এগিয়ে চলেছে, হয়তো কেউ slip কেটে পড়ে গেল, আবার উঠে চলা শুরু করল। কিন্তু অক্ষয় সরোবরে পৌঁছালে—“কাম গন্ধ নাহি তায়।” নারী-পুরুষ পরস্পরকে ছুঁলেই সমাধিস্থ হয়ে যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজার সময় সারদা- মাকে ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। শাস্ত্রে বলেছে ‘রসো বৈ সঃ’ এই অবস্থায় রসাভাস নয় রসের “উল্লাস” হয়, রসোল্লাস। হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। তখন শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এই অবস্থার সন্ধান কি করে পাবে ? রসোল্লাসের ব্যাখ্যা ফ্রয়েডের “লিবিডো তত্ত্ব” কখনও করতে পারে ? “লিবিডো”-“লিবিডো” বারবার এই নামটা শুনে আমার মনে হয়েছে কোন ভারতীয় দর্শন থেকে কুলকুণ্ডলিনীর ব্যাপারটা ফ্রয়েড জেনেছিল। কুলকুণ্ডলিনীকে আদ্যাশক্তি বলা হয়েছে এটাকেই ও ‘লিবিডো’ বলে চালিয়েছে। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনীর রহস্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকায় সব গোলমাল হয়ে গেছে। এই যে
দ্যাখো, সাধারণ নর-নারীর যে প্রেম এটা প্রবৃত্তিজাত— একথাতো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু মানুষ অন্যান্য জীবের থেকে কিসে উন্মত চ—না সে প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির অধীনতায় না থেকে সে স্বাধীনতা চায় বা মুক্ত হতে চায়। এই স্বাধীনতাও তার সহজাত প্রবৃত্তি। তাহলে মানুষ কেন প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে –কেন সে আছ বা আবিষ্ট হয়ে থাকবে ? একমাত্র মানবের মধ্যে প্রকৃত প্রেম জাগ্ৰত হলেই আছন্নদশা কেটে যায়, মানব স্বাধীন হয়, মানুষের মানবজন্ম সার্থক হয়, মানবজীবনের চরম উৎকর্ষতা বা perfection লাভ হয়। এইগুলি ঋষিদের শিক্ষা – আলতু-ফালতু কিছু যুক্তিজাল দিয়ে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করাটা কোন ধার্মিক ব্যক্তির কাজ নয়। মানুষের সর্বতোমুখী কল্যাণ হোক—এটাই সাধু ব্যক্তির, ধার্মিক ব্যক্তির প্রার্থনা হওয়া উচিত। দ্যাখো, কত প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় আর্য্য-ঋষিরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে যজ্ঞের আগুন জ্বেলে তার চারিদিকে বসে অথবা সূর্যের দিকে মুখ করে সমবেতভাবে উদাত্তকণ্ঠে প্রার্থনা করত। “সর্বে ভবন্তুঃ সুখিনঃ।” অথবা ভূঃ শান্তিঃ, ভূবঃ শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ ইত্যাদি। তাহলে এটাই বুঝতে হবে, যিনি নিজে শান্তি পেয়েছেন তিনিই পারেন অপরকে শান্তি দিতে বা সর্বতোভাবে অপরের জন্য শান্তি প্রার্থনা করতে। যিনি আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন তিনিই পারেন অপরকে আনন্দ দিতে বা অপরকে আনন্দের সন্ধান দিতে। তাই আমাদের কাজ হবে আংশিক জ্ঞান না চেয়ে জীবনে পরিপূর্ণতা কি করে হয় তার জন্য ব্রতী হওয়া। আর সম্পূর্ণের কথা বলতে পারে একমাত্র বেদান্ত। তাই দর্শন যদি follow করতে হয় তাহলে বেদান্ত দর্শন follow করো, স্বামী বিবেকানন্দ পড়, দ্যাখো, যুবকরা যদি বিবেকানন্দ পড়তে শুরু করে তাহলে — যুবকদের চরিত্রই শুধু বদলে যাবে তা নয়, এই দেশটারও আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে ।