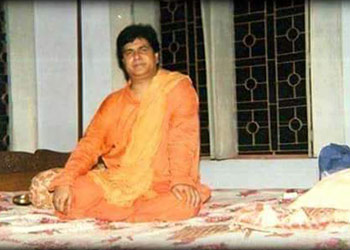জিজ্ঞাসু—আপনার আগেও তো ভারতে তথা পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন—তাঁরাও জ্ঞানের বাণী, প্রেমের বাণী ছড়িয়ে গেছেন, অধ্যাত্মশিক্ষা, সংযম ইত্যাদি নানান শিক্ষাও দিয়ে গেছেন। তাঁদের জীবন ও জীবনী হয়তো অনেকে আদর্শ করেছে, আবার অনেকে করেনি। জগৎ যে রকম সেইরকমই তো রয়ে যাচ্ছে তাহলে এবার আপনি ধর্মজগতের লোক হয়ে, একজন গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী হয়ে জগৎ বা জীবনের পরিবর্তনের জন্য কি করবেন ?
গুরুমহারাজ—দ্যাখো আমার গুরুদেব স্বামী রামানন্দ অবধূতজীও আমাকে পরীক্ষাছলে এ ধরণেরই কথা বলেছিলেন—জগৎ ‘জ্যায়সা কি ত্যায়সা, কুত্তা কা পুছ’ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই ! তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তিনি সবই জানতেন, তবু হয়তো আমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। জগৎ-সংসারের সৃষ্টি কবে হয়েছে, কিভাবে হয়েছে তার সঠিক সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত তো করা যায়নি। বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা অনুমান করে কিছু তত্ত্ব বা তথ্য দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু সৃষ্টি হবার পর এখন যে বিবর্তনের পালা চলছে এটা তো দেখতে পাচ্ছ। বিবর্তন মানেই তো এগিয়ে চলা—তাহলে জগৎ জ্যায়সা কি ত্যায়সা নয়। তোমার মনে হতে পারে যে, বিভিন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেছেন তাতে কি হল ? – কিন্তু কিছু হচ্ছে বইকি ! তোমার An- tenna-য় হয়তো তা ধরা পড়ছে না।
পরমানন্দ জানে যে, কি করলে সৃষ্টির কাজকে এগিয়ে নিয়েযাওয়া যায়। তাই যদি রাজনীতির দ্বারা মানুষের কল্যাণ হোত তাহলে আমি নিশ্চয়ই রাজনীতির নেতা হ’তাম। যদি বিশেষ কোন মঠ, মিশন জগতে বা মজহব্-এ যোগ দিলে মানুষের কল্যাণ হত তাহলে সেখানেই যোগ দিতাম, পৃথকভাবে পরমানন্দ মিশনের প্রয়োজন হত না। মানুষের ভালো করার জন্য প্রচুর সংগঠন, সংঘ, প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলিতেও কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু ধর্ম তো প্রাতিষ্ঠানিক নয়—ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে কাজের সুবিধার জন্য। প্রকৃতপক্ষে প্রাণই ধর্ম। প্রাণের দ্বারাই জীবের সৃষ্টি। পিতার শুক্র ও মাতার রজঃ নিয়ে প্রাণের ধারাতেই জীবের সৃষ্টি। আবার প্রাণবায়ুর ক্রিয়াশীলতাতেই জীবন আর প্রাণবায়ুর ক্রিয়াশীলতা বন্ধ হলেই মৃত্যু। এইভাবে প্রাণই জীবজগৎকে ধরে আছে। তাই জীবনের নিরিখে প্রাণই ধর্ম। আর শক্তিকে প্রাণরূপে ধরে ব্যাখ্যা করা যায় যে, জড়জগৎত্ত বিধৃত হয়ে রয়েছে প্রাণে। স্বামী বিবেকানন্দ এগুলি চমৎকার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। তন্ত্রের মা, বৈষ্ণবের রাধা, যোগীর ঈশ্বর, প্রতীক উপাসকের প্রণব-এ সবই প্রাণ। প্রাণাশ্রয়ী না হলে যে কোন ধর্মমত হিংসাশ্রয়ী ও বিষয়াশ্রয়ী হয়। একহাতে ধর্মপুস্তক অন্যহাতে তরবারি নিয়ে বা ছলে, বলে, কৌশলে অপরকে স্ব-ধর্মমতে আনা প্রাণাশ্রয়ী নয়। ধর্মের কোন প্রবর্তক বা প্রবক্তা হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তক বা প্রবক্তা রয়েছে কিন্তু সনাতন ধর্মের কোন প্রবর্তক নেই। আর ধর্মই সনাতন, যা নিত্য-শাশ্বত।
তবে ধর্মজগতের মহাপুরুষেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেছেন ঠিকই কিন্তু তা সংখ্যায় কম। ভারতবর্ষেই এর সংখ্যা সব- চেয়ে বেশী এবং প্রাচীনকাল থেকে এই পরম্পরা চলে আসছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার কেরল, বাংলা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে মহাপুরুষদের জন্মগ্রহণের হার বেশী। উত্তরভারত, বিহার, উড়িষ্যায় তুলনামূলকভাবে কম। পবিত্র আধার ছাড়া মহাপুরুষগণ শরীর নিতে পারেন না। ফলে যে অঞ্চলে মেয়েরা বা মায়েরা শরীর ও মনে যত শুচি বা পবিত্র ও আধ্যাত্মিক, সেই অঞ্চলে ততই ভালো মানুষ বা মহাপুরুষ জন্মানোর সম্ভাবনা বেশী। উত্তরভারতে ভালো মানুষ হয়তো রয়েছে কিন্তু বৈরাগ্যবান মানুষ খুবই কম। আমি ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে last উত্তরভারত গিয়েছিলাম আর যেতে ভালো লাগে না।
আমাকে তুমি যে গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী বললে, তা আমার কিন্তু গেরুয়ার প্রতি কোন টানই ছিল না। বনগ্রামে আসা অবধি আমার গেরুয়া-পরার বাসনা তৈরি হয়নি—আমি শুধু জানতাম আমাকে কিছু কাজ করতে হবে। বাল্যকাল থেকে ১১ বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণকালে আমি গেরুয়াধারীদের যে রূপ দেখেছিলাম তাতে বরং গেরুয়ার প্রতি বিরক্তই ছিলাম। বড় বড় মণ্ডলেশ্বর, পীঠাধীশ, মঠাধীশদের দেখেছি—এরা নানারকম অনাচার করে, মানুষকে হেয় করে। আবার যে সমস্ত উন্নত আধার বা মহাত্মাদের দেখেছি তারা হয় উলঙ্গ অবস্থায়, নয় সাদা কাপড়ে। স্বামী বাউলানন্দ সাদা কাপড় পরতেন, বৃন্দাবনের মহাত্মা যাদবানন্দও তাই। গুরুদেব রামানন্দজী উলঙ্গ ছিলেন। মৌনীবাবা, উড়িয়াবাবা উলঙ্গ ছিলেন। মহর্ষিরমণ, স্বামী বাউলানন্দের বিরজাহোম হয়নি, তাই বলে কি তাঁরা সম্যকরূপে অনাসক্ত ছিলেন না! সম্যকরূপে অনাসক্তিই সন্ন্যাস। আমি দেখেছি এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা প্রথম- জীবনে বা ব্রহ্মচারী অবস্থায় খুবই ভালো ছিলেন, চেতনার উত্তরণ ঘটছিল। গেরুয়া গ্রহণ করার পর অহংকার এসে গেল—পতন হোল । সাধুদের ক্ষেত্রে গেরুয়া একটা protection, যা ভগবানের বস্ত্র বা ভিগোয়া। গেরুয়া সমাজের মানুষদের সমীহ করতে শেখায়, সাধুর কাছ থেকে তারা নিজেকে দূরে রাখে আর সাধুরাও সেই সুবিধাগুলি পান। গেরুয়া সর্বদা সাধুদেরকে ত্যাগ ও অনাসক্তির প্রতীক বলে মনে করায় ও স্ব-স্ব আদর্শ পালনে সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমানে যে কেউ যে কোন প্রয়োজনে গেরুয়া পরে। বহু চোর, অপরাধী পুলিশের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য গেরুয়া পরছে। C ID বা C.B.I-এর লোকেরাও গেরুয়া পরে সব চোর ধরার চেষ্টা করছে। তাছাড়া বিভিন্ন কপট ব্যক্তি গেরুয়া প’রে সমাজে এত অন্যায়, অনাচার করছে যে, প্রায় শুনতে পাবে অমুক স্থানে অমুকবাবা public-এর হাতে মার খেয়েছে বা পুলিশ অমুক বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। মানুষও এদের দ্বারা বারবার প্রতারিত হয়ে বর্তমানে সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে।
ভগবান বুদ্ধ এবং স্বামী বিবেকানন্দ গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের পূর্ণ আদর্শস্বরূপ। আমার ব্রহ্মচর্য আশ্রমের আদর্শ শুকদেব, গৃহস্থ আশ্রমের আদর্শ রাজা জনক, বানপ্রস্থ আশ্রমের আদর্শ যাজ্ঞবল্ক্য আর সন্ন্যাসী আশ্রমের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। আচার্য শঙ্কর কিন্তু আদর্শ নয় কারণ তিনি আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ ছিলেন কিন্তু সামাজিকভাবে পূর্ণ ছিলেন না। বর্তমানে সন্ন্যাসীদের আদর্শ তাই স্বামী বিবেকানন্দ। যিনি বীরকণ্ঠে বলেছিলেন—এই দেশের একটা কুকুরও যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন আমি বারবার শরীর নেব। কি সাহস, কি তেজ, কি প্রেম, কি বীরত্ব! আজকের দিনে এটাই চাই। ম্যাড়মেড়ে ভাব আর মেয়েলি সুরে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা, নয়তো কীর্তনের ঢঙে গান গাওয়া বা কথকতা শোনানো -এসব সন্ন্যাসীদের কি প্রয়োজন ।
ভগবান বুদ্ধ আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে জনসাধারণকে ধর্মাচরণের অধিকার দিয়েছিলেন—ফলে সেই সময় সমাজে বৌদ্ধপ্লাবন এসে গিয়েছিল, এটা কত বড় বীরত্ব বা মহত্ত্ব একবার ভাব ! কিন্তু আচার্য শঙ্কর সাধারণকে ধর্মাচরণের অধিকার দেননি। সাধারণকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ফলেই ভারতবর্ষ দুর্বল হোল। যে সমাজে ধর্মাচরণ সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়, সে সমাজ শক্ত-সবল কি করে হবে ? তুর্কী, তাতার, মোগল, ইংরেজ এইসব জাতিগুলির কোন প্রাচীন ইতিহাসই নেই, নেই নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-দর্শন। কিন্তু ভারতবর্ষের সব ছিল–এর ইতিহাস ও সভ্যতা সুপ্রাচীন, এদেরই শিক্ষা- সংস্কৃতি, শিল্প-দর্শন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে ওরাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল ও সভ্যতার আলো ঐ সব জাতিকে দেখিয়ে- ছিল। প্রাচীন সভ্যতা বলতে গ্রীস, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতা, যা ভারত থেকেই গেছে। তবু ঐ সব জাতির কাছে ভারত ১০০০ বছর গোলামি করল। স্বামীজী গোটা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে ভারতের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে হৃদয়ে গভীর দুঃখ নিয়ে সাঁতরে কন্যাকুমারিকার সেই ছোট্ট পাথরখণ্ডটিতে বসে ধ্যানের গভীরে ডুবে গেলেন—জানতে চাইলেন কি এর কারণ ? যে জাতি সুপ্রাচীনকাল থেকে এত উন্নত—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অধ্যাত্মে, পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে, কতকগুলি uncultured জাতির হাতে সেই ভারতবর্ষের এই পরিণতির কারণ কি ? স্বামীজী দিব্যচক্ষে দেখলেন—শত-সহস্ৰ খণ্ডে বিভাজিত সমাজই এরজন্য দায়ী। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র—আবার ব্রাহ্মণদের উঁচু-নীচু ও শূদ্রদেরও স্তরভেদ এইরকম শত-সহস্র ভাগে সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ফলে যারাই বাইরে থেকে এসেছে সহজেই তারা দেশটা দখল করে নিয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে রয়েছে “একতাই বল”। পাঁচটা লাঠি একসঙ্গে বেঁধে দিলে আর সেই বাণ্ডিল ভাঙা যায় না কিন্তু একটা একটা লাঠিকে পৃথক পৃথক ভাবে পটাপট ভেঙে ফেলা যায়। স্বামীজীর আগে আর একজন মহাত্মা এটা বুঝেছিলেন, তিনি হলেন চাণক্য। চাণক্য চেষ্টাও করেছিলেন চন্দ্রগুপ্তকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে এক ছত্রতলে আনা যায় কিনা। তিনি অনেকটাই successful হয়েছিলেন— যার ফলস্বরূপ আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন মহান রাজা অশোককে পেয়েছিলাম। যিনি ভারতবর্ষের আদর্শ—সত্য, ত্যাগ, প্রেম ও শান্তির বাণী পুত্র-কন্যা ও ধর্ম-প্রচারকের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যেটা ভারতবর্ষের বিশেষত্ব –রাজা অশোক বিদেশে ছেলে-মেয়েকে পাঠালেন – বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পাঠালেন কিন্তু সৈন্যদল পাঠাননি। অপরপক্ষে বাইরের যত গোষ্ঠী ভারতে এসেছে তারা প্রথমেই সৈন্যদল পাঠিয়েছে। এমনকি ইংরেজরাও ব্যবসা করতে এসেছিল বটে কিন্তু আত্মরক্ষার নাম করে সৈন্য রাখার অধিকার আদায় করে নিয়েছিল।
তবে আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম যিনি ‘ভারত- ভাবনা’ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বক্তৃতায়, লেখায় ‘হে ভারত!’ —এই সম্বোধন করলেন। সমস্যার বীজ কোথায় তা বুঝতে পেরে তিনি চেয়েছিলেন তার মূল উৎপাটন করতে। তবে তিনি কতটা successful হয়েছিলেন তার পরিমাপ বাটখারা দিয়ে বা ইঞ্চি মেপে আমি করতে যাব না। এসব সমালোচকদের কাজ- তোমাদের কাজ, তোমরা ওসব কর। আমি শুধু তোমাদের কাছে ২৫০০ বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জগতের বিবর্তনটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন মহাপুরুষ শরীর নিয়েছেন, কাজ করেছেন, কাজ সমাপনান্তে তাঁরা চলে গেছেন। এবার তিনি কি করে গেলেন, সমাজকে কি দিয়ে গেলেন, সেটা তোমরা কি বুঝবে ? স্বামীজী শরীর ছাড়ার আগে গুরু-ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— বিবেকানন্দ কি করে গেল, তা আর একটা বিবেকানন্দ এলে বুঝতে পারতো! তাহলেই ব্যাপারটা বোঝ একবার !
দেখ, যে কোন দর্শন বা যে কোন ধর্মমতের উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়, কিন্তু আদর্শেই যত গোলমাল। ইসলাম বর্তমানে নানা ভাগে বিভক্ত, খ্রীষ্টানসমাজ আরও বেশী, বৌদ্ধসমাজ শতধা বিভক্ত, হিন্দুসমাজের তো অবস্থা দেখছই। তাহলে সাধারণ মানুষ কি ভরসা পাবে ! বাপ-ঠাকুর্দা ধর্মাচরণ করে এসেছে তাই অনেকে পরম্পরা বজায় রেখেছে। কিন্তু আধুনিক ছেলে-মেয়েরা ধর্মাচরণ মানছে না। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া সব মহাদেশের কথাই বলছি আর সব ধর্মমতের কথাই বলছি – ইসলামিক রাষ্ট্র communist হয়ে যাচ্ছে, খ্রীষ্টান দেশগুলির যুবকেরা হিপি কিংবা punk হয়ে যাচ্ছে, আর ভারতে যে কি হচ্ছে তার নাম দেওয়া যাবে না। তাহলে এখন উপায় ! দর্শন রয়েছে, ধর্মাচরণ রয়েছে, সংঘ-মজহব-মঠ-মিশন-চার্চ-মন্দির রয়েছে—তবু কেন young generation-এর এই অনীহা ? উত্তর একটাই—উপযুক্ত আদর্শের অভাব। ছেলে-মেয়েরা কোন filmstar অথবা player অথবা কোন rockstar কে আদর্শ করছে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখো—ধর্মজগতের আদর্শ কোথায় । তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজকে ধর্মমুখী বা অধ্যাত্মমুখী করতে গেলে ধর্মজগতের কোন আদর্শ মানবের প্রয়োজন, যিনি নিজ জীবনে ধর্ম অনুশীলন করে জগতের সামনে নিজেকে তুলে ধরবেন। অর্থাৎ জগৎ তাঁর শিক্ষাই মেনে নেবে—যিনি নিজ জীবনে সেই শিক্ষাকে অনুশীলন ও যোজনা করেছেন এবং তার ফললাভ করেছেন। ধার-করা বিদ্যা, মুখস্থ বিদ্যার কচকচানি আর ব্যাখ্যা আধুনিক মানুষ শুনতে চায় না। এখনও দেখবে যেখানে কথকতা হচ্ছে, পুরাণ-রামায়ণ পাঠ হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে—সেখানে কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অলসভাবে পা ছড়িয়ে বসে বসে সে সব শুনছে আর ‘আহা’ ‘আহা’ করছে, নয়তো চোখের জল ফেলছে। যুবকেরা সেখানে থাকবে কেন! তারা দেখবে যেখানে খেলাধুলা হচ্ছে —অন্তত সাইকেল খেলা, নাহয় কসরৎ প্রদর্শন, শরীর প্রদর্শন অথবা নাচ-গান হুল্লোড় চলছে সেখানে ভিড় জমিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই প্রচলিত রাস্তা থেকে সরে গিয়ে এক ক্ষীণজীবী যুবককে গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলতে বলেছিলেন। আর এটাও বলেছিলেন যে, শরীর মজবুত হলে তবেই গীতার মর্মার্থ ভালোভাবে বোঝা যাবে। যাইহোক আমার গুরুদেব রামানন্দ অবধূত বলেছিলেন : ‘পরম্পরার গোলাম হয়ো না কিন্তু পরম্পরাকে মেনে চলো।” তাই তাঁরই নির্দেশানুসারে আমাকে এসব পরতে হয়েছে। যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান সন্ন্যাসীদের আদর্শ—তিনিও গেরুয়া পরেছিলেন তাই আমি গেরুয়া পরলাম সন্ন্যাসীদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার জন্য। এটা ভারতের কৃষ্টিতে রয়েছে যে, বারবার সম্রাটের রাজমুকুট সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হয়েছে—তাহলে সেইরকম আদর্শবান সন্ন্যাসী হলে আজও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। আর পরমানন্দ কি করবে ? সে জানে মানুষকে পরিবর্তন করতে হলে তার বিচারের ধারাকে পরিবর্তন করতে হবে—তবেই মানুষ পরিবর্তন হবে। সে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে।
মঠাধীশদের কথা যা বলছিলাম তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, তাঁর কথা বলছি শোন : বারাণসীর এক মঠাধীশ তিনি, রুপোর সিংহাসন, সোনার খড়ম, হাতে কানে-গলায় সোনার অলঙ্কার, তাতে আবার হীরে বসানো। তিনি বেদান্তী-সন্ন্যাসী — বেদান্ত চর্চা করতেন, অনেক ভক্ত শুনতেও আসতো। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললাম, দেখলাম তিনি সকলকে ‘প্রাণিমাত্র’ বা ‘জীবমাত্র’ বলে সম্বোধন করছেন আর নিজেকে বলছেন ‘প্রভু’। ওনার সেবকেরা সকলেই ওনাকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করছেন। কেউ তা না করলে তিনি বিরক্ত বোধ করছেন। আমি তখন পরিব্রাজক বালকশরীর। উনি আমাকে উপদেশ দিলেন— “ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না যে কোন একটা রাস্তা ধরো, দিয়ে চুপ করে এক জায়গায় বসো। ” সেখানে ওঁর ভক্তরাও অনেকে ছিল তাই আমি চুপ করে বসে রইলাম। উনি আমাকে উদ্দেশ্য করে আবার বললেন, “কি হল চুপ করে আছ কেন—কিছু কথা বল ?” আমি সবিনয়ে বললাম, “একটা কথা বলব ?” উনি বললেন, “হ্যাঁ-হ্যাঁ, বল।” আমি বললাম— ‘আমি তো রাস্তা খুঁজতেই পথে বেরিয়েছি, আমি সেই রাস্তা পেতে চাই যা আমাকে ঈশ্বরের মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আপনার যদি সেই রাস্তার সন্ধান জানা থাকে তাহলে আমাকে বলে দিন। তবে হ্যাঁ, আমি এমন রাস্তার সন্ধান চাই না যা আমাকে আপনার মতো এমন জায়গায় পৌঁছে দেয় যা দিয়ে পীঠাধীশ, মোহন্ত ইত্যাদি পদ অথবা রুপোর সিংহাসন, সোনার খড়ম, অলঙ্কারাদি লাভ হয় আর কথায় এবং কাজে দুস্তর ব্যবধান থাকে।
উনি বললেন, ‘এখন চলে যাও, পরে কথা হবে।’ ওখানে যারা ভক্তমণ্ডলী ছিল, উনি তাদের উদ্দেশে যে কথাগুলো বললেন সেটা আমি যেতে যেতে শুনতে পেলাম। উনি বলছিলেন—“সিদ্ধ হ্যায়, বালক শরীরমে ঘুমৃতা হ্যায়। উনকো বলনে কা হক্ হ্যায়—ইসি লিয়ে বোলা।” উপস্থিত ব্যক্তিরা মোহন্তর সিদ্ধ চেনার ক্ষমতা দেখে হয়তো আরও অবাক হল, তাদের তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়তো আরও বেড়ে গেল। —এটাই চালাকি, আর এই যে ভণ্ডামি, আমার এটার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ছিল, যিনি প্রতিদিন বেদান্তপাঠ করছেন, বলছেন “সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম” —অথচ ছোট-বড়, উচ্চ-নীচের পার্থক্য দেখছেন ! বেদান্তে শূদ্র-ভদ্র, ধনী-নির্ধন, পাপী-পুণ্যবানের পার্থক্য কোথায় ? যেখানে জীব আর জড়েরও পার্থক্য থাকছে না, সেখানে উচ্চ-নীচ, জাত-পাত, সাধু-গৃহী এইসব sentiment সৃষ্টি করে সমাজের সর্বনাশ করা ছাড়া আর কি হচ্ছে !
এই যে পরম্পরা চলে আসছে সাধুসমাজে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, এই যে ধর্মের নামে ভণ্ডামি–এর ফলেই সাধারণ মানুষ সমাজের উচ্চবর্গের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছিল। কারণ উচ্চবর্গেরা সাধুসমাজ বা ব্রাহ্মণদের দলে টেনে রেখে বেশ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল আর বঞ্চিত হচ্ছিল সাধারণ মানুষেরা। ফলে বিদেশীদের হাতে চলে গিয়েছিল ভারতবর্ষ। উচ্চবর্গের মাইনে করা সৈন্যরা হয়তো লড়াই করেছে কিন্তু সাধারণ মানুষ দেশরক্ষার জন্য কাস্তে-কোদাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—এমন তো কোথাও হয়নি। যাইহোক, বারাণসীতেই আবার দশাশ্বমেধ ঘাটে কামরূপ আশ্রমে দেখেছি—রান্নাবান্নার বা সাধুদের খেতে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, আশ্রয় মিলবে কিন্তু আহার নয়। যারা ওখানে permanent থাকেন তাঁরা, আবার যাঁরা ঘুরতে ঘুরতে এসে আশ্রয় নেন, তাঁরাও মাধুকরী করে তাঁদের প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ করে নেন। আমি দেখেছি একটুখানি আটা হয়তো কোন সাধু পেয়েছে তা সেটাকেই জল ঢেলে ২/৩ টে লেট্টি করে, ধুনির আগুনে সেঁকে একটু চাটনি দিয়ে পরমানন্দে খেয়ে মনের সুখে ‘জয় শিব-শন্তো’ অথবা ‘রাম-রাম-সিয়ারাম’ ইত্যাদি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে বিশ্রামের ব্যবস্থা করছেন। অনেকে আবার ধুনির সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সৎসঙ্গে মশগুল হয়ে গেছেন। আমি ছোটবেলায় বেশ কয়েকদিন ওখানে থেকেছি, অনেক উন্নত সাধুদের সাথে সে সময় আমার যোগাযোগ হয়েছিল।
আবার দেখেছি এমন মঠ, যেখানে সাধুদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা আছে। ডাল-রুটি-ভাত-তরকারি, দই, মাঝে মাঝে ‘জিলাপি’ও হয়। সেখানে দেখেছি সাধুরা চর্ব্য-চুষ্য খেয়ে-দেয়ে হয়তো দু’ঘণ্টা খাবার নিয়েই আলোচনা চালিয়ে গেল। একদিন শুনলাম একজন বলছে, ‘রোজ করলার তরকারি কি ভাল লাগে ? খাবার আস্বাদনের ভালোলাগাটাই যদি উদ্দেশ্য ছিল তাহলে সংসারাশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাসাশ্রমে আসা কেন ! ওখানেই তো বেশ ভালো ছিল ! সম্যকরূপে অনাসক্তিই সন্ন্যাস । তাই সম্যকরূপে অর্থাৎ শুধু খাওয়া বা শোওয়া ইত্যাদি একটা-দুটো বিষয়ে নয় সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে— “সম্যকরূপে অনাসক্তি” কথাটা বলা হয়েছে, এইটা না এলে শুধু গেরুয়া পরে অহঙ্কার বাড়িয়ে লাভ কি ! গেরুয়া না পরাকালীন যেটুকু সঞ্চয় হয়েছিল সেটাকেও খরচা করা ছাড়া তো আর কিছু হয় না ! তাই মহাজনগণ বলেছেন, “সাধু সাবধান”!