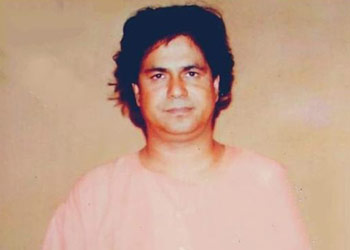জিজ্ঞাসু—এই যে অত দেশ ঘুরলেন, সে সব দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা বা বিশেষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে কি আপনার আলোচনা, মতবিনিময় বা বিতর্ক ইত্যাদি হয়েছে ?
গুরুমহারাজ—বিতর্ক হবে কেন—মতের আদান-প্রদান বলতে পারো। আর বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার সাথে তো যোগাযোগ হবেই—কেননা যেহেতু আমি গেরুয়াপরা একজন হিন্দু-সন্ন্যাসী ফলে আমার পরিচয়ই তো আমি অধ্যাত্মজগতের লোক। প্রথমেই লেনি আমাকে ও যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ মহাকারী সোসাইটি-তে নিয়ে গেল। বিয়ন ছিল আমার সঙ্গে। ওখানে পৌঁছে দেখি এক এক করে অনেক লোকই জমায়েত হল —একটা বিশাল হলঘরে। তারপর ওদের যিনি প্রধান, তিনি জাপানী ভাষায় বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। তারপর শুরু হল বিভিন্ন আসনে বিভিন্ন মুদ্রায় বা প্রক্রিয়ায় অনেকটা নামাজপড়ার মতো করে ঐ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করা, তারপর আবার কিছুক্ষণ ধ্যানও করাল। প্রধান যা বলছে বা যা করছে সকলে তাকে অনুসরণ করে তাই তাই করতে লাগল। বিয়ন চুপচাপ বসে থাকলেও আমি কিন্তু ও যা করতে বলছে তাই করতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এসব চলার পর অনুষ্ঠান শেষ হোল। দেখলাম প্রায় সকলেই গলদঘর্ম হয়ে হাঁসফাঁস করছে অর্থাৎ আসন-মুদ্রাগুলি করা বেশ কষ্টকর কাজ। অনুষ্ঠান শেষের কিছুক্ষণ পরই দেখলাম বেশ ভালোমত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। খাওয়ার পয়সাটা হয়তো সংস্থার সভ্যরা চাঁদা করে দিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু লোককে দেখলাম যারা শুধু খাবার লোভেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল এবং এরা প্রায় শেষের দিকে এল আর খাওয়া হয়ে গেলেই চলে গেল।
ওদের সংস্থার ব্যাপারটায় বুঝলাম যে, কোন এক জাপানি ভদ্রলোক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা, ফলে মন্ত্রাদি এখনও জাপানি ভাষায় উচ্চারিত হয়। চীনাদের ‘তাও’-এর মতো কিছুটা এদের আচার-আচরণ । তাছাড়া আরও মিল আছে—উভয় সংস্থাই বুদ্ধ-প্রভাব-যুক্ত। ক্রিয়াকর্মগুলিতে শারীরিক সুস্থতা আসার সম্ভাবনা, আর ঐ ধ্যানাভ্যাসের কিছু সুফল ছাড়া আধ্যাত্মিকতার গভীরতা তেমন কিছু দেখলাম না।
বিয়ন আর একটা Society-তে নিয়ে গিয়েছিল—এটাও এশিয়া সংস্থা। তবে পয়সার বিচারে বা ব্যবস্থাপনায় এরা বেশই উন্নত। ওদের সংস্থার ভিতরে ছোট ছোট অনেক ঘর আছে, ভিতরে প্রধানদের থাকার ব্যবস্থা আছে আর চারিদিকের ঘরবাড়ির মাঝে ছোট বাঁধানো একটা pool রয়েছে। স্বচ্ছ জল, জল বের করে দেবর বা ঢোকানোর সুন্দর ব্যবস্থাও রয়েছে। ওখানে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে হয়, কারণ এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওদের পৃথক পৃথক গ্রুপে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা যে সময় পৌঁছুলাম সেটা সন্ধ্যের দিক। দেখলাম সকলেই পৌঁছে এক- একটা ঘরে গিয়ে নিজের নিজের জামা-প্যান্ট ফটাফট হলে ফেলছে- ছেলে-মেয়ে, যুবকবৃদ্ধ সবাই। অল্প loose dress থাকতে পারে, তাতে আপত্তি নেই। তারপর সকলে ওই পুলের জলে নেমে পড়ছে – সেখানে এক হাঁটু থেকে এক বুক পর্যন্ত জল রয়েছে—জল গরম ব্রার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে ঠাণ্ডা জল নয়। ওখানে খালি গায়ে খানিক ডুবে থাকলে সারাদিনের ধকলে শরীরটায় বেশ আরাম পাওয়া যায়। যাইহাক আমরা ওদের প্রধানের সঙ্গে আগেই আলাপ করেছিলাম। ওখানে আমার পরিচয় করানো হোল যে, আমি একজন ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী — ভারতীয় যোগ পরম্পরার একজন। শুনে উনি বললেন, ‘তাহলে আজকের অনুষ্ঠান আপনিই চালিয়ে দিন’। ‘আমি বললাম, দেখুন, আমি আপনাদের সংস্থার কাজকর্ম দেখার জন্যই এসেছি—আপনাদের কিছু শেখাতে আমি আসিনি। সুতরাং অনুগ্রহ করে আপনার practice আপনি শুরু করুন। আমরা একটা উঁচু বেদীতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম যে, একঘণ্টার ক্লাসে কি যোগ শিক্ষা হয়। প্রধান এসে pool-এর ধারে একটা উঁচু মঞ্চে দাঁড়ালেন —সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলো নিভে গিয়ে শুধু রঙীন dim light জ্বলতে লাগল—পরিবেশটা যেন এক মায়াময়, স্বপ্নময় হয়ে গেল। প্রধান কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। তারপর তিনি সকলকে শান্ত হয়ে ঈষদুষ্ণ জলে গা ডুবিয়ে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, “আপনারা সকলে নিজেদের বয়স, শিক্ষা, position, status সব ভুলে যান—ভুলে যান—ভুলে যান। ” তারপর কিছুক্ষণ বিরতি, বিরতির পর একটা সুন্দর music-ও বাজতে লাগল তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন, “আপনারা আপনাদের অতীতের দিকে ফিরে যান—ফিরে যান—ফিরে যান । ভাবুন আপনারা সকলেই কিশোর বা কিশোরী।” কিছুক্ষণ পর আবার বলতে লাগলেন, “ভাবুন আপনারা বালক বা বালিকা, উচ্ছল-প্রাণচঞ্চল, সব সময় লম্পঝম্প করছেন – ভাবুন, ভাবতে থাকুন।” কি আশ্চর্য ! দু’একজন বৃদ্ধলোক দেখি জলের মধ্যে লাফালাফি করতে লাগল— হয়তো নিজেকে বালক ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলতে লাগলেন, “এবার ভাবুন আপনারা শিশু, মায়ের কোলে শুয়ে রয়েছেন—হাত-পা ছুঁড়ছেন আর আধো আধো কথা বলছেন—ভাবুন—ভাবুন।” “তোমাদের কি বলব, এই এখানে যারা আছে নগেন-টগেন, এরা যদি আমার সাথে ওখানে থাকতো, তো আমি হেসে গড়িয়ে পড়তাম আর নগেনের যে কি হত !” তারপর হল কি জানো, প্রায় সমস্ত লোকই জলে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল আর আধো আধো কিছু কথা অস্ফুটে বলতে লাগল, কেউ কেউ আবার ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদতেও লাগল । এরপর উনি বলতে লাগলেন, এবার ভাবুন আপনারা সকলেই শান্ত হয়ে, নিশ্চেষ্ট হয়ে মায়ের গর্ভে রয়েছেন, ভাবুন—ভাবতে থাকুন, শান্ত হয়ে যান—শান্ত হয়ে যান। সকলেই জলে গা ডুবিয়ে শান্ত হয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য
—প্রায় ১০-১৫ মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে আলো জ্বলতে লাগল আর সকলেই একে একে উঠে এসে নিজের পোশাক পরতে লাগল—কিন্তু তখনও দেখলাম কেউ কেউ উঁ-উঁ করে কাঁদছে, অথবা বালকের ন্যায় লাফাচ্ছে। আমি ওখানে দু’একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এই সংস্থায় যোগ শিখতে এসে তোমার কি উপকার হয়েছে ? ওদের বেশীরভাগই বলল—সারাদিনের ক্লান্তি এখানে এলে নাশ হয়ে যায় আর তাছাড়া fast life-এর যে competition আর তার জন্য বেড়ে ওঠা tension, তা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যায়। ওদের কেউ সপ্তাহে একদিন, কেউ পনেরো দিনে একদিন এই centre-এ আসে এবং ঐ ক্রিয়াটি করে। একটা ব্যাচ্-এর course সম্পূর্ণ হলে আমি প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি যোগ ? উনি বললেন এটা ভারতীয় যোগবিজ্ঞানের যোগ। আমি আর কোন বিতর্ক করলাম না। তবে শুধু ওখানে নয় অন্যত্রও দেখলাম ভারতবর্ষের যোগকে ভাঙিয়ে বহু মানুষ বহুভাবে করে-কম্মে খাচ্ছে।
এছাড়া আমি মহেশযোগীর বিভিন্ন যোগ Centre-এ গিয়েছি, Theosophical Society-তে গিয়েছি, ISCON-এ গিয়েছি, খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন ধর্মীয় সভাতেও গিয়েছি। ইউরোপ ঘুরে দেখলাম কি, ভারতে বিভিন্ন ধর্মের বোধহয় অত শাখা বা সংস্থা নেই যা ওইসব দেশে রয়েছে। আর সকলেই মোটামুটি চালাচ্ছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে দুটি ভাগ ক্যাথলিক আর প্রটেষ্টান্ট। এর মধ্যে আমেরিকানরা ক্যাথলিক আর ব্রিটিশরা প্রোটেষ্টান্ট। এছাড়া ওখানে লুথারিয়ান, কেলভিনিয়ান, আর্মেনিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন মতের চার্চও রয়েছে। ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপ। আর প্রোটেষ্টান্টদের প্রধান হল আর্চবিশপ। ক্যাথলিকদেরও আর্চবিশপ পদ রয়েছে যাঁরা পরবর্তীকালে Vatican city-তে থাকার অধিকার পান বা পোপ হিসাবে নির্বাচিতও হতে পারেন। আমার সাথে আলাপ হয়েছিল একজন আর্চবিশপের, ওনার নাম ফাদার ফ্রেডরিক। সাধারণত ক্যাথলিক ফাদাররা খুবই গোঁড়া প্রকৃতির হয়—ইনি কিন্তু সে রকম নন। উনি প্রথম যখন ভাটিক্যান সিটির Library-তে ঢোকার অনুমতি পেয়েছিলেন, তখন উনি প্রাচীন কিছু manuscript থেকে এমন কিছু তথ্য পান যা ভারতীয় উপনিষদের সঙ্গে মেলে। এটা পাবার পর উনি পোপ জন্ পল্-কে সরাসরি এ নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। পোপ ওকে বলেন যে, তুমি যা আজ জানছ তা আমি আরও ২০/৩০ বছর আগে জেনেছি। কিন্তু আমি যেমন আমার পূর্বসূরিদের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে চলেছি—তুমিও সেইরকম চল। এতেই আমাদের এবং সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের মঙ্গল।
আমি ওনাকে দুটো জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললাম যীশু নিজে বাইবেল লেখেননি, বাইবেল লেখা হয়েছিল যীশুর মৃত্যুর পরে আর তা ছাপা অক্ষরে মানুষের কাছে আসে তাঁর মৃত্যুর প্রায় কয়েকশ বছর পরে। অথচ বর্তমানের লিখিত New Testament-কে একমাত্র প্রামাণ্য ধরে, সবকিছুই সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হয়। এতে কি যীশুর অবমূল্যায়িত হয় না ? উনি শান্ত গলায় বললেন—আমার পূর্ববর্তী ফাদারেরা যা সিদ্ধান্ত করে গেছেন, তাই আমারও গ্রহণীয়। নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা গ্রহণ করার কোন অধিকার আমার নেই ?
এরপর আমি ওনাকে বললাম, আপনার গলায় ঝোলানো যে যীশুর মূর্তি রয়েছে ওটা তো white যীশু। আপনি কি জানেন যে, যীশুর গায়ের রঙ সাদা ছিল না, জেরুজালেম এলাকার লোক এশিয়ানদের মতো গায়ের রঙবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ yellowish। ওনার চোখও নীল বা কটা ছিল না, কালো ছিল। চুল বাদামি ছিল না, এশিয়ানদের মতোই কালো ছিল। বাইবেলে বর্ণিত যীশুকে তো আপনারা বদলে ফেলেছেন—তাহলে বাইবেল যীশু বিরোধী না হোক, যীশুর এই white concept- টাতো বাইবেল বিরোধী ? এ ব্যাপারে আপনি কি বলছেন ?
এই জিজ্ঞাসার উত্তরেও উনি আশ্চর্য রকমের শান্ত থাকলেন, একটুও বিচলিত না হয়ে উত্তর দিলেন—আপনার কথার মধ্যে হয়তো যুক্তি রয়েছে, কিন্তু আমার পদটা এমন যে, আমি নিরুপায়। পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই আমার একমাত্র কর্তব্য ও সঠিকধর্ম অনুশীলন। আর আমার বিশ্বাস—এতেই আমার স্বর্গে যাবার পথ সুগম হবে। আপনার সাথে আলাপ করে আমার খুব ভালো লাগল। পরে কখনও আপনার সাথে আমার আবার দেখা হবে, এই বলে উনি চলে গেলেন।
জিজ্ঞাসু—বিদ্যা স্ত্রী এবং অবিদ্যা স্ত্রী বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?
গুরুমহারাজ—সাধন, ভোজন এবং শয়নের সময় যে স্ত্রী স্বামীকে বিরক্ত করে এবং যে অপরের নামে নালিশ করে করে স্বামীকে উত্তেজিতকরে ও তাকে অবিবেকোচিত কাজ করতে বাধ্য করে, সেই অবিদ্যা স্ত্রী। আর যে স্ত্রী স্বামীকে ধর্মপথে সহযোগিতা করে, তাকে বিবেকী হতে সাহায্য করে, নিজের ত্যাগ, সংযম, ভালোবাসা দিয়ে—স্বামীর সমস্ত দুঃখকে নিজের বলে অনুভব করে তার বোঝা হাল্কা করে দেয়— সেই স্ত্রী-ই বিদ্যা স্ত্রী।
জিজ্ঞাসু—personified God-ব্যাপারটা কি ?
গুরুমহারাজ—ঈশ্বরকে যখন ব্যক্তিহিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কালীসাধকেরা কালীকে ‘মা’ হিসাবে দেখছেন, হজরত মহম্মদ আল্লাহকে “বন্ধু” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাই মহম্মদকে বলা হয় ‘হাবিব-এ রসুল’, যীশু God-কে ‘Father’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, এই যে ভাবনাসকল মহাজনেরা সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন, এতে করে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে ‘Person’ বা ব্যক্তি ভাবছে। কেউ ভাবছে তাঁর পুরুষশরীর—কেউ বা একধাপ এগিয়ে বলছে—তিনি অর্ধনারীশ্বর। তারপর একটা অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিও বানিয়ে ফেলে পুজো শুরু করছে। তাহলে সিদ্ধান্ত কি—“ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। / ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেবঃ।”— এটা কিছুটা Impersonal চিন্তার পরিস্ফুটন। তিনি জড়, তিনি জীব, তিনিই নিত্য, তিনিই লীলা, কারও কাছে তিনি personified কিন্তু কোথাও Impersonal.
চেতনার ঊর্ধ্বক্রমের শেষ তিনটি ধাপ হ’ল ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সমাধি দু’প্রকার, সবিকল্প এবং নির্বিকল্প। God, আল্লাহ্, ঈশ্বর, জীব, জীবন, জগৎ—এগুলি সবই সবিকল্প পর্যন্ত থাকে। নির্বিকল্প একাকার। সবিকল্পের কল্পনাই পরবর্তীতে মূর্তিতে রূপ নিয়েছে। সুতরাং মুসলিম বা খ্রীষ্টানদের যে মূর্তিপূজার বিরোধিতা, এটা টেকে না। প্রকৃত ‘অমূর্ত’কে বর্ণনা করাই যায় না। তবে বিকল্পকে আশ্রয় করে ‘মায়া’ অর্থাৎ জগৎজ্ঞান থেকে উত্তীর্ণ হতে হয় ‘একে’-র দিকে। এরপর ‘এক’-কেও অতিক্রম করে যাওয়াই নির্বিকল্প।
জিজ্ঞাসু—তাহলে ঈশ্বরই কি আর লীলা ব্যাপারটাই বা কি ?
গুরুমহারাজ—“অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং”- ‘চর’ অর্থাৎ dynamic এবং ‘অচর’ অর্থাৎ static. এই জড়জগৎ, জীবজগৎ—সমস্ত কিছুতে যিনি বা যা ব্যাপ্ত তাই ঈশ্বর। তিনি অণুতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন আবার বিভুতে ওতপ্রোত রয়েছেন। আর এর বাইরে কিছুই নেই। শাস্ত্র বলেছে— “যঃ ঈক্ষতে সঃ ঈশ্বরঃ”—যিনি সর্বব্যাপক, যিনি নিজেই নিজেকে দেখেন, যিনি নিজেই নিজেকে আস্বাদন করেন—তিনিই ঈশ্বর। কিন্তু বোঝাতে গিয়ে এই যে ‘তিনি’ বা ‘যিনি অথবা যে শব্দগুলো আসছে, এতেই মানুষ মনে করছে যে, ‘ঈশ্বর’ হয়তো কোন ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর একটা তত্ত্ব। যে তত্ত্ব সবকিছুতে অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ররূপে অণুতে অনুস্যূত আবার বৃহদাতিবৃহদ্রূপে ‘বিভু’-তে ওতপ্রোত, তাই ঈশ্বর। সবকিছু যে মূল principle-এ সৃষ্টি হচ্ছে বা হয়েছে, যা এখন রয়েছে (স্থিতি) এবং যা বিনাশপ্রাপ্ত (রূপান্তর, ক্ষয়, লয়) হচ্ছে বা হয়েছে, তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়েছে। এইজন্যই বলা হয়েছে যে, তিনি নিজেই নিজেকে আস্বাদন করছেন। যে কোন ধর্মমতের perception এটাই। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখো, যে কোন ধর্মমতের উন্নত মহাত্মারা এই একই কথা বলছেন। পৃথিবীকে নিচে থেকে দেখলে বৈচিত্র্যপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু মহাকাশচারীরা দেখে নীলাভ সবুজ গ্রহ। তেমনি ধর্মীয় বিভেদ মানুষের চেতনার নিম্নস্তরে।উন্নতস্তরের মহামানবরা একই বা অখণ্ডতত্ত্বকে বোধ করেন। তাহলে এখানে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে, ঈশ্বর যদি একটা তত্ত্বই হবে তাহলে সেই তত্ত্ব অবগত হতে গেলে কোন না কোন ধর্মমতের ধারা বা বলা ভালো ধর্মবিজ্ঞানের ধারা ধরতে হচ্ছে কেন—অন্য বিজ্ঞানের ধারা দিয়ে তা লাভ হচ্ছে না কেন ? এটা বুঝতে গেলে শারীরবিজ্ঞানকে জানতে হবে। শরীর পাঁচ প্রকার কোষ দিয়ে নির্মিত। যা বিবেক আশ্রয় করেই ভেদ করা যায়। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়—এই তিন প্রকার কোষের ক্রিয়া প্রায় সবজীবের মধ্যেই চলেছে। বিজ্ঞানময় কোষ বা বুদ্ধির জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারে মনুষ্যশরীরে। কিন্তু আনন্দময় কোষ কিভাবে বিকশিত হয়—brain cell-এর কোন অংশে সেই কোষের অবস্থান এবং সেই কোষগুলি কিভাবে activated হয়, তা কিন্তু শারীর- বিজ্ঞানীরা এখনও জানে না। ভারতীয় আর্যঋষিরা বহুকাল পূর্বেই এই রহস্য জেনেছিলেন, বলেছিলেন—‘পঞ্চকোষ বিবেকভেদাঃ’—বিবেককে আশ্রয় করে পঞ্চকোষ ভেদ করা যায়। এবার বিবেকাশ্রিত হতে গেলেই তো তোমাকে ধর্মাশ্রিত হতে হয় আর সত্য, ত্যাগ, প্রেম ও শান্তির বোধপ্রাপ্ত হতে হলে সদাচার, পরোপকার, ভালোবাসা ও সংযমের অনুশীলন করতে হয় জীবনে। পৃথিবীতে যে কোন ধর্মমত মূল যে চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলি হ’ল—সত্য, ত্যাগ, প্রেম এবং শান্তি। বাকী যা কিছু মানবিক মহৎ গুণসমূহ রয়েছে, সেগুলি এর মধ্যেই পড়ে যাবে। এবার চাই পথ এবং destination বা গন্তব্যস্থলের ঠিকানা। তাহলেই পথিক তার সাধ্যানুযায়ী ঠিকই একদিন পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থলে। এখানে বলা হয়েছে কুলকুণ্ডলিনীই পথ। মূলাধারকে আশ্রয় করে সহস্রার পর্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর যে ঊর্ধ্বগতি—সেটাই পথ। এইজন্য বলা যায় মত ভিন্ন ভিন্ন হোক—পথ একটাই। পথিক পথ পেল, চলতে শুরু করল, এবার চলার পথে তার যে অভিজ্ঞতা, সে তো সেই বলবে, কে কি বলছে, আগে কে কি বর্ণনা দিয়েছে, সেসব শোনার তো তখন তার আর প্রয়োজন নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, নেমতন্নের কার্ডখানার প্রয়োজন নেমতন্নবাড়ীর ঠিকানাটা পাওয়ার জন্য, ঠিকানা জানা হয়ে গেল—তারপর ওটাকে ফেলে দাও। এখানেও তাই হয়, সাধক নিজেই যখন পরম সত্যকে বোধে বোধ করেন তখন অন্যদের বোধের সাথে তাঁর মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন কি ? সেই পথে চলতে চলতে সবিকল্পের সীমা ছাড়িয়ে নির্বিকল্পে পৌঁছে ঐ সাধক বোধ করেন ঈশ্বরতত্ত্ব। আর যে শরীর দিয়ে ঐ তত্ত্ব লাভ হ’ল ওটি তখন দিব্যশরীর হয়ে যায়, তখন বিরাট ঈশ্বরতত্ত্ব ঐ শরীরকে ঘিরে ক্রিয়াশীল হয়। গ্রহবাসী ধন্য হয় শরীরধারী স্বয়ং ‘ঈশ্বর’কে হাতের কাছে পেয়ে। এইরূপ শরীরধারীকে ‘ভগবান’ নামে অভিহিত করা হয়।
আর ঈশ্বরের লীলার কথা বলছ। লীলা কি বোঝা যায় ! কথাতেই রয়েছে লীলা বোঝা ভার । লীলা চিরন্তন, যা কিছু দেখছ, জগৎ-জীবন-সংসার, সমাজ, বৃক্ষ-লতা, সবই তাঁর লীলা, বৈচিত্র্যই লীলা। আর ভগবান বা মহাপুরুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেই ভুল করে শুধু অনেকে ‘লীলা’মনে করে, এটা ঠিক নয়। সবই লীলা —লীলা চিরন্তন।
জিজ্ঞাসু—ভগবান বুদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন ও মা গৌতমীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, ভগবান শ্রীচৈতন্যও গর্ভধারিণীর মাথায় পা রেখেছিলেন— এগুলোও কি লীলা ?
গুরুমহারাজ—বললাম তো সবই লীলা। একটু আগে তোমাদের বলছিলাম যে, মানুষই ঈশ্বর হতে পারে সাধনজগতের শীর্ষে পৌঁছে, ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হয়ে। ওখানে দু’রকমের ব্যাপার ঘটে—একটা as- cending এবং অপরটা descending। Ascending হল সেটাই যা বিবর্তনের ধারা ধরে, এক-একটা জীবন অতিক্রম করতে করতে সাধক যখন সাধনার দ্বারা অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে আসে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাধারণত যেটা ঘটে সেটা হ’ল এই জগতেই আর এক জগৎ আছে—যেখানে উন্নত আধারসমূহ জগৎকল্যাণ বা জীবকল্যাণের জন্য সুক্ষাতিসূক্ষ শরীরে অথবা জ্যোতির্ময়শরীরে ঋষিলোকে অবস্থান করেন। জগতের প্রয়োজনে সেখান থেকেও পৃথিবীতে দু’একজন এসে মানবকল্যামূলক কাজ করে যান। আবার এমনও হয় যে, মহাজাগতিক principle-এর যে কথা বলছিলাম—সেখান থেকেই সরাসরি শরীরধারণ করেও কাজ হয়। এঁদেরকেই বলা হয় Descending । Descend অর্থাৎ অবতরণ বা ‘নেমে আসা’ যা থেকেই ‘অবতার’ কথাটি এসেছে।
এবার তুমি যে দুটি উদাহরণ দিলে সেগুলি Descending শরীর অর্থাৎ এঁরা ঈশ্বরের অবতার বা এঁরাই স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ। এঁরা ভগবান, তাই বলা হয় ভগবান বুদ্ধ বা ভগবান শ্রীচৈতন্য। ভগবান বুদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন ও মা গৌতমীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ঘটনাটা বলছি শোন। গৌতম গৃহত্যাগের পর দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। ওনার শরীর এত জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, শুধু চামড়া ঢাকা কঙ্কালছাড়া তাঁকে আর কিছু মনে হোত না। বৃদ্ধ শুদ্ধোদন সমস্ত খবরই রাখতেন আর ভাবতেন একদিন না একদিন এই রাজ্যপাট নিতে গৌতম নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তাই তিনি অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কষ্ট করেও রাজকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাই তো বলবতী হয়—মানুষ তো অনেক কিছুই ভাবে, কার্যকরী হয় কি ? হয় না। শুদ্ধোদনের ইচ্ছাও কার্যকরী হ’ল না কারণ গৌতম সাধনা ত্যাগ করলেন না বরং তার চরম শিখরে পৌঁছলেন অর্থাৎ বুদ্ধত্ব বা অর্হত্ব অর্জন করলেন। তাঁর নাম হ’ল গৌতম বুদ্ধ। এবার ভগবান বুদ্ধ তাঁর জ্ঞানরাশি যখনই মানুষের কাছে বিতরণ করতে লাগলেন তখন একে একে তাঁর চারিপাশে ভক্তের দল ভিড় করতে লাগল। আনন্দ, সারিপুত্ত আদি ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। সাধারণত তিনি কখনই কোন গৃহে রাত্রিবাস করতেন না—তা রাজগৃহই হোক বা সাধারণ পর্ণকুটীরই হোক। সেইজন্য দেখবে বৌদ্ধগ্রন্থে বিভিন্ন বন বা বৃক্ষতলের উল্লেখ আছে। শুধু বর্ষাকালে বুদ্ধদেব ২/৩ মাস কোন স্থানে থেকে যেতেন, তারপর শুরু হোত আবার পরিভ্রমণ। গোটা ভারতবর্ষ বুদ্ধ পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করেছিলেন, এই বনগ্রামেও ভগবান বুদ্ধ এসেছিলেন। এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বনগ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ন’কাকাদের বাড়ীর ওখানে তখন কাপালিকরা শিলামূর্তি শক্তিপূজা করত ৷ পশুবলি এমনকি নরবলিও হত, ভগবান বুদ্ধ সেই বলি বন্ধ করেছিলেন। এখন অবশ্য আর পশুবলি হয় না।
যাইহোক ঘুরতে ঘুরতে ভগবান বুদ্ধ একবার তাঁর জন্মভূমি কপিলাবস্তুতেও গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীদের দ্বাদশবর্ষ গৃহাভিমুখী হতে নেই, তারপর একবার দর্শন করতে হয়। তখন শুদ্ধোদন বৃদ্ধ হয়েছেন, গৌতমীও প্রৌঢ়া, রাহুল দ্বাদশবর্ষীয় বালক। দূতমুখে খবর পেয়ে শুদ্ধোদন সম্বর্ধনার সমস্ত আয়োজন করেছিলেন কিন্তু বুদ্ধ রাজবাড়ীতে ওঠেননি, তিনি গাছতলায় রাত কাটিয়েছিলেন। সকালে একেবারে রাজদরবারে ভিক্ষাপাত্র হাতে এসে হাজির। বৃদ্ধ শুদ্ধোদন তাঁকে সব কথা বলার পর রাজ্যপাট গ্রহণ করার কথাও বললেন। বুদ্ধ নির্বাক, শান্ত, ধীর- স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্দরমহলের অন্তরাল থেকে গৌতমী ও যশোধরা সব দেখছিলেন, যশোধরা রাহুলকে শিখিয়ে দিলেন যাও ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে “পিতৃধন’ চেয়ে নাও। রাহুল মায়ের কথামতো পিতার কাছে গিয়ে বলল, ‘বাবা, আমাকে পিতৃধন দাও।’ বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, ‘চীবর নিয়ে এস’। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পোশাককে চীবর বলে। চীবর আনা হলে তিনি রাহুলকে তা পরিয়ে দিলেন এবং মন্ত্র শেখালেন —’বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘম্ শরণং গচ্ছামি। ‘ রাহুলের এই পরিণতি দেখে গৌতমী আর থাকতে পারলেন না, ছুটে নেমে এসে বুদ্ধের চরণে পতিত হলেন। বুদ্ধ শান্ত — অচঞ্চল — ধীর ও স্থির। গোতমী বললেন, ‘তুমি রাহুলকেও নিয়ে যাচ্ছ, তাহলে আমরা এই শ্মশানপুরীতে কেন থাকবো ? আমাদেরকেও তোমার সংঘে স্থান করে দাও।’ ভগবান বুদ্ধ সংঘ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু নারীদের জন্য কোন স্থান রাখেননি, শুধু পুরুষদের জন্য সংঘের অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন গৌতমী ও যশোধরার জন্য তিনি পৃথকভাবে নারীদের জন্য সংঘ করার অনুমতি দিলেন। এবার পিতা শুদ্ধোদনের পালা। তিনি সবকিছু দেখে আর থাকতে পারলেন না। সিংহাসন থেকে নেমে এসে বুদ্ধের সামনে নতজানু হলেন। বললেন, “তুমি পুত্র, কিন্তু তোমার জ্যোতির্ময় মূর্তি, তোমার অপার্থিব শান্তভাব দেখে মনে হচ্ছে, তুমি শুধু আমার পুত্র নও, তুমি পিতা’, এরপর ভগবান শুদ্ধোদনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।
সুতরাং তুমি যে রকম বললে ব্যাপারটা ঐ রকম হয়নি। এটা একটা বিশেষ ব্যাপার—যা পরবর্তীকালের ইতিহাস। পুরুষোত্তম স্থিতিতে অর্থাৎ চরম ও পরম স্থিতিতে আর পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি লৌকিক সম্পর্কের স্থান কোথায় ? শচীমাতার ক্ষেত্রেও এইরূপই হয়েছিল। মহাপ্রভুর মধ্যে যখন মহাভাব প্রকাশ পেত তখন তিনি কখনও স্বয়ং বিষ্ণু, কখনও রাধা, কখনও কৃষ্ণ ভাবে থাকতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে ভাবস্থ অবস্থায় নৃত্য করতেন, সংকীর্তন করতেন, তাতে অনেকেই যোগদান করত—আনন্দ করত। এরপর তিনি শ্রীবাসের মন্দিরে প্রবেশ করতেন যেখানে বাইরের লোকেদের একদম প্রবেশ নিষেধ ছিল। শুধু অন্তরঙ্গরাই সেই ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেতো। এইজন্য বলা হয়েছে, ‘বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম-সংকীর্তন, অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে প্রেম আলাপন।’
শ্রীবাস মন্দিরে বিষ্ণুখট্টে অবস্থান করে প্রভু ভাবস্থ অবস্থায় কখনও বৈকুণ্ঠের কথা, কখনও বৃন্দাবনের কথা আলাপন করতেন। উপস্থিতজনেরা যা বুঝত বুঝত কিন্তু অপার্থিব আনন্দে তারা বিভোর হয়ে থাকত। মানুষের পেটে কথা থাকে না। যেভাবেই হোক এই ঘরের কথা শচীমায়ের কানে পৌঁছেছিল। শচীমাতা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে একসাথে খেতে দিতেন। নিত্যানন্দকে শচীমাতা বিশ্বরূপ জ্ঞান করতেন। আর নিমাই-এর যেন কোন ক্ষতি না হয়, নিতাই যাতে সর্বদা তাঁর পাশে পাশে থেকে তাঁকে রক্ষা করেন, তারজন্যও নিতাইকে যত্ন করতেন। শচীমা আহারান্তে একদিন নিতাইকে ধরলেন যাতে শ্রীবাসমন্দিরে রাত্রে কি ঘটনা ঘটে তা তাঁকে যেন দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। নিত্যানন্দ পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। মহাপ্রভুর কঠিন অনুশাসন আর ওখানে বাইরের কারও যাবার কোন অনুমতি নেই। কিন্তু তাই বলে গর্ভধারিণী কেন নয়—বিদ্রোহ করে উঠল নিত্যানন্দের মন। তবু ভোলাবার জন্য বললেন, ‘মা, ওখানে আমরা সকলে তোমার পুত্রকে নারায়ণজ্ঞানে পূজা করি।’ মা শিউরে উঠে বললেন, ‘সে কি রে। মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে পূজা ? আমার নিমাই-এর যে এতে ঘোর অমঙ্গল হবে — আমাকে একবার ওখানে নিয়ে যাবি আমি সকলকে বলে দেব যে, ও আমার পুত্র নিমাই —ও ঠাকুর-টাকুর কিছু নয়।’ নিত্যানন্দ বিশ্রামকক্ষে মহাপ্রভুর সাথে দেখা করলেন, আর মায়ের জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি দুটো জিনিস কখনই প্রত্যাখ্যান করেননি, অদ্বৈত আচার্যের প্রার্থনা আর নিতাই-এর অনুরোধ। এখানেই পার্ষদদের মধ্যে সামান্য ভেদ। স্বামী বিবেকানন্দ, হনুমান, নিত্যানন্দ, বলরাম এঁরা রুদ্র অবতার। হরি এঁদের পাশে পাশে থাকেন বলেই এঁরা সংযত, শৃঙ্খলাপরায়ণ থাকেন বা বলা যায় হরি এঁদের সংযত রাখেন। তা নাহলে এঁরা যদি স্ব-স্বরূপে চলে যান তাহলে হয় শান্ত-সমাহিত হয়ে সমাধির গভীরে ডুবে যাবেন, নাহলে ত্রিশূল চালিয়ে ত্রিশিরা নাশ করে দেবেন। জাগতিক, পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক যে সব আকর্ষণে জীবের জন্ম-মৃত্যু হয় তা এক নিমেষে নাশ করে দেবেন। ফলে জীব সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপপ্রাপ্ত হবেন। এটা ওঁরা করতে পারেন, মাথায় চাঁটি মেরে জীবের মুক্তি ঘটাতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টির তো এটা নিয়ম নয়। যোগমায়া এবং মহামায়ার জগৎ। সুতরাং সেই জগতের নিয়মের অনুশাসনে চলতে হয় বলেই হরির অবতার যাঁরা, তাঁরা রুদ্র অবতারদের শান্ত ও সংযত রাখেন। তাই অদ্বৈতের ভক্তিভাব আর নিত্যানন্দের ভাবের মধ্যেও পার্থক্য রাখতে হয়। অদ্বৈত মহাজ্ঞানী মহাপ্রভুর আগমন বার্তা তিনিই প্রথম জানতে পেরেছিলেন কারণ তিনি ভগবানের আগমনের জন্য প্রত্যহ গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাও করতেন। তাঁর ধারণা ছিল এই গঙ্গা-সুরধনীর ধারা ধরেই একদিন ভগবানের অবতরণ হবে, হয়েছিলও তাই। তাই শচীমাতার গৃহে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। বিশ্বরূপ যখন ছোট তখন থেকেই তিনি তাঁর পড়াশুনার ভার নেন। বিশ্বরূপের মধ্যেই তিনি ভগবানকে দেখতে চেয়েছিলেন কিনা কে জানে কিন্তু যে মন্ত্র তিনি কানে কানে রোজ তাঁকে শোনাতেন তাতে কিশোর বিশ্বরূপের আর গৃহে থাকা হল না। বিশ্বরূপ যখন অল্প বয়সী তখন বিশ্বম্ভর নিমাই-এর জন্ম হয়। অদ্বৈত ঠাকুর নিমাইকে দেখলেন—নামকরণও হল, পরে বিশ্বরূপের সন্ধানে বালক নিমাই দু- চারবার এসেও ছিল অদ্বৈতের টোলে। কিন্তু ভগবানের লীলা কি অত সহজ! প্রৌঢ় অদ্বৈতকে বারবার ধোঁকা দিয়েছে বালক নিমাই, আচার্যের ষোল আনা বিশ্বাস যে, শচীমাতার গর্ভজাত সন্তানই স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার, তিনি ধারণাও করেছেন তিনিই নিমাই, কিন্তু তবুও যেন ঠিক ধরতে পারছেন না। একটু দ্বিধা—এও এক মধুর লীলা ! “ও তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলে ধরা দেয় না।” আবার বলা হয়েছে, “ওরে কুশীলব, কিসের করিস গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে।” এরপর গৌরলীলার আরও চমৎকার প্রকাশ। নবদ্বীপেরই বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে, বিভিন্ন টোল থেকে পাঠ শিখে, নবদ্বীপে নিজেই পণ্ডিত হয়ে বসলেন, টোল খুললেন। আর যে সে পণ্ডিত নয়—নিমাই পণ্ডিত ! এত বিদ্যার অহংকার যে, যে কোন পণ্ডিত দেখলেই তার সাথে তর্কযুদ্ধ করতেন, তাকে পরাস্ত করে তার টিকি কেটে তাকে নবদ্বীপ থেকে তাড়াতেন। নিমাই-এর ভয়ে তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ তটস্থ হয়ে থাকতো। বহু পণ্ডিত নিমাইকে রাস্তায় দেখলেই পুঁথি গুটিয়ে উল্টোদিকে মুখ করে বসে থাকতো। পণ্ডিত-সমাজে নিমাই-এর নামে চি-টি পড়ে গেল ; অতি ভদ্র জগন্নাথ পণ্ডিতের এই ছেলে! সব খবরই পাচ্ছিলেন আচার্য অদ্বৈত, ঠিক মেলাতে পারছিলেন না, তবু আশায় আশায় বুক বেঁধে সময় কাটাচ্ছিলেন আর হরির কাছেই সবকিছু সমর্পণ করছিলেন। সমগ্র পণ্ডিতসমাজ সেদিন নিমাই-এর সঙ্গে অদ্বৈতকেও দুষেছিল। কিন্তু গয়া থেকে ফেরার পর যখন মহাপ্রভুর নতুন লীলা শুরু হ’ল— হল ভাবান্তর, তখন কোথায় অহংকারী নিমাই, তখন গলিত অহং— দ্রবীভূত অবস্থা ! কথায় বলে, ‘বিনয়ের অবতার’, মহাপ্রভুর এই রকম অবস্থা ছিল—যাঁকে দেখছেন তাঁরই পায়ে পড়ছেন, অঝোরে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, চারিদিকে কৃষ্ণ দেখছেন তবু কৃষ্ণবিরহে কাঁদছেন। চণ্ডীদাস মানস দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখে লিখেছিলেন—“যে করে কানুর আশ ধরে তার পায়। / সোনার পুতলি যেন ধুলাতে গড়ায়।” মহাপ্রভুর এই অবস্থা দেখে শচীমাতা কেঁদে আকুল, সকলে ব্যাকুল কিন্তু অদ্বৈতের লাফানি দেখে কে ! সবাইকে ডঙ্কা বাজিয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন, “বলেছিলাম না, এ-ই হরির অবতার, এবার দেখো কি লীলা করে লীলাময় !’
যাইহোক অদ্বৈতের কথা এইজন্য বললাম যে, মহাপ্রভু ওনার প্রার্থনা কখনও অমঞ্জুর করেননি। কিন্তু শচীমাতা আবার অদ্বৈতকে গৃহে ঢুকতে দিতেন না। কারণ ঐ যে বড় ছেলে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগী হবার পিছনে অদ্বৈতের হাত ছিল বলে বিশ্বাস। তাই তিনি ভয় করতেন যে, নিমাইও যেন ওঁর পাল্লায় পড়ে গৃহত্যাগী না হন। তাই তিনি বারবার অদ্বৈতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণাধিক তোমার গৃহে আর আমি থাকবো শান্তিপুরে তা কি হয় ! গঙ্গারঘাটে, শ্রীবাস অঙ্গনে নিত্য দেখা হত ওঁদের, যেখানে কোন খামতি ছিল না। এবার আবার শ্রীবাস-অঙ্গনের কথাতেই ফিরে আসি। ওখানে মহাপ্রভুর অনুমতি নিয়ে নিতাই নিয়ে এসেছিল শচীমাতাকে। নাম-সংকীর্তন হয়ে যাবার পর মহাপ্রভু যখন গৃহাভ্যন্তরে বিষ্ণুখটে মহাভাব অবস্থায় রয়েছেন, তখন ভাবস্থ অবস্থাতেই তিনি আদেশ দিয়েছিলেন—“ঘর থেকে শচীমাতাকে বের করে দিতে। ঘটনাটা কি ঘটেছিল, উপস্থিত সকলের তো ভক্তভাব, তাই তারা মহাপ্রভুকে স্বয়ং নারায়ণ দেখছে কিন্তু শচীমাতার তো পুত্রভাব, তিনি বাকীদের আচার-অনুষ্ঠানে বিরক্ত হচ্ছিলেন, তাই এই আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে মা-কে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঐ ঘটনার পর থেকে মায়ের মনে অনুতাপ হয়। তিনি অনুভব করতে থাকেন যে, তিনি যেন এক সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছেন। তাই তিনি নিতাইকে আর একদিন নিয়ে যাবার জন্য ধরলেন। সেদিন নিতাই মহাপ্রভুর অনুমতি ছাড়াই মাকে নিয়ে গিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। মহাপ্রভু ঘরে ঢুকেই বিষ্ণুখট্টে বসেই আদেশ করলেন, ‘বৈষ্ণব-অপরাধে অপরাধীকে ঘর থেকে বের করে দাও।’ সবাই এ ওর মুখ চাওয়া- চাওয়ি করছে, কেউ তো জানে না নিতাই-এর কম্মো। মহাপ্রভু গর্জন করে আদেশ দিচ্ছেন—সবাই ভয়ে কম্পমান, এমন সময় মা শচীমাতা তুলসী, চন্দন, পূজার উপচার নিয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন । তিনি সকলকে আশ্বস্ত করে, ভাবস্থ মহাপ্রভুর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে, তুলসী-চন্দন দিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন, পুষ্পাদি দিয়ে তাঁর অর্চনা ও পূজা করলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করে যখন প্রণাম করছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু তাঁর শ্রীচরণ শচীমাতার মস্তকে চাপিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : ‘আমি তোমার সকল বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষমা করলাম।’ এই হচ্ছে ঘটনা। এখানে বৈষ্ণব অপরাধ বলতে – মা শচীমাতা বৈষ্ণবদের নিন্দা করতেন, অদ্বৈতকে তো সহ্য করতে পার- তেনই না, নিতাই ছাড়া আর কাউকে বাড়ীতে ঘেঁষতে দিতেন না। এই নিয়ে নিমাই-এর সাথে শচীমাতার কথা কাটাকাটি হত। এই ঘটনায় তৎকালীন শাক্ত বা শৈবরা বেশ আমোদ পেয়েছিল। তারা রটাতো যে, নিমাইকে কৃষ্ণের অবতার বলছো—তা কই কৃষ্ণ বা রামের সঙ্গে তো মায়ের ঝগড়া কখনও হয়নি বরং কি মধুর সম্পর্কই না ছিল—তা তোমাদের অবতারের এ রকম ব্যবহার কেন ? বৈষ্ণবদের কাছে এসব শুনতে খুব কষ্ট লাগত। এইভাবেই বৈষ্ণব অপরাধ হয়েছিল।
মহাপ্রভুর ভাবজগতের লীলা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি, মহাপ্রভু এটা বুঝলেন, তাই তিনি নিত্যানন্দকে ভার দিয়ে বাংলা ছেড়ে চলে গেলেন। বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলা নবদ্বীপে প্রকট হয়েছিল। বৃন্দাবনের গোপীলীলাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ লীলা। গোপীদের যে সখীভাব তার তুলনা হয় না। দ্রৌপদীও ভগবানের সখী ছিলেন, এমনকি কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে ‘সখী’ বলে সম্বোধনও করতেন। তবু দ্রৌপদী গোপীলীলার স্বাদ পাননি। দ্রৌপদীর আহ্বানে ভগবান বস্ত্র জোগান দিয়েছিলেন, লজ্জা নিবারণ করেছিলেন আর বৃন্দাবনের গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করলেন, লজ্জাহরণ করলেন—তাই তিনি গোপীদের শ্রীহরি—এই রহস্য গভীর অনুধ্যানের দ্বারা বুঝতে হবে। উদ্ধব যখন মথুরা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিল, তখন দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘সখা আমাদের কথা বলে তো, আমাদের মনে রাখে তো ?’ আর গোপীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমাদের কৃষ্ণ কেমন আছে, কুশল তো ?’—এই তফাৎ, চণ্ডীদাস লিখলেন, “তোমারি কুশলে কুশল মানি”, এ বড় শক্ত ভাব ৷ সাধারণ ভক্ত এ ভাব পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ‘আমি’ থাকলে ‘তুমি’ আছ, শুধু ‘তুমি’—এটা বড় একটা হয় না। তাই বৃন্দাবনের গোপীলীলাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ লীলা। যেখানে জ্ঞানের ওপারে গিয়ে গোপীরা কৃষ্ণের সাথে লীলা করেছেন।
এইভাব শ্রীবাসের মন্দিরে মহাপ্রভু প্রকট করেছিলেন। আবার তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে উড়িষ্যার পুরীতে হ’ল গম্ভীরালীলা— গুপ্তলীলা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে সেটাকে প্রকট করলেন—মুহুর্মুহু সমাধিতে। কিন্তু কিছুটা আবার অপ্রকট ছিল, যেমন সবার হাতে খেতে পারতেন না, সব কথা সকলকে বলতে পারতেন না, লাটুকে বাইরে পাহারায় বসিয়ে রেখে ত্যাগী ভক্তদের নিয়ে আলাদা করে sitting করতেন। ঠাকুরের এই অপ্রকট ভাবগুলি হয়তো এবার প্রকট হবে। বর্তমান বৈষ্ণবরা মহাপ্রভুর এইসব ভাব একদমই নিতে পারেনি। নিত্যানন্দের শিক্ষা নিয়ে সেটাকেই মেনে চলার চেষ্টা করে। বৃন্দাবনে যাদবানন্দকে দেখেছিলাম রাত্রি ১-৩০ থেকে ভোর ৪-৩০ পর্যন্ত গোপালকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে। আমি সব দেখলাম, পাখা বন্ধ করলে বললাম—কি হ’ল ? ও ইঙ্গিত করে বাইরে যেতে বলল, বাইরে এসে বলল—“গোপাল ঘুমিয়ে পড়ল, এতক্ষণ গরমে ছটফট করছিল, তাই হাওয়া দিচ্ছিলাম।” এটা কে করে বলো তো ? মা করে সন্তানের জন্য। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে বা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে এটাকে ন্যাকামি মনে হবে। কিন্তু এটা বুদ্ধির বিচার নয়—এখানেই মানুষ ভুল করে, বুঝতে পারে না ব্যাপারগুলো কি হচ্ছে। আর বুঝতে না পেরেই সমালোচনা শুরু করে দেয়, পাণ্ডিত্য জাহির করে। এগুলো ভাব- জগতের ব্যাপার—যার সে জগতের সন্ধান নেই, সে কি করে বুঝবে ! প্রাণে প্রাণে সংযোগ হলে মৃন্ময়ী হয়ে যান চিন্ময়ী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদক্ষিণেশ্বরের ‘মা’ ভবতারিণীকে খাওয়াতেন, পূজা করতেন। লোকে দেখতো ঠাকুর নিজেই খাচ্ছেন ; নিজের মাথাতেই ফুল চাপাচ্ছেন—এটাই তো হয় ! এখানে ভাবজগতের গভীরে প্রবেশ করে প্রাণের সাথে প্রাণের সংযোগ হয়ে গেছে, অর্থাৎ drain কাটতে কাটতে সমুদ্রের সাথে সংযোগ ঘটে গেছে। তাহলে তাতে জোয়ার-ভাটা কি খেলবে না, নাকি সেই জল লবণাক্ত স্বাদযুক্ত হবে না ? ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকমই হয়। এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর দিয়েই সেই মহাশক্তি ক্রিয়া করত, এটাকেই বুঝতে হবে। সিনেমায় দেখায় যে, সাধক সাধনা করছে আর তার সামনে একটা আলোর বলয় সৃষ্টি হ’ল, সেটা আবার ছোট থেকে বড় হল, তারপর সেখান থেকে একটা খড়্গাধারিণী মূর্তি প্রকট হ’ল, তারপর হয়তো বলল, “বৎস, কি খবর !” এ রকমটা 1. কিন্তু বাস্তবে হয় না। এখানে যা কিছু হয় ভাবজগতে। স্থূল-জগতে তিনি ইচ্ছা করলে নিজেকে প্রকট করতে পারেন কিন্তু তার প্রয়োজন হয় না। ভাবজগতেই দেখা হয়, কথা হয়, ভাব বিনিময় করা যায়। আবার ভেদ অভেদে পরিণত হয়, তখন আর ভেদাভেদ থাকে না। তোমরাও তো অনেক কিছু শুনলে—এই ভাবজগতের রহস্য কি ভাবজগৎ দিয়ে ধরতে পারলে, ভেদাভেদ কি ঘুচল তোমাদের ? যদি ঘোচে তাহলেই জানবে মঙ্গল, এতেই জীবের অগ্রগতি হয়, চেতনার উত্তরণ হয়।