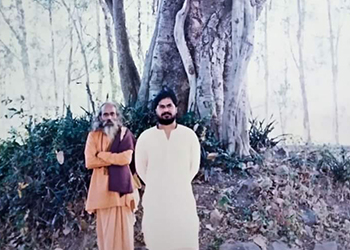জিজ্ঞাসু—উত্তরভারতে গঙ্গার মাহাত্ম্য নিয়ে বহু আশ্রমে পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি হয় আর গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করা হয়, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাংলায় গঙ্গার প্রতি সে ধরণের ভক্তি বা ভালোবাসা নেই। গঙ্গা তো সেই একই, তাহলে এ রকম মনোভাবের কারণ কি ?
গুরুমহারাজ–উত্তরভারত বলতে তুমি হরিদ্বার, ঋষিকেশ ইত্যাদি স্থানগুলোর কথা বলছ তো? হ্যাঁ, হরিদ্বারে গঙ্গামাতার মন্দির খুবই বিখ্যাত আর প্রতি সন্ধ্যায় গঙ্গার আরতি দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। গঙ্গার উৎসস্থলগুলিতে যেমন তুমি গঙ্গার মহিমা বা মাহাত্ম্য বর্ণনের আধিক্য দেখেছ তেমনি তুমি যদি দক্ষিণ- ভারতে নর্মদার উৎসস্থল অমরকণ্টকে যাও, ওখানে দেখবে বিভিন্ন মঠ, মিশন, ধর্মস্থলে নর্মদামাতার মাহাত্ম্য বর্ণনা হচ্ছে, নর্মদা-মাতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে সাধু-সন্তরা নর্মদা পরিক্রমা করছেন। বলা হয় ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। নদী এই দেশের মাতৃস্বরূপা। তাহলে মায়ের বন্দনা করবে না! উৎসমুখে নদীর জলধারা পবিত্র থাকে, পরিষ্কার ও নির্মল থাকে। আর এসব স্থান দুর্গম হওয়ায় সাধারণত সাধু-সন্তরাই সেখানে থাকেন—সংসারী মানুষেরা বসবাস করে না। তাই মাতৃরূপা নদীর ভূমিকা যে কতখানি, তার মর্যাদা তো এই ত্যাগী মানুষগুলোই দেবেন। তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষও নদীর প্রতি ভক্তিমান বা শ্রদ্ধাবান হবে। এতে কি হবে ? না নদীর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার বা দূষণ অনেকটাই বন্ধ হবে। যদিও সাধুদের এই প্রচেষ্টার বাস্তবরূপ খুব একটা কার্যকরী হয়নি। মানুষ কলকারখানা বা নগর-সভ্যতার বর্জ্যপদার্থ ফেলে নদীগুলোকে দূষিত করে ফেলছে। গঙ্গার কথা তো বলারই নেই—পৃথিবীর মধ্যে দূষিত নদীগুলোর অন্যতম। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় গঙ্গাদূষণ নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ তৈরী হয়েছে। মানুষের মধ্যেও চেতনা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু এসব করেও ফল কতটা হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। আসলে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা এত অধিক হয়ে গেছে আর গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে এতবেশী জনবহুল important নগর, শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে যে, গঙ্গাদূষণ রোধ করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। আগে বলা হত গঙ্গাজলে জীবাণু জন্মায় না আর এখন কলকাতার গঙ্গার জলে কীট কিলবিল করছে। গঙ্গার জলে যত পচা বর্জ্যপদার্থ, নর্দমার জল, পোড়াতেল-মোবিল, কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মিশছে আর এর ফলে জলে যে সমস্ত চুনজাতীয় যৌগ ছিল যা জলকে নির্মল রাখত, সেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে গঙ্গাজলের quality খারাপ হয়ে গেছে।
কিন্তু হরিদ্বার পর্যন্ত তো তেমন বেশী নগর নেই, কল-কারখানা নেই, তাই ঐ স্থান পর্যন্ত গঙ্গাজল নির্মল—পবিত্র। বহুপূর্বে গঙ্গোত্রী- হিমবাহ হরিদ্বার বা হরদুয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ওখানে ছিল গঙ্গার উৎস। আবহমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ার সাথে সাথে ওটি পিছোতে পিছোতে বর্তমানে গঙ্গোত্রী থেকেও আরও প্রায় ১৫ কিমি উপরে গোমুখে চলে গেছে। গঙ্গোত্রীতেও গঙ্গামন্দির রয়েছে, ওখানেও প্রত্যহ পূজা হয় এবং জাঁকজমকপূর্ণ-ভাবে আরতি হয়। ওখানেই ভগীরথেরও মন্দির রয়েছে। পুরাণে কথিত আছে যে, ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে এনেছিল। সগর রাজার বংশধর ছিল ভগীরথ। এরা ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের রাজা ছিল, ফলে নিজেদের এলাকাকে নদী দ্বারা সমৃদ্ধ করারও তাগিদ ছিল। বহুকাল পূর্বে অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধেরও আগের যুগে গঙ্গার জলধারা উত্তরপ্রদেশের খানিকটা অঞ্চল cover করে হরিয়ানা-রাজস্থান হয়ে, পুষ্কর তীর্থ হয়ে আরব সাগরে পড়েছিল। তখন ঐ নদীর নাম ছিল সরস্বতী। ফলে ভারতের পশ্চিম দিক তখন শস্যশ্যামলা ছিল এবং প্রচুর জনপদ, নগরী গড়ে উঠেছিল, সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। এরফলে সম্পদ ও খাদ্যের লোভে মধ্যএশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বিভিন্ন যাযাবর দস্যু ও অন্যান্য জাতিরা বারবার হানা দিতে লাগল, ক্রমাগত সংঘর্ষ ও নানা অত্যাচারে ঐ সব অঞ্চলে ভারতীয় রক্তের সাথে বিদেশীরক্ত মিশে বর্ণসংকর তৈরী হতে লাগল। আর তাদের অনেকে বিদেশীদের সাহায্য করতে লাগল এবং বহিঃশত্রুরা ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে লাগল। সেইসময় বিভিন্ন সাধু-মহাত্মারা তৎকালীন শক্তিশালী রাজা সগরকে অনুরোধ করেন গঙ্গার মূলধারাকে অন্যপথে ঘুরিয়ে দিতে যাতে ভারতের পশ্চিমসীমান্ত barren land-এ পরিণত হয় এবং বিদেশী আক্রমণ বন্ধ হয়।
সগর—দিলীপ—অসমঞ্জ — অংশুমান — ভগীরথ —এই পাঁচপুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গঙ্গার মূল ধারাকে ঘুরিয়ে দেবার কাজটি করেছিল। এতে প্রায় ১০০ বছরে ষাট হাজার শ্রমিক, ঠিকাদার, ইঞ্জিনীয়ার ওখানে কাজ করেছিল—সেটা ভাবা যায় ? এখনও সাধুরা শিবালিক range অতিক্রম করে কৈলাসের দিকে হেঁটে পরিক্রমা করে। ঐ পথে যাবার সময় যদি শিবালিকের যে কোন চূড়া থেকে গঙ্গার গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা যায় তো দেখা যাবে যে, উৎস থেকে বেরিয়ে গঙ্গা প্রথমে দক্ষিণবাহিনী হয়ে ৫০/৬০ কিমি চলে এসেছে, তারপর পুনরায় উত্তরবাহিনী হয়ে আবার ৪০/৫০ কিমি গিয়ে ধরাসতে এসে সমভূমিতে পড়েছে। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর ধারাকেও গঙ্গার ধারার সঙ্গে মেশানো হয়েছিল, যাতে গঙ্গার মূলধারাটির গুরুত্ব বাড়ে। এছাড়া অসংখ্য পাহাড়ি ঝরণা ও ছোট ছোট নদী মিলে গঙ্গাকে আরও পুষ্ট করেছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে গঙ্গার কন্যা পদ্মা, গঙ্গাকে বলা হয়েছে হরপ্রিয়া আর পদ্মাকে বলা হয়েছে শিবকন্যা। মুর্শিদাবাদে ফারাক্কার কাছে গঙ্গার মূলধারাটি পদ্মা নাম নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। শাখানদীকে এই অর্থেই কন্যা বলা হয়েছে। এবার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের পদ্মা মূলধারা হওয়া সত্ত্বেও এদিকের গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কেন ? আসলে শাস্ত্রে ভগীরথের যে গঙ্গা আনার গল্প রয়েছে তাতে গঙ্গা- সাগরের তৎকালীন বিখ্যাত সাধু বা মহাত্মা কপিল মুনির উল্লেখ আছে, তাই পশ্চিমবঙ্গের শাখাটিকেই ভাগীরথী নাম দেওয়া হয়েছে। তবে গঙ্গার মূলধারা হওয়ায় এবং আরও কিছু নদী এর সাথে মেশায় পদ্মা স্থানে স্থানে বিশাল চওড়া হয়েছে। আমি যখন বাংলাদেশ ঘুরেছি তখন দেখেছি আসিরিগঞ্জ থেকে ঢাকা যেতে মোটরলঞ্চে কয়েকঘণ্টা লেগে গেল। এপার-ওপার দেখাই যায় না।
যাইহোক ভারতের উত্তর বা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজা হওয়ায় সগররাজা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করতে হলে কোন বড় নদীকে এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত করতে হবে। সভ্যতা সদাই নদীমাতৃক। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, কোন সভ্যতা কোন না কোন নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। নদী থেকে যে শুধু সেচকার্যই হয় তা নয়, পণ্য বা লোক-পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা ইত্যাদির জন্যও নদী একান্ত উপযোগী। এছাড়া সেই অঞ্চলের পানীয় জলের উৎস নদী। নলকূপ বা কুয়ো খুঁড়েও যে জলের layer পাওয়া যায়—তা নদী তীরবর্তী অঞ্চল যে level-এ রয়েছে তার থেকে দুরবর্তী অঞ্চলে layer এর গভীরতা অনেক বেশী। এজন্য গাছপালা নদী-তীরবর্তী স্থানে নীচের দিকে মূল চালিয়ে নিকটস্থ layer থেকে জল সংগ্রহ করে। এর ফলে বনাঞ্চল বা বনভূমি নদী-অধ্যুষিত এলাকাতেই হয়—নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে বনভূমি বা বৃক্ষাদি ভালো হয় না। এছাড়া যে কোন মিষ্টি ফলের গাছ নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই ভালো জন্মে। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে তো ফল খুবই ভালো হয় এবং quality-ও ভালো হয়। কারণ এখানকার মাটিতে বা বালিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। মাটিতে ক্যালসিয়াম বেশী থাকাটা ফলগাছের পক্ষে খুবই ভালো। যে কোন টক-জাতীয় ফলগাছের গোড়ায় চুন দিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই গাছের ফলে মিষ্টতা আসে । ক্যালসিয়াম বা চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে জলাশয়ে মাছ চাষ করলে মাছের রোগ কম হয়—মাছের মিষ্টতা বা taste ভালো হয়। যারা গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের লোক তারা যত রকম মাছের variety-র নাম জানে এখানকার লোকেরা তা জানে না। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আর তাদের রন্ধন পদ্ধতিও ভিন্ন, এগুলি কিন্তু নদী বা গঙ্গা নেই এমন অঞ্চলের লোকেরা সত্যিই জানে না। আমার মা গঙ্গার মাছ রান্না করতেন আর তার যে taste তা আজও আমার মনে আছে। গঙ্গার মাছের যা taste, পুকুরের মাছে সেই taste থাকে না। সুতরাং মানবজীবনে বা সমাজজীবনে নদীর প্রভাব ব্যাপক ও বিশাল। আর যেহেতু গঙ্গা ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর দীর্ঘ বিস্তৃত নদী, তাই এই নদীর অববাহিকা ও প্লাবনভূমির বিস্তৃতিও অনেক বেশী। ফলে লক্ষ লক্ষ তথা কোটি কোটি মানুষ এই নদী থেকে উপকার পায়। পুরুষানুক্রমে নদীর আনুকূল্য পেতে পেতে, নদীর সাথে জীবনের অনেক হাসিকান্নাও জড়িয়ে পড়ে। এইভাবেই সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে নদী স্বাভাবিকভাবেই বারে বারে স্থান করে নিয়েছে। বলা হয় নারী-নদী-মৃত্তিকা এই তিনটির মধ্যে একটা সম্পর্ক বা সাদৃশ্য রয়েছে। নদীমাতৃক অঞ্চলে মৃত্তিকা উর্বর হয় এবং নারীরাও বহু প্রসবিনী হয়। মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চলে নদী নেই, তাই মাটিও অনুর্বর ও বন্ধ্যা, সেখানকার নারীরাও কম fertile বা বন্ধ্যা হয়। যাইহোক নদীবন্দনা এই পর্যন্তই থাক।