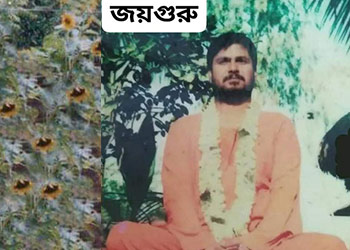জিজ্ঞাসা :– পশ্চিমবাংলায় আলু, ধান ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন খুবই ভালো হয়, নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও excss হয় – তাহলে পশ্চিমবঙ্গ এগুলি বিদেশে রপ্তানী করে তো রাজ্যের অর্থনৈতিক দুর্দশা কমাতে পারে ?
গুরুমহারাজ :– তুমি পশ্চিমবাংলার অর্থনীতির ব্যাপারে খুবই চিন্তা-ভাবনা করো মনে হোচ্ছে ! কিন্তু বাবা_ তোমার ভাবনা অনুযায়ী-ই কি দেশের সব কিছু চলবে ? প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে – সেই অনুযায়ী সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কাজ-কারবারগুলি হয় – বুঝেছো ? Export-import ব্যাপারটা সরাসরি রাজ্যের হাতে নাই, কেন্দ্রের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, সেগুলিকে follow করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাধারণত চাল, পাট আর চা বিদেশের বাজারে রপ্তানি হয় আর মালদহ-মুর্শিদাবাদের আম – তাও সামান্য ! আলু পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাশ্চাত্তের দেশগুলিতে রপ্তানি হয় না। কিছুটা সোজা পথে বাংলাদেশে যায় আর অনেকটাই চোরাপথে হয়তো যায় – ওটাকে অবশ্য export বলা যায় না !
তবে, পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান সমস্যা কি বলোতো – জনসংখ্যা ! দিল্লি শহরের জনসংখ্যাই প্রায় দুই কোটি (১৯৯৭) – ভাবো তো ! যেখানে ২০টি ইঁদুর ধরে, সেখানে যদি ৩০০টি ইঁদুর রাখো__তাহলে সমস্যা তো হবেই !
পূর্ববাংলায় যখন ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছিল – তখন যে দলে দলে শুধু হিন্দুরা ওদেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল তা নয়, ঐ ঘটনার আগে বা পরে বহু মুসলমানেরাও ভারতে চলে এসেছিল। কারণ পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি মুসলমানদেরকেও বিধর্মী-ই মনে করতো, ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে খান সেনারা ওখানকার মানুষের উপর বিশেষতঃ নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল। সেইসব অত্যাচার থেকে বাঁচতেই লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্ডার টপকে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। তাছাড়া তখন (সাতের দশক, আটের দশক) বাংলাদেশ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করা অনেক বেশি আরামদায়ক ছিল। এইসব প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর একটা গভীর এবং গোপন ব্যাপারও রয়েছে__সেটা অবশ্য এখানে আলোচনা করা উচিত হবে না, বলেই সেই আলোচনায় যাচ্ছি না।
যাই হোক, বাঙালি হিন্দুরা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত গঙ্গা বা অন্য কোনো নদীর ধারে কোনরকমে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছিল । আর বাঙালি মুসলমানেরা শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় – ভারতবর্ষের যে কোনো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এবং বিভিন্ন শহরে অর্থাৎ যেখানে রুজি-রুটির ব্যবস্থাও হবে, আবার বহু মানুষের ভিড়ে বিদেশী হিসাবে চিহ্নিতও হোতে হবে না – এইসব ভেবে ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ মিটে গেলে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর সম্পর্ক তৈরি হোলো এবং নানারকম চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শরণার্থী চুক্তিও স্বাক্ষরিত হোলো। তাছাড়া নিজ নিজ রাজ্যে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে – রাজ্য সরকার-ই নিজেদের উদ্যোগে refugee-দের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিল। ফলে এককালীন একটা ভীষণ জনসংখ্যার চাপ এসে পড়ল পশ্চিমবঙ্গে । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও কিছু এই ধরনের মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল।
এরপর হোলো কি__ এদেশে এসে কেউ তো জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা দেখলো না – ফলে কয়েক দশকের মধ্যেই ৬০/৭০(সাতের দশক) কোটি সংখ্যাটা ১১০/১১৫ কোটি (১৯৯৭)-তে দাঁড়িয়েছে !
ভারতবর্ষের বেশিরভাগ অংশই নদীমাতৃক এবং উর্বর এলাকা, তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সেচপ্রকল্প আর উন্নত প্রযুক্তিতে কৃষিকার্য্য হোচ্ছে বলেই এতোসংখ্যক মানুষ এই দেশে খেতে পাচ্ছে ! ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই “green revolution”- প্রজেক্ট ভারতবর্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছে ! এর ফলেই এতো অধিক জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ কৃষিতে স্বনির্ভর আর শুধু স্বনির্ভর-ই নয় – বিদেশে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে পারছে !
তবে ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুবই সমস্যার সৃষ্টি করছে ! যেহেতু ‘জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ’-এই ব্যাপারটা ঐ সমাজে প্রায় একেবারেই নেই – তাই এদের community-তে জনবিস্ফোরণ ঘটছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত ছিল, তাই এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উর্দুভাষী ঐসব সম্প্রদায়ের মানুষদের শ্রমিক হিসাবে ইউরোপের দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাজ মিটে গেলে জার্মানিরা ওই শ্রমিকদের সে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নরওয়ে বা আরও কিছু দেশ এই ধরনের নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে নি। নরওয়েতে কুড়ি হাজার উর্দুভাষী মানুষ রয়ে গেছিলো।
তারপর মজাটা কি হোলো জানো__এখন (১৯৯৭) অর্থাৎ বর্তমানে__ নরওয়ের জনসংখ্যা হয়েছে ৬৫ লক্ষ, যাদের মধ্যে ১৭ লক্ষ ওই সম্প্রদায়ের মানুষেরা ! ফলে সেদেশে এদের দাবি দাওয়া বাড়ছে, আর এতে নরওয়ের জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, অশান্তি-ঝামেলা বাড়ছে ! ওরা কি ভাবছে জানো__আবার নতুন একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি উঠবে নাকি !!
গুরুমহারাজ :– তুমি পশ্চিমবাংলার অর্থনীতির ব্যাপারে খুবই চিন্তা-ভাবনা করো মনে হোচ্ছে ! কিন্তু বাবা_ তোমার ভাবনা অনুযায়ী-ই কি দেশের সব কিছু চলবে ? প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে – সেই অনুযায়ী সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কাজ-কারবারগুলি হয় – বুঝেছো ? Export-import ব্যাপারটা সরাসরি রাজ্যের হাতে নাই, কেন্দ্রের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, সেগুলিকে follow করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাধারণত চাল, পাট আর চা বিদেশের বাজারে রপ্তানি হয় আর মালদহ-মুর্শিদাবাদের আম – তাও সামান্য ! আলু পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাশ্চাত্তের দেশগুলিতে রপ্তানি হয় না। কিছুটা সোজা পথে বাংলাদেশে যায় আর অনেকটাই চোরাপথে হয়তো যায় – ওটাকে অবশ্য export বলা যায় না !
তবে, পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান সমস্যা কি বলোতো – জনসংখ্যা ! দিল্লি শহরের জনসংখ্যাই প্রায় দুই কোটি (১৯৯৭) – ভাবো তো ! যেখানে ২০টি ইঁদুর ধরে, সেখানে যদি ৩০০টি ইঁদুর রাখো__তাহলে সমস্যা তো হবেই !
পূর্ববাংলায় যখন ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছিল – তখন যে দলে দলে শুধু হিন্দুরা ওদেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল তা নয়, ঐ ঘটনার আগে বা পরে বহু মুসলমানেরাও ভারতে চলে এসেছিল। কারণ পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি মুসলমানদেরকেও বিধর্মী-ই মনে করতো, ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে খান সেনারা ওখানকার মানুষের উপর বিশেষতঃ নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল। সেইসব অত্যাচার থেকে বাঁচতেই লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্ডার টপকে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। তাছাড়া তখন (সাতের দশক, আটের দশক) বাংলাদেশ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করা অনেক বেশি আরামদায়ক ছিল। এইসব প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর একটা গভীর এবং গোপন ব্যাপারও রয়েছে__সেটা অবশ্য এখানে আলোচনা করা উচিত হবে না, বলেই সেই আলোচনায় যাচ্ছি না।
যাই হোক, বাঙালি হিন্দুরা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত গঙ্গা বা অন্য কোনো নদীর ধারে কোনরকমে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছিল । আর বাঙালি মুসলমানেরা শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় – ভারতবর্ষের যে কোনো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এবং বিভিন্ন শহরে অর্থাৎ যেখানে রুজি-রুটির ব্যবস্থাও হবে, আবার বহু মানুষের ভিড়ে বিদেশী হিসাবে চিহ্নিতও হোতে হবে না – এইসব ভেবে ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ মিটে গেলে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর সম্পর্ক তৈরি হোলো এবং নানারকম চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শরণার্থী চুক্তিও স্বাক্ষরিত হোলো। তাছাড়া নিজ নিজ রাজ্যে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে – রাজ্য সরকার-ই নিজেদের উদ্যোগে refugee-দের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিল। ফলে এককালীন একটা ভীষণ জনসংখ্যার চাপ এসে পড়ল পশ্চিমবঙ্গে । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও কিছু এই ধরনের মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল।
এরপর হোলো কি__ এদেশে এসে কেউ তো জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা দেখলো না – ফলে কয়েক দশকের মধ্যেই ৬০/৭০(সাতের দশক) কোটি সংখ্যাটা ১১০/১১৫ কোটি (১৯৯৭)-তে দাঁড়িয়েছে !
ভারতবর্ষের বেশিরভাগ অংশই নদীমাতৃক এবং উর্বর এলাকা, তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সেচপ্রকল্প আর উন্নত প্রযুক্তিতে কৃষিকার্য্য হোচ্ছে বলেই এতোসংখ্যক মানুষ এই দেশে খেতে পাচ্ছে ! ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই “green revolution”- প্রজেক্ট ভারতবর্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছে ! এর ফলেই এতো অধিক জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ কৃষিতে স্বনির্ভর আর শুধু স্বনির্ভর-ই নয় – বিদেশে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে পারছে !
তবে ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুবই সমস্যার সৃষ্টি করছে ! যেহেতু ‘জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ’-এই ব্যাপারটা ঐ সমাজে প্রায় একেবারেই নেই – তাই এদের community-তে জনবিস্ফোরণ ঘটছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত ছিল, তাই এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উর্দুভাষী ঐসব সম্প্রদায়ের মানুষদের শ্রমিক হিসাবে ইউরোপের দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাজ মিটে গেলে জার্মানিরা ওই শ্রমিকদের সে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নরওয়ে বা আরও কিছু দেশ এই ধরনের নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে নি। নরওয়েতে কুড়ি হাজার উর্দুভাষী মানুষ রয়ে গেছিলো।
তারপর মজাটা কি হোলো জানো__এখন (১৯৯৭) অর্থাৎ বর্তমানে__ নরওয়ের জনসংখ্যা হয়েছে ৬৫ লক্ষ, যাদের মধ্যে ১৭ লক্ষ ওই সম্প্রদায়ের মানুষেরা ! ফলে সেদেশে এদের দাবি দাওয়া বাড়ছে, আর এতে নরওয়ের জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, অশান্তি-ঝামেলা বাড়ছে ! ওরা কি ভাবছে জানো__আবার নতুন একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি উঠবে নাকি !!