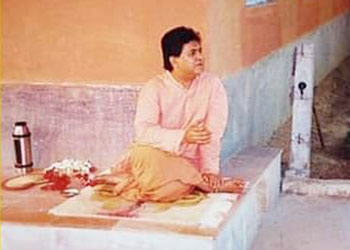গুরু মহারাজ স্বামী পরমানন্দের কাছে বনগ্রাম পরমানন্দ মিশনে সিটিং-এ বসে আমরা মানব সমাজের বিবর্তনের যে সমস্ত কথা শুনেছিলাম – সেইগুলি এখন এখানে পরপর বিভিন্ন এপিসোড অনুযায়ী আলোচনা করা হচ্ছে । গুরুমহারাজ বলেছিলেন সমস্ত জীব-জন্তুদের মধ্যে মানুষ-ই প্রথম আকাশকে ভালো করে দেখলো এবং তার বিশালতা নিয়ে, তার ব্যাপ্তি নিয়ে – আকাশকে কেন্দ্র করে নানান প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে_ তারা চিন্তা করতে শুরু করলো । এই চিন্তার গভীরতা যত বাড়তে লাগল – ততই জগতের অজানা রহস্যসমূহ তাদের কাছে উন্মোচিত হতে থাকলো । যে কোনো আবিষ্কার, যেকোন সৃষ্টি অর্থাৎ এক কথায় যে কোনো নতুন কিছু করতে গেলে_ আগে মানুষকে স্থির হতেই হয় । ওই যে কৃষিজীবী গোষ্ঠী এক একটা স্থানে স্থিতু হয়েছিল – এর ফলেই তারা একের পর এক আবিষ্কার করে নিজেদেরকে উন্নত করে তুলতে পেরেছিল ।
অপরপক্ষে যাযাবর গোষ্ঠী বা পশুপালক গোষ্ঠী কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে Setteled হোল না – ফলে তারা অপেক্ষাকৃত অসভ্য-ই থেকে গেল । তাদের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি কোমল মানবিক গুণসম্পন্ন জাগ্রত-ই হলো না,ফলে তাদের জীবনযাত্রায় দেখা যেতো হিংসা, মারামারি, রক্তপাত, জিঘাংসা ইত্যাদি ।
এই পশুপালক গোষ্ঠী বা যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষ বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের ঢালে বা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর সুযোগ পেলেই কৃষিজীবী গোষ্ঠীর কোন বসতি থেকে খাদ্য, গৃহপালিত পশু ও নারীদেরকে লুটপাট করে নিয়ে চলে যেতো । ধীরে ধীরে তারা কৃষিজীবী গোষ্ঠীর লোকেদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকা শুরু করল – যাতে কৃষিজীবী গোষ্ঠীর সৈন্যরা বা ক্ষত্রিয়শ্রেণী এদের নাগাল না পায় । হয়তো এই কারণেই এরা মরুভূমি বা দুর্গম অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং সুযোগ পেলেই অতর্কিতে কোন জনপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটপাট করে আবার ফিরে যেতো ওইসব দুর্গম স্থানে ৷ রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে দীর্ঘদিন থাকার জন্যই তাদের স্বভাবও রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল ।
গুরু মহারাজের কাছে আমরা শুনেছিলাম যে, পশুপালক গোষ্ঠীদের অনেকেই ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে কৃষিজীবীদের জীবন-রীতি মেনে নিয়েছিল । এদের মধ্যে যারা পরে সভ্য হয়েছিল, তাদের জীবন-যাপনের ধারা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই – এই কথার সত্যতা বোঝা যায় । উদাহরণ দিয়ে উনি বলেছিলেন – ” যেমন ধর – কোন পশুকে খাদ্যের জন্য বলিদান করার সময় পুরোনো (সভ্য) গোষ্ঠী এক কোপে কেটে ফেলতো _ যাতে ঐ পশুটার কষ্ট কম হয়, কিন্তু অন্য দল( সদ্য সভ্য হওয়া গোষ্ঠী) পশু বলি দেবার সময় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতো তাদের কষ্ট পাওয়া দেখে ঐসব মানুষেরা একপ্রকার সুখ অনুভব কোরতো_, আবার দেখবে অনেক গোষ্ঠী রয়েছে যারা পশুদেরকে মারার সময় তাড়া কোরে, আঘাত কোরে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত কোরে_ তারপর হত্যা করে (অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা আজও বিদ্যমান)। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দলের মানুষেরা অনেক পরে সভ্য সমাজে এসেছে – ফলে কালচার-এ এখনো বন্যতা রয়ে গেছে, স্বভাবে আদিমতা রয়ে গেছে ।
গুরুমহারাজ আরও বলেছিলেন – সমাজের বা পরিবারের কোন মানুষ মারা গেলে কৃষিজীবী গোষ্ঠীর মানুষেরা কষ্ট পেতো, কারণ দীর্ঘদিনের সমাজবদ্ধতা তাদেরকে পরস্পরের সাথে পরস্পরকে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা ছিল| তাই কোন এক সদস্য মারা গেলে – বাকি সকলেই শোক পালন করতো । কোনরকমে একবেলা হবিষ্যান্ন খেয়ে বা একেবারেই না খেয়ে বেশ কয়েক দিন কাটিয়ে দিতো ৷
অপরপক্ষে বেদুইন-যাযাবর-পশুপালক গোষ্ঠীর গতিশীল জীবন, সেখানে কারো জন্য থেমে যাওয়া, কারো জন্য শোকে আকুল হওয়া – এসবের কোন স্থান ছিল না । কারণ জীবনের অধিকাংশ সময়টাই কাটতো ঘোড়ার পিঠে বা উটের পিঠে ৷ রাত্রিতে কোন স্থানে তাঁবু খাটিয়ে শুধু একটু বিশ্রাম ।
গুরু মহারাজের কাছে শুনেছিলাম – চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং-এর মতো নৃশংস মরুদস্যুরা প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে তরবারির এক কোপে হত্যা করতো এবং সেই রক্তমাখা তরবারি থেকে রক্ত নিয়ে কপালে তিলক কাটতো, তারপর লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসতো এবং আবার শুরু হতো শুধু দৌড়-দৌড় আর দৌড় । সুযোগ পেলে আবার লুটপাট-হত্যা-ধ্বংসলীলা ! এই ধরনের মরুদস্যুরা মাত্র কয়েকশো বছর আগে সভ্য জগতের মূলস্রোতে এসে মিশেছিল ! সুতরাং তাদের মধ্যে অবশ্য কখনই_ ‘দীর্ঘকাল আগে থাকতে যারা সভ্য’ – তাদের মতো আচরণ আশা করতেও পারা যায় না । তাদের মধ্যে নৃশংসতা, হিংসা, গোঁড়ামি, স্বার্থপরতা – এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক !
গুরু মহারাজ বলেছিলেন – মহাপুরুষ, মহাত্মা, অবতার-পুরুষেরা ঐ কৃষিজীবি সভ্য মানুষের মধ্যে শরীর ধারন করে, দীর্ঘকাল থেকে তাদের চেতনাকে উন্নত করার কাজটি করে যাচ্ছিলেন । কিন্তু সবই তো ঈশ্বরের – সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি । ভালোটিও তাঁর মন্দটিও তাঁর । ভালো রয়েছে বলেই মন্দ রয়েছে – যেমন আলো আছে বলে রয়েছে অন্ধকার, দিন রয়েছে বলেই রয়েছে রাত্রি ! বিবর্তনের ফলে মন্দ ই তো একদিন ভালো হয়ে উঠবে! তাছাড়া_এই পৃথিবীগ্রহের জীবচেতনার বিবর্তন ঘটিয়ে একেও পূর্ণত্বে পৌঁছে দিতে হবে । তাই মহাজাগতিক নিয়মে ওই সমস্ত অনুন্নত গোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছে ! তাঁরা ওই নৃশংস, অসভ্য জনগোষ্ঠীর মানুষদেরকে একত্রিত করার, সমাজবদ্ধ করার, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে এক স্থানে স্থিতু করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । ঈশ্বর সম্বন্ধে, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন – যাতে করে এই সমস্ত মানুষেরা হিংসা-নৃশংসতা-জিঘাংসা ভুলে শান্ত হয়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়াশীল-ক্ষমাশীল, সহ্যশীল হয়ে উঠতে পারে ৷
ভারতবর্ষে নদীবিধৌত সমতল ভূমির মানুষ বহুদিন থেকেই মুনি-ঋষি-মহাপুরুষগণের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল ৷ এখানে মরুভূমি থেকে আগত বা পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে আগত কোন ধর্মাদর্শের প্রয়োজন ছিল না । মরুদস্যুরা জোর করে তাদের সেখানকার ধর্মমত বা ধর্মাচরনকে এখানে নিয়ে আসাতেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। যেহেতু ঐ মরুদস্যুরা এখানে এসে রাজা হয়ে বসেছিল তাই দলে দলে সাধারণ মানুষ রাজার ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল( অবশ্য, তৎকালীন সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের উপর উচ্চশ্রেণীর মানুষের অত্যাচার ও এর অন্যতম একটা কারন ছিল)। এর ফলে কি হোল_ঈশপের গল্পে লেজকাটা শিয়ালের মতো ,যারা নতুন ধর্মমত গ্রহণ করল_তারাই উদ্যোগী হয়ে বাকিদেরকেও স্বমতে আনার চেষ্টা করতে লাগলো।(ক্রমশঃ)
অপরপক্ষে যাযাবর গোষ্ঠী বা পশুপালক গোষ্ঠী কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে Setteled হোল না – ফলে তারা অপেক্ষাকৃত অসভ্য-ই থেকে গেল । তাদের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি কোমল মানবিক গুণসম্পন্ন জাগ্রত-ই হলো না,ফলে তাদের জীবনযাত্রায় দেখা যেতো হিংসা, মারামারি, রক্তপাত, জিঘাংসা ইত্যাদি ।
এই পশুপালক গোষ্ঠী বা যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষ বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের ঢালে বা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর সুযোগ পেলেই কৃষিজীবী গোষ্ঠীর কোন বসতি থেকে খাদ্য, গৃহপালিত পশু ও নারীদেরকে লুটপাট করে নিয়ে চলে যেতো । ধীরে ধীরে তারা কৃষিজীবী গোষ্ঠীর লোকেদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকা শুরু করল – যাতে কৃষিজীবী গোষ্ঠীর সৈন্যরা বা ক্ষত্রিয়শ্রেণী এদের নাগাল না পায় । হয়তো এই কারণেই এরা মরুভূমি বা দুর্গম অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং সুযোগ পেলেই অতর্কিতে কোন জনপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটপাট করে আবার ফিরে যেতো ওইসব দুর্গম স্থানে ৷ রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে দীর্ঘদিন থাকার জন্যই তাদের স্বভাবও রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল ।
গুরু মহারাজের কাছে আমরা শুনেছিলাম যে, পশুপালক গোষ্ঠীদের অনেকেই ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে কৃষিজীবীদের জীবন-রীতি মেনে নিয়েছিল । এদের মধ্যে যারা পরে সভ্য হয়েছিল, তাদের জীবন-যাপনের ধারা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই – এই কথার সত্যতা বোঝা যায় । উদাহরণ দিয়ে উনি বলেছিলেন – ” যেমন ধর – কোন পশুকে খাদ্যের জন্য বলিদান করার সময় পুরোনো (সভ্য) গোষ্ঠী এক কোপে কেটে ফেলতো _ যাতে ঐ পশুটার কষ্ট কম হয়, কিন্তু অন্য দল( সদ্য সভ্য হওয়া গোষ্ঠী) পশু বলি দেবার সময় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতো তাদের কষ্ট পাওয়া দেখে ঐসব মানুষেরা একপ্রকার সুখ অনুভব কোরতো_, আবার দেখবে অনেক গোষ্ঠী রয়েছে যারা পশুদেরকে মারার সময় তাড়া কোরে, আঘাত কোরে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত কোরে_ তারপর হত্যা করে (অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা আজও বিদ্যমান)। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দলের মানুষেরা অনেক পরে সভ্য সমাজে এসেছে – ফলে কালচার-এ এখনো বন্যতা রয়ে গেছে, স্বভাবে আদিমতা রয়ে গেছে ।
গুরুমহারাজ আরও বলেছিলেন – সমাজের বা পরিবারের কোন মানুষ মারা গেলে কৃষিজীবী গোষ্ঠীর মানুষেরা কষ্ট পেতো, কারণ দীর্ঘদিনের সমাজবদ্ধতা তাদেরকে পরস্পরের সাথে পরস্পরকে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা ছিল| তাই কোন এক সদস্য মারা গেলে – বাকি সকলেই শোক পালন করতো । কোনরকমে একবেলা হবিষ্যান্ন খেয়ে বা একেবারেই না খেয়ে বেশ কয়েক দিন কাটিয়ে দিতো ৷
অপরপক্ষে বেদুইন-যাযাবর-পশুপালক গোষ্ঠীর গতিশীল জীবন, সেখানে কারো জন্য থেমে যাওয়া, কারো জন্য শোকে আকুল হওয়া – এসবের কোন স্থান ছিল না । কারণ জীবনের অধিকাংশ সময়টাই কাটতো ঘোড়ার পিঠে বা উটের পিঠে ৷ রাত্রিতে কোন স্থানে তাঁবু খাটিয়ে শুধু একটু বিশ্রাম ।
গুরু মহারাজের কাছে শুনেছিলাম – চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং-এর মতো নৃশংস মরুদস্যুরা প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে তরবারির এক কোপে হত্যা করতো এবং সেই রক্তমাখা তরবারি থেকে রক্ত নিয়ে কপালে তিলক কাটতো, তারপর লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসতো এবং আবার শুরু হতো শুধু দৌড়-দৌড় আর দৌড় । সুযোগ পেলে আবার লুটপাট-হত্যা-ধ্বংসলীলা ! এই ধরনের মরুদস্যুরা মাত্র কয়েকশো বছর আগে সভ্য জগতের মূলস্রোতে এসে মিশেছিল ! সুতরাং তাদের মধ্যে অবশ্য কখনই_ ‘দীর্ঘকাল আগে থাকতে যারা সভ্য’ – তাদের মতো আচরণ আশা করতেও পারা যায় না । তাদের মধ্যে নৃশংসতা, হিংসা, গোঁড়ামি, স্বার্থপরতা – এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক !
গুরু মহারাজ বলেছিলেন – মহাপুরুষ, মহাত্মা, অবতার-পুরুষেরা ঐ কৃষিজীবি সভ্য মানুষের মধ্যে শরীর ধারন করে, দীর্ঘকাল থেকে তাদের চেতনাকে উন্নত করার কাজটি করে যাচ্ছিলেন । কিন্তু সবই তো ঈশ্বরের – সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি । ভালোটিও তাঁর মন্দটিও তাঁর । ভালো রয়েছে বলেই মন্দ রয়েছে – যেমন আলো আছে বলে রয়েছে অন্ধকার, দিন রয়েছে বলেই রয়েছে রাত্রি ! বিবর্তনের ফলে মন্দ ই তো একদিন ভালো হয়ে উঠবে! তাছাড়া_এই পৃথিবীগ্রহের জীবচেতনার বিবর্তন ঘটিয়ে একেও পূর্ণত্বে পৌঁছে দিতে হবে । তাই মহাজাগতিক নিয়মে ওই সমস্ত অনুন্নত গোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছে ! তাঁরা ওই নৃশংস, অসভ্য জনগোষ্ঠীর মানুষদেরকে একত্রিত করার, সমাজবদ্ধ করার, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে এক স্থানে স্থিতু করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । ঈশ্বর সম্বন্ধে, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন – যাতে করে এই সমস্ত মানুষেরা হিংসা-নৃশংসতা-জিঘাংসা ভুলে শান্ত হয়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়াশীল-ক্ষমাশীল, সহ্যশীল হয়ে উঠতে পারে ৷
ভারতবর্ষে নদীবিধৌত সমতল ভূমির মানুষ বহুদিন থেকেই মুনি-ঋষি-মহাপুরুষগণের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল ৷ এখানে মরুভূমি থেকে আগত বা পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে আগত কোন ধর্মাদর্শের প্রয়োজন ছিল না । মরুদস্যুরা জোর করে তাদের সেখানকার ধর্মমত বা ধর্মাচরনকে এখানে নিয়ে আসাতেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। যেহেতু ঐ মরুদস্যুরা এখানে এসে রাজা হয়ে বসেছিল তাই দলে দলে সাধারণ মানুষ রাজার ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল( অবশ্য, তৎকালীন সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের উপর উচ্চশ্রেণীর মানুষের অত্যাচার ও এর অন্যতম একটা কারন ছিল)। এর ফলে কি হোল_ঈশপের গল্পে লেজকাটা শিয়ালের মতো ,যারা নতুন ধর্মমত গ্রহণ করল_তারাই উদ্যোগী হয়ে বাকিদেরকেও স্বমতে আনার চেষ্টা করতে লাগলো।(ক্রমশঃ)