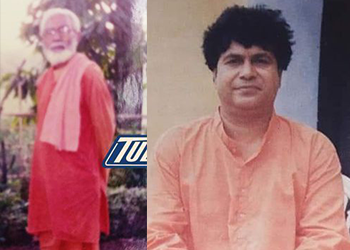শ্রী শ্রী গুরুমহারাজ স্বামী পরমানন্দের কথা (বলা এবং লেখা) এখানে আলোচনা করা হচ্ছিলো। গুরুমহারাজ বলেছেন – ” প্রিয় আত্মন্ ! ব্রহ্মানন্দ বা সহজ আনন্দ অনির্বচনীয়, ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র অনুভূতি (ব্রহ্মানুভূতি) সত্য।” এই যে গুরুমহারাজ বলেছেন যে, ‘ব্রহ্মানন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না’– এই ‘ভাষা’ সম্বন্ধে এরপরেই উনি আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন – ” মানবের মননশক্তিই ক্রম-অভিব্যক্তির ফলে ভাষায় রূপ গ্রহণ করেছে। ভাব-প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ আকার ও ইঙ্গিত এবং অর্থবাহী নানাধরনের ধ্বনি বা অস্ফুট আওয়াজে। প্রকৃতির তাড়নায় তা ক্রমশঃ বিচিত্র ধ্বনিরূপে প্রকাশ পেতে থাকে মানবের মুখে। বাকযন্ত্রের অনুশীলন অবিরত চলতে লাগল, কালক্রমে অন্তরের সত্য ও মননজাত ভাব স্পষ্টরূপে সুব্যক্ত ভাষার দ্বারা প্রকাশ হতে লাগল। মানবের মুখনিঃসৃত ধ্বনিই ‘ভাষা’ নামে পরিণতি লাভ করলো।”
সুধী পাঠকবৃন্দ ! ভাষা (মানবের মুখের ভাষা)-র ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে গুরুমহারাজের এই সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সত্যিই অসাধারণ! আমরা সাধারণভাবে জানি যে, ‘মনের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম-ই ভাষা।’ গুরুমহারাজ সেই কথাকেই আরো সুগভীর চিন্তা ও মননশক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে এই সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাপারে উনি আরো বলেছেন, ” সেই ‘ভাষা’ বিভিন্ন চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত হয়ে অক্ষর বা লিপিতে রূপ লাভ করে। এই ভাষা ও লিপিকে কেন্দ্র করে ভাষাবিজ্ঞান প্রকাশিত হোলো।” তাহলে বোঝা গেল যে, প্রথমে মনের ভাব প্রকাশিত করার প্রথম উপায় ছিল ‘আকার-ইঙ্গিতে’র মাধ্যমে। এর পরের ধাপ ছিল নানা ধরনের ধ্বনি বা অস্ফুট আওয়াজ। এই ধ্বনির প্রকাশের মাধ্যমে মানবের মুখগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত বাকযন্ত্রের ক্রমাগত অনুশীলন চলতে থাকলো। এইভাবে মানুষ যতই সভ্য হোতে থাকলো_ ততই তার মুখের ভাষার স্পষ্টতা ও সুর-বৈচিত্র্যের বহর দেখা গেল। এইভাবে মানব তার মনের ভাব উপলব্ধ সত্য সুস্পষ্টভাবে ‘ভাষা’ রূপে প্রকাশিত হোলো।
এরপরের stage এলো অক্ষর বা ‘লিপি’। লিপির মাধ্যমে মুখের ভাষা সাহিত্যে প্রকাশিত হোলো_এবং একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হোলো। এইটাই ভাষাবিজ্ঞান ! এবার গুরুমহারাজ এই প্রসঙ্গে বললেন যে, ” এখন (বর্তমানে) সেই অপরিশুদ্ধ ভাষাই উন্নত ভাষায় পরিণত হয়েছে। ভাষার এই ক্রমবিকাশ আবহমানকাল ধরে চলছে। যতদিন মানবের জীবনস্রোত বইতে থাকবে, ততদিন ভাষার স্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হোতে থাকবে।”
এইখানে একটা কথা অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য, আর তা হোলো – ‘ভাষার ক্রমবিকাশ’ বা ‘ভাষার বিবর্তন’৷ এর মানে হোচ্ছে মানুষের ভাষার প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং যতদিন যাবে ততই তা আরো পরিবর্তিত হবে । এর সাথে সাথে আরো একটা কথা লক্ষ্য রাখতে হবে, আর তা হোলো__ নতুন নতুন ভাষার জন্ম যেমন হোতে পারে, আবার হয়তো পুরোনো কোনো ভাষার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে ।
এরপরে গুরুমহারাজ ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা এবং সেই ভাষার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন । উনি বলেছেন_ “প্রাক বৈদিক আর্য ভাষা ভারতবর্ষের সাধারণের প্রচলিত ভাষা, পাণিনির দ্বারা সংস্কার লাভ করে এই ভাষার নাম হল সংস্কৃত । এইভাবে প্রাচীন আর্য ভাষা সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে ‘সংস্কৃত’ নাম ধারণ করল । ভারতীয় পণ্ডিতগণ আবার ব্যাকরণ-এর কঠিন সংস্কৃত ভাষাকে বেঁধে ফেলল। কিন্তু ভাষার প্রবাহ রোধ হোলোনা, অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হোতে লাগল এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও উপভাষা সৃষ্টি হোলো ।”
সুধী পাঠকবৃন্দ ! এই হোলো ভারতবর্ষের ভাষা বিবর্তনের ইতিহাস বা এখনকার ভাষার ক্রমবিকাশ! এইবার ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন এবং বহুল প্রশংসিত, বহুল প্রচলিত ভাষা হিসাবে স্বীকৃত সংস্কৃতের (পাণীনির সংস্কারের পর) এমন করুণ হোলো কেন ? এই প্রসঙ্গে গুরু মহারাজের কথা অনুযায়ী বলতে হয়__ ‘ওই যে পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের বন্ধনে সংস্কৃত ভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন, সেই বেষ্টনী ভেঙে আর সামনের দিকে এই ভাষা প্রবাহিত হোতে পারলোনা, আদি সংস্কৃত ভাষা রূপেই রয়ে গেল ! কিন্তু যেহেতু ভাষা প্রবহমান, গতিশীল, পরিবর্তনশীল__ তাই এই সংস্কৃত ভাষাই কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে কথ্য ভাষার নতুন স্রোত জনজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হোতে লাগল । সুতরাং মানবের ভাষা থেমে থাকে না_ তার গতি আছে, ছন্দ আছে এবং রূপান্তর আছে ।’__এগুলো সবই গুরু মহারাজের কথা ।।
এতক্ষণ ধরে গুরুমহারাজ ভাষার বিবর্তন নিয়ে এই জন্যেই এতোটা আলোচনা করলেন, যাতে আমরা এটা বুঝতে পারি যে_ কথ্য ভাষা (সাধারণ মানুষের কথা বলার ভাষা) বা লেখ্য ভাষা (সাহিত্যের ভাষা) এগুলি মানুষের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম- উপলব্ধ সত্য প্রকাশের মাধ্যম ! কিন্তু সত্য-উপলব্ধি, ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মবোধ__এইগুলি অন্তর্জগতের ব্যাপার, বাহ্য প্রকাশের ব্যাপার নয় ! এই জন্যেই গুরু মহারাজ বললেন __”তাই ভাষা ব্রহ্মানন্দ বা সহজ আনন্দকে ব্যক্ত করতে পারেনা, শুধুমাত্র আভাস দেয়- ইঙ্গিত দেয়। আত্মাই আত্মাকে বোধ করে – ইহাই বোধে বোধ এবং জীবনবোধ।”
(ক্রমশঃ)
সুধী পাঠকবৃন্দ ! ভাষা (মানবের মুখের ভাষা)-র ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে গুরুমহারাজের এই সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সত্যিই অসাধারণ! আমরা সাধারণভাবে জানি যে, ‘মনের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম-ই ভাষা।’ গুরুমহারাজ সেই কথাকেই আরো সুগভীর চিন্তা ও মননশক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে এই সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাপারে উনি আরো বলেছেন, ” সেই ‘ভাষা’ বিভিন্ন চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত হয়ে অক্ষর বা লিপিতে রূপ লাভ করে। এই ভাষা ও লিপিকে কেন্দ্র করে ভাষাবিজ্ঞান প্রকাশিত হোলো।” তাহলে বোঝা গেল যে, প্রথমে মনের ভাব প্রকাশিত করার প্রথম উপায় ছিল ‘আকার-ইঙ্গিতে’র মাধ্যমে। এর পরের ধাপ ছিল নানা ধরনের ধ্বনি বা অস্ফুট আওয়াজ। এই ধ্বনির প্রকাশের মাধ্যমে মানবের মুখগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত বাকযন্ত্রের ক্রমাগত অনুশীলন চলতে থাকলো। এইভাবে মানুষ যতই সভ্য হোতে থাকলো_ ততই তার মুখের ভাষার স্পষ্টতা ও সুর-বৈচিত্র্যের বহর দেখা গেল। এইভাবে মানব তার মনের ভাব উপলব্ধ সত্য সুস্পষ্টভাবে ‘ভাষা’ রূপে প্রকাশিত হোলো।
এরপরের stage এলো অক্ষর বা ‘লিপি’। লিপির মাধ্যমে মুখের ভাষা সাহিত্যে প্রকাশিত হোলো_এবং একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হোলো। এইটাই ভাষাবিজ্ঞান ! এবার গুরুমহারাজ এই প্রসঙ্গে বললেন যে, ” এখন (বর্তমানে) সেই অপরিশুদ্ধ ভাষাই উন্নত ভাষায় পরিণত হয়েছে। ভাষার এই ক্রমবিকাশ আবহমানকাল ধরে চলছে। যতদিন মানবের জীবনস্রোত বইতে থাকবে, ততদিন ভাষার স্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হোতে থাকবে।”
এইখানে একটা কথা অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য, আর তা হোলো – ‘ভাষার ক্রমবিকাশ’ বা ‘ভাষার বিবর্তন’৷ এর মানে হোচ্ছে মানুষের ভাষার প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং যতদিন যাবে ততই তা আরো পরিবর্তিত হবে । এর সাথে সাথে আরো একটা কথা লক্ষ্য রাখতে হবে, আর তা হোলো__ নতুন নতুন ভাষার জন্ম যেমন হোতে পারে, আবার হয়তো পুরোনো কোনো ভাষার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে ।
এরপরে গুরুমহারাজ ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা এবং সেই ভাষার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন । উনি বলেছেন_ “প্রাক বৈদিক আর্য ভাষা ভারতবর্ষের সাধারণের প্রচলিত ভাষা, পাণিনির দ্বারা সংস্কার লাভ করে এই ভাষার নাম হল সংস্কৃত । এইভাবে প্রাচীন আর্য ভাষা সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে ‘সংস্কৃত’ নাম ধারণ করল । ভারতীয় পণ্ডিতগণ আবার ব্যাকরণ-এর কঠিন সংস্কৃত ভাষাকে বেঁধে ফেলল। কিন্তু ভাষার প্রবাহ রোধ হোলোনা, অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হোতে লাগল এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও উপভাষা সৃষ্টি হোলো ।”
সুধী পাঠকবৃন্দ ! এই হোলো ভারতবর্ষের ভাষা বিবর্তনের ইতিহাস বা এখনকার ভাষার ক্রমবিকাশ! এইবার ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন এবং বহুল প্রশংসিত, বহুল প্রচলিত ভাষা হিসাবে স্বীকৃত সংস্কৃতের (পাণীনির সংস্কারের পর) এমন করুণ হোলো কেন ? এই প্রসঙ্গে গুরু মহারাজের কথা অনুযায়ী বলতে হয়__ ‘ওই যে পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের বন্ধনে সংস্কৃত ভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন, সেই বেষ্টনী ভেঙে আর সামনের দিকে এই ভাষা প্রবাহিত হোতে পারলোনা, আদি সংস্কৃত ভাষা রূপেই রয়ে গেল ! কিন্তু যেহেতু ভাষা প্রবহমান, গতিশীল, পরিবর্তনশীল__ তাই এই সংস্কৃত ভাষাই কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে কথ্য ভাষার নতুন স্রোত জনজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হোতে লাগল । সুতরাং মানবের ভাষা থেমে থাকে না_ তার গতি আছে, ছন্দ আছে এবং রূপান্তর আছে ।’__এগুলো সবই গুরু মহারাজের কথা ।।
এতক্ষণ ধরে গুরুমহারাজ ভাষার বিবর্তন নিয়ে এই জন্যেই এতোটা আলোচনা করলেন, যাতে আমরা এটা বুঝতে পারি যে_ কথ্য ভাষা (সাধারণ মানুষের কথা বলার ভাষা) বা লেখ্য ভাষা (সাহিত্যের ভাষা) এগুলি মানুষের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম- উপলব্ধ সত্য প্রকাশের মাধ্যম ! কিন্তু সত্য-উপলব্ধি, ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মবোধ__এইগুলি অন্তর্জগতের ব্যাপার, বাহ্য প্রকাশের ব্যাপার নয় ! এই জন্যেই গুরু মহারাজ বললেন __”তাই ভাষা ব্রহ্মানন্দ বা সহজ আনন্দকে ব্যক্ত করতে পারেনা, শুধুমাত্র আভাস দেয়- ইঙ্গিত দেয়। আত্মাই আত্মাকে বোধ করে – ইহাই বোধে বোধ এবং জীবনবোধ।”
(ক্রমশঃ)