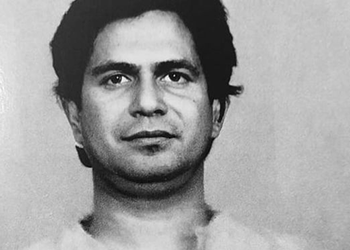আমরা আগের আলোচনায় প্রথম stanza-র একেবারে শেষাংশের কথা নিয়ে কথা বলেছিলাম ৷ সেখানে গুরুজীর বিশ্বম্ভর-রূপের কথা বলতে গিয়ে, এই ব্যাপারে আমার নিজস্ব অনুভূতির কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল । কিন্তু ভগবান পরমানন্দ তো অনাদি-অনন্তের স্থূলরূপ ! তাই তাঁর মহিমার কথা, তাঁর গুণের কথা, তাঁর রূপের কথা বলা অর্থাৎ এককথায় ভাষার মাধ্যমে কিছু বলার দ্বারা বা স্তব-স্তুতির সাহায্যে তাঁর মহিমা প্রকাশ করাটাও খুবই ছেলেমানুষী !
তবুও মহাজনগণ কালে কালে শ্রীভগবানের স্তুতিগান রচনা করে গেছেন এবং তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসারীরা আজও সেই কাজ করে যাচ্ছেন। এঁরা এই কাজ করেন কারণ__যদি সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীভগবানের মহিমার কথা, গুণের কথা ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া যায় এবং সেইসব শুনে যদি কিয়দংশ মানুষের মধ্যেও ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মায় — সেটাই হোলো উদ্দেশ্য ! এইজন্যেই বলা হয় যে, ‘মহাজনগণও শ্রীভগবানের কাজেরই অংশীদার – তাঁরাও শ্রীভগবানের সহচর’ ৷
যাইহোক, যেটা বলার কথা, সেটা হোলো – আমরা ‘বিশ্বম্ভররূপম’ কথাটির যেটুকু অর্থ করেছি__ শ্রীভগবানের ‘বিশ্বম্ভর’ নামকরণের নিশ্চয়ই আরো আরো গুরুতর, গুঢ়তর অর্থ রয়েছে – এটাও আপনারা জেনে রাখবেন !
এবার আমরা ঐ বন্দনাগীতি-র দ্বিতীয় stanza-র কথায় চলে যাবো কিন্তু তার আগে বলা দরকার যে, প্রতিটি stanza-র শেষে । “ওঁ হর হর সদগুরো মহাদেব:” – এই কথাগুলি বলা রয়েছে ৷ এখানে একটা কথা মনে হোতেই পারে যে, গুরুকে শুধু ‘হর’ বা ‘মহাদেব’ বলা হোচ্ছে কেন ? গুরু প্রণামমন্ত্রে রয়েছে “গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর:” – সুতরাং গুরু হলেন সাক্ষাৎ ‘ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর’ এই ত্রিদেব তত্ত্বের মিলিত রূপ ৷ এ ছাড়াও ওই প্রণাম মন্ত্রেই অন্যত্র বলা রয়েছে “গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম”! সুতরাং গুরু হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ! তার মানে হচ্ছে – সদগুরু সগুনতত্ত্ব (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর), আবার নির্গুণতত্ত্ব(ব্রহ্ম)-ও বটে ! গুরুকে যে ব্যক্তি যেভাবে গ্রহণ করতে পারবেন – তিনি তাকে সেই ভাবেই তার বাঞ্ছিত ফল প্রদান করবেন ৷ শ্রীমদ্ভগবতগীতায় রয়েছে – “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাং তথৈব ভজাম্যহম্ ৷”
এখানে এই বন্দনাগীতির রচনাকার স্বামী তপেশ্বরানন্দ মহারাজ যেহেতু পূর্বে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তিনি ওই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের ‘বন্দনাগীতি’ অনুসরণে এই “পরমানন্দ বন্দনা” রচনা করেছিলেন, সুতরাং স্বামী প্রণবানন্দকে শিবাবতার বলা হয় বলেই ওনাকে “শিব” হিসাবে মেনে নিয়ে স্তুতি করা হয়েছে ৷ যেহেতু মূল রচনায় (প্রণবানন্দ বন্দনা) ‘হর_হর’ এবং ‘মহাদেব’ কথাটি রয়েছে, তাই তপেশ্বরানন্দজীও ঐ কথাটিই রেখে দিয়েছিলেন – আর কোনো পরিবর্তন করেন নি ৷ তবে এটাও ঠিক যে, ঐ বন্দনাগীতিতেই পরবর্তী stanza-য় ‘সচ্চিদানন্দ’ কথাটিও রয়েছে ৷ আর আমরা জানি ‘সচ্চিদানন্দ’ বা ‘সৎ-চিৎ-আনন্দ’ – ‘ব্রহ্ম’ শব্দেরই পরিপূরক ! আমরা এখন ওই stanza-র কথাতেই চলে যাই !
দ্বিতীয় stanza-র শুরুতে বলা হয়েছে – “সৌম্যং রম্যং দিব্যং সচ্চিদানন্দং, জয় সচ্চিদানন্দং !” ‘সৌমং’ ও ‘রম্যং’ শব্দ দুটির দ্বারাও সুন্দর-কেই বোঝানো হয় – কিন্তু স্বামী পরমানন্দের ‘সৌন্দর্য’ যেন অপার্থিব ! যে সৌন্দর্যের মধ্যে সরলতা রয়েছে – সহজতা রয়েছে – পবিত্রতা রয়েছে, তাছাড়া সেই সৌন্দর্য ‘দিব্য’ বা divine, তাই ওখানে ‘দিব্যং’ শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে ৷ এর পরের শব্দটিই হোলো – ‘সচ্চিদানন্দং’ – যে শব্দটি নিয়ে একটু আগেই আলোচনা করা হচ্ছিলো ৷ ‘সচ্চিদানন্দ’ শব্দটি ব্রহ্মবাচক – তাই বলা হয় ‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম’ !
গুরুমহারাজ স্থূলশরীর-বিশিষ্ট একজন মহামানব রূপে আমাদের সকলের কাছে প্রকাশিত থাকলেও স্বরূপতঃ তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ-ই ৷ হয়তো আপনারা বলবেন যে, তিনি তো মানবাকারে ছিলেন _আর শুধু একটা মানবই নয়, সকল জীবসহ এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকল কিছুই তো ব্রহ্মস্বরূপ ! আচার্য্য শংকর তো বলেছেনই – “জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ”! – হ্যাঁ, এগুলো একদমই সত্যি কথা ৷ কিন্তু এটাও ঠিক যে, জড়জগত-এর চেতনা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং জীবসমূহের চেতনা প্রকটিত অবস্থায় থাকলেও তাদের ব্রহ্মচেতনা বা পরমচৈতন্য অজ্ঞানতারূপ মেঘের আবরণে ঢাকা সূর্যের ন্যায় হয়, তা যেন কোথাও একটু আবছা বা gloomy অথবা একেবারেই dark বা অন্ধকার ৷
এইজন্যেই তো জীবসকলের জীবনে এতো হাহাকার ! পৃথিবীগ্রহের সর্বোন্নত জীব মানুষগণের মধ্যেই এই হাহাকার সবচাইতে প্রকট। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক – কারণ এই গ্রহের জীববিবর্তন-রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের সর্বোচ্চ শিখরে থাকায় জীবকুলের স্বভাবে যা কিছু রয়েছে_ সেই সবকিছুর প্রকাশ মানুষেই সর্বাপেক্ষা বেশি তো হবেই — তাই না ? তবু এইখানে একটি বিশেষ বিষয় রয়েছে – যা গুরুমহারাজ সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আর সেটা হোলো – ” মানবের জীবনে যেমন need of life (অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান), necessity of life (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুরক্ষা) রয়েছে – তেমনি রয়েছে purpose of life অর্থাৎ পূর্ণতা অর্জন বা আত্মসাক্ষাৎকার” ৷
সাধারণতঃ মানুষ হিসাবে আমরা (বেশিরভাগ মানুষেরা)need এবং necessity নিয়েই মেতে থাকি ৷ তার স্বরূপকে জানার, আত্মসাক্ষাৎকার করার, ঈশ্বরত্ব অর্জন (ঈশ্বরলাভ)-এর চেষ্টাই করি না ৷ এইজন্যেই মহাপুরুষগণ (‘plus world’ থেকে আগত নির্দিষ্ট মহাপুরুষগণ) পৃথিবীতে শরীর ধারণ করে – সাধারণ মানুষকে প্রেম দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে – যতোটা পারেন তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করান এবং কিভাবে পূর্ণত্বলাভ করতে হয় তার উপায় বাতলে যান ৷ শত-সহস্র মানুষ তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ধ্যান-জপ, যোগাদির দ্বারা আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট হ’ন, তাদেরকে দেখে আবার আরো অন্যেরা উদ্বুদ্ধ হ’ন – এইভাবেই পরম্পরাক্রমে এই স্রোত প্রবাহিত হোতে থাকে সন্মুখের পানে৷ চরৈবেতি -চরৈবেতি -চরৈবেতি ।৷