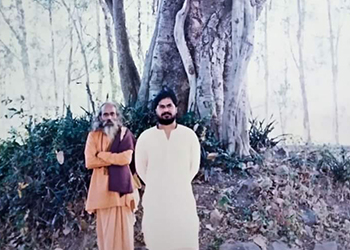প্রিয় আত্মন্—এবার ‘উপাসনা’ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। ‘উপাসনা’ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রথমে জানতে হবে ‘উপাসনা’ শব্দের অর্থ কি, আর কিভাবে উপাসনা জীবনে যোজনা করতে হবে।
‘উপাসনা’ শব্দটি সংস্কৃত, ‘উপ-সমীপে আসন’—অর্থাৎ উপ—আস্+অন্ (স্ত্রী আ)—এই তিন অংশ। ‘উপ’—উপসর্গে, আস—উপবেশনে, অন্ প্রত্যয় যোগে ‘উপাসনা’।
মানব মননশীল। মানবের মনে অনেক কামনা-বাসনা বিদ্যমান। মনের এই নিম্নমুখী বেগকে অশুদ্ধ মন বলা হয় এবং কামনা-বাসনা বিমুক্ত মনের ঊর্ধ্ব বেগকে বিশুদ্ধ মন বলা হয়। মনই হল বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। অনিত্য বিষয়-বাসনা বিজড়িত মনই বন্ধন-কারক। অনিত্য বিষয়-বাসনা বিমুক্ত মন বা নিত্যমুখী মনই মুক্তি প্রদায়ক। এই অনিত্য বিষয় আসক্ত মনকে বিষয় বিমুক্ত করবার নিমিত্তই উপাসনা বা আরাধনা মানবজীবনে একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত রকমের উপাসনার উদ্দেশ্যই হল মনকে বিশুদ্ধ বা নির্মল করা। সমস্ত রকমের কামনা-বাসনার মূল হল অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। মনের ভ্রান্তিনাশের নিমিত্তই উপাসনা মানবজীবনে অবধারিত। কায়-মন-বাক্যে অন্তঃকরণের সমূহ বৃত্তিকে ভগবৎমুখী করে তুলতে হবে। যেন তৈলধারার ন্যায় চিত্তবৃত্তিসমূহ উপাস্যে সতত প্রবাহিত হয়। এই উপাসনা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অনেক প্রকার হতে পারে, কিন্তু উপাস্য সর্বকালেই এক, বহু কখনই নয়। সর্বদেশে, সর্বকালে ঐ একই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর বহুরূপে, বহুনামে উপাসিত হচ্ছেন। সুতরাং দেশ, কাল ও পাত্রভেদে অনুষ্ঠানগত ও আচারগত ভেদ পরিলক্ষিত হলেও উপাস্য ঐ একই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর।
প্রিয় আত্মন্, প্রতিটি মানবের আপন প্রকৃতিগত সংস্কার বা স্বভাব বিদ্যমান। মানবের ঐ স্বভাবই হল মানবের বৈশিষ্ট্য। ঐ স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য মানবের পূর্ব হতেই সহজাতক্রমে তার প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকে। স্বভাব-নির্দিষ্ট কর্মের দ্বারা ঐ বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে তার বিকাশ করাই হল সাধনা।
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান। আর গুণের তারতম্য অনুসারে মানব প্রকৃতিতে স্বভাবের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই কারণে আপন আপন প্রকৃতিগত স্বভাব অনুযায়ী সংসারে অনেক প্রকার উপাসনাগত ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং আচার-অনুষ্ঠানগত ভেদ, অধিকারী বিশেষে ভেদরূপে পরিলক্ষিত হয়। অতএব আমরা নিশ্চিত হলাম- সমস্ত উপাসনার উদ্দেশ্য বা পরম লক্ষ্য হল ঈশ্বর সাক্ষাৎকার। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্ম-সাক্ষাৎকার বা পরমেশ্বরের বোধ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধির হেতু বা অবিদ্যানাশের জন্য মানবের কর্ম ও উপাসনা একান্ত প্রয়োজন বা আবশ্যক। এই উপাসনা আবার অধিকারী বিশেষে ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম, কর্ম ইত্যাদি বৈচিত্র্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রিয় আত্মন—যার সদ্গুরুর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা এবং সাধনার প্রতি নিষ্ঠা আছে, তার অতি শীঘ্রই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। কে কি বলল, কার কি হল— এইরূপ ভাবনায় বিচলিত না হয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে আপন সাধনা করতে হবে। তাহলে ভগবৎ কৃপায় অতি শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করা যায়। তাই সাধনায় প্রথমত প্রয়োজন শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়ত ধৈর্য্য এবং তৃতীয়ত অনুরাগ বা ব্যাকুলতা। এগুলি সাধকের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। প্রতিটি জীবন সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রকাশ। প্রত্যেক জীবনে রয়েছে আধ্যাত্মিক রহস্য বা সেই তত্ত্ব। সুতরাং ঐ পরম সত্য প্রত্যেককেই বোধে বোধ করতে হবে। পরমাত্মার প্রকাশের জন্য মানবজীবন লাভ হয়েছে। তাঁর প্রতি অনুরাগ আসবার জন্য দেহে প্রাণ এসেছে। তাঁকে মনন করবার জন্য মানসিক বল এবং তাঁকে চিন্তা করবার জন্য বুদ্ধি আর তাঁর বোধের জন্য এই আনন্দময় তনু বা দুর্লভ মানবজীবন লাভ হয়েছে।
প্রিয় আত্মন্—সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ না করলে বিবেক জাগ্রত হয় না আর বিবেক জাগ্রত না হলে বৈরাগ্য আসে না এবং বৈরাগ্য না এলে সত্যনিষ্ঠা ও সত্যলাভ হয় না। ভাব ও অভাবের অধিষ্ঠান হল মানবের স্বভাব। এই স্বভাবই হল—মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য। অভাব হতে স্বভাবে এবং স্বভাব হতে মহাভাবে মানবের উত্তরণ করাই হল উপাসনার লক্ষ্য। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপে বিরাজিত ঐ সচ্চিদানন্দই চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার ও মন দ্বারা ব্যক্ত হয়ে সমস্ত লোকে বিচরণ করছে।
প্রিয় আত্মন্, সাধারণত মানবের অভিমানী মনের স্তর দ্বন্দ্বাত্মক, কেবল গুণপ্রদ বা কেবল দোষপ্রদ নয়। গুণের সঙ্গে দোষ, সুবিধার সঙ্গে অসুবিধা, অনুকূলতার সঙ্গে প্রতিকূলতা এবং সুখের সঙ্গে দুঃখ–এরূপ দ্বন্দ্ব চলছে। ঐ সকল দ্বন্দ্বযুক্ত অভিমানী মনের স্তর হতে সহজ সংগ্রাম করে মানবকে মুক্ত হতে হবে। মানবকে আত্মমুখী হতে হবে—অনাত্ম বিষয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে। ঐ অনাত্মক অভিমানী ভাবগুলিই আত্ম-স্বরূপ জীবনকে আত্মতত্ত্ব হতে বিস্মৃত রেখেছে। সেইহেতু সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ— এই সমস্ত ভাবগুলি ঐ অসহজ অভিমানী মনোজগতের চিত্তবিকার। এই অসহজ অবস্হা হতে সহজ স্হিতিতে যাওয়ার যে কলা-তাই উপাসনা বা আরাধনা।
এই উপাসনা প্রসঙ্গে প্রথমে এসে পড়ে ইষ্ট। সেইহেতু ইষ্ট বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। যাঁর স্মরণে বা অনুশীলনে মানবের সমগ্র অনিষ্ট দূরীভূত হয়—তাই মানবের ইষ্ট। ইষ্টকে একান্ত-ভাবে আত্মভাবনা না করলে ইষ্টের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হয় না আর ভালবাসা জাগ্রত না হলে আত্মসমর্পণের ভাব আসে না। আবার আত্মসমর্পণের ভাব না এলে ভগবৎ প্রেম লাভ হয়। না। সুতরাং ভগবৎ প্রেম লাভ করতে হলে আত্মসমর্পণভাব একান্ত প্রয়োজন। ইষ্টকে আত্মভাবে চিন্তা করতে হয় এবং ভাবে তন্ময়তা এলে একাত্মস্বরূপ হওয়া যায়। ভয় এবং হীনমন্যতা দ্বারা উপাসনা করলে ভগবৎ প্রেমের আবির্ভাব হয় না। সুতরাং ইষ্টকে অতি আপন অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন—এইরূপ একান্তভাবে আত্মভাবনা না করলে ইষ্টের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা আসে না । প্রশ্ন হতে পারে—আত্মসমর্পণের ভাব কিভাবে আসে ? উত্তরে বলতে হয়— অকপট বিশ্বাস হতে আসে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধা হতে আসে আনুগত্য, আনুগত্যের গভীরতাই হল উৎসর্গ আর আত্মোৎসর্গই হল আত্মসমর্পণ। ইষ্টের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসার উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা এনে দেয় আত্মসমর্পণের ভাব। আর আত্মসমর্পণের পরিণতিস্বরূপ ভগবৎ প্রেমের আবির্ভাব বা অমৃতলাভ । যা লাভ হলে ভক্ত আর কিছুই চায় না। প্রেমই পরমেশ্বর, যাঁর প্রাপ্তিতে আর চাওয়ার কিছু থাকে না। ভক্তিযোগের এবং ভগবৎ উপাসনার এটাই হল চরম পরিণতি বা পরমপ্রাপ্তি। এককথায় দ্বিধাহীনচিত্তে ইষ্টে অনুরক্তিই ভক্তি।
এই ভক্তিযোগের কতকগুলি অনুশীলন আছে—যার অভাবে আরাধনা পূর্ণতালাভ করতে পারে না। অনুশীলনগুলি হল—সর্বভূতে বা সর্বজীবে প্রীতি ও ভালবাসা, সর্বোপরি নীচ স্বার্থভাবনা ভুলে সর্বভূতের নিমিত্ত কল্যাণকামনা করা এবং সকলের নিমিত্ত ব্যক্তিসুখ-সুবিধা ও স্বার্থত্যাগ করা। এইরূপ সুমহান ত্যাগের মহিমায় ভক্তিযোগীর অন্তর বৈরাগ্যের আলোকে জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে—দেহ, মন ও বাক্য পবিত্র হয়। তখন ভগবৎ প্রেম দিব্যধারায় বিগলিত হতে থাকে ভক্তিযোগীর অন্তর্দেশে। সুতরাং সর্বভূতে ভালবাসা ও তার জন্য নিজ স্বার্থত্যাগ—এটাই ভক্তিযোগের চরম আদর্শ। ভক্তিযোগ ত্যাগ ও ভালবাসার শিক্ষা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে আত্মম্ভরিতা, স্বার্থান্ধতা, নিষ্ঠুরতা, সংঘর্ষ ও সামাজিক অশান্তির একমাত্র কারণ প্রেমের অপূর্ণতা।
প্রিয় আত্মন্—এই আরাধনায় অধিকারী ভেদে প্রতীকের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কারণ রূপ ও রেখার মধ্যে দিয়েই মানব-মনের ধর্ম প্রকাশিত। সেইজন্য প্রতীক ছাড়া চিন্তা-করা মানবিক স্তরে অসম্ভব। মানবের মন যতক্ষণ জান্তব অবস্হা বা অবিকশিত অবস্হায় থাকে, ততক্ষণ তার প্রতীকের অবশ্যই প্রয়োজন। মানবের মনের বিকাশের সাথে সাথে আরাধ্য প্রতীকের গুণগুলি চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ে। তখন আর মূর্তি বা প্রতীকে বিশেষ লক্ষ্য থাকে না—মূর্তি বা প্রতীক লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর মনের বিকাশের সাথে সাথে গুণও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন আসে এক চূড়ান্ত পরিণতি—যা মানবিক স্তরের ঊর্ধ্বে প্রকৃত সহজ আনন্দ বা অনাবিল ভূমানন্দ। ভক্ত সমাহিত হয় ভগবানে। আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের করুণা অপার। তুমিই তাঁর প্রকাশ—তোমাতে তিনি প্রকাশিত।
প্রিয় আত্মন্, সাধারণত নির্গুণ, নিরাকার তত্ত্ব খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই ধারণা করতে পারে। সেইহতু ঐরূপ অধিকারীদের নিকট সাকার উপাসনা অতি সহজ এবং সুলভ। ঐ সগুণ সাকারের সোপান অতিক্রম করে নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বে বোধে বোধ প্রাপ্ত হতে হবে। এইজন্য ঐ সকল উপাসকের প্রথমে সগুণ বা সাকার উপাসনার প্রয়োজন হয়। এই সাকার বা প্রতীক উপাসনার কথা ভাবলে আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্ন এসে উপস্হিত হয়, যথা—যদি সেই তত্ত্ব অচিস্তানীয় – অব্যক্ত হয়, তাহলে তা কেমন করে জ্ঞানের – বিষয় হতে পারে ? যদি সেই তত্ত্ব ভাবাতীত হয়, তাহলে কি করে ভাবনা তাতে আরোপ করা যায় ? যদি সেই তত্ত্ব নির্গুণ হয়, তাহলে মনন বা চিন্তন কেমন করে করা যাবে ? কারণ সমস্ত মনন বা চিন্তন তো আকারকে কেন্দ্র করেই। তাহলে নিরাকারকে কেমন করে চিন্তন করা যাবে ? নির্গুণের কেমন করে বিচার চলবে ? ভাবনার বিষয় না থাকলে কেমন করে ধ্যান হবে ? বিষয়-বিহীন ভক্তি কি সম্ভব ? —এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয় সগুণ বা সাকার উপাসনায়।
নির্গুণ উপাসনা হল অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা, যা আত্মবিচারকে মাধ্যম করে নেতিনেতি—নেতি করে সমাধি ও তত্ত্ব সাক্ষাৎকার। কিন্তু জ্ঞানমার্গের উত্তম অধিকারী ব্যতীত এই পথে উপাসনা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানব পরমেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে থাকে এইরূপ যে পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি জীব-জগতের বাইরে কোথাও অবস্হান করছেন কেউ বলে তিনি স্বর্গে, কেউ বলে বৈকুণ্ঠে, কেউ বলে বেহেস্তে আবার কেউ কেউ বলে তিনি হেভেন-এ—ইত্যাদি নানা মুনির নানা মত । কিন্তু তিনি যে সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত কিছু করবার সামর্থ্য রাখেন—এ সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নেই । তথাপি তাঁর নাম, আচার ও অবস্হান নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও মত-পার্থক্য সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে পরিলক্ষিত হয় ।
প্রিয় আত্মন্—পরমেশ্বর সর্বব্যাপী। পণ্ডিত হতে মূর্খ, যোগী, ভোগী, রোগী, উত্তম, অধম এবং সমস্ত চরাচর বিশ্বে ঐ একই পরমেশ্বর বিরাজমান। যা দেখছ—সবই তাঁর প্রকাশ। নাম ও রূপে কেবল ভেদ বিচিত্রতা দৃষ্ট হচ্ছে। এর কারণ অবিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা ঐ একই শক্তির দুইটি ক্রিয়া। সুতরাং নিরাকার তত্ত্বই প্রেমবশত সাকাররূপ ধরে প্রতিভাসিত। আকারেই নিরাকার আবার নিরাকারেই আকার। ভাণ্ডেতেই ব্রহ্মাণ্ড আবার ব্রহ্মাণ্ডেই ভাণ্ড ওতপ্রোত। বস্তুতঃ সেই তত্ত্ব নিৰ্গুণ, সগুণ—এই দুইয়ের অতীত। একাধারে সমস্ত কিছুই তাঁর প্রকাশ। এটাই সহজবোধে বোধিতত্ত্ব।
প্রিয় আত্মন্—এইবার ঐ ভক্তিযোগের প্রতীক উপাসনা বা মূর্তিপূজা হল আমাদের আলোচ্য বিষয়। সাধারণত মূর্তিপূজা যাঁরা করেন, তাঁদের ভিতর কেউ কেউ ভেবে থাকেন যে-মূর্তি ছাড়া আর কোথাও ঈশ্বর নেই। কিন্তু মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য তা নয়। তথাপি ঈশ্বর যখন সর্বত্রই আছেন বা তিনি যখন সর্বব্যাপী, সেহেতু মূর্তিতেও যে তিনি আছেন—এটা আশ্চর্যের কথা নয় । সুতরাং তাঁর উপাসনা অন্যভাবে যেমন সম্ভব, মূর্তিতেও সেরূপ সম্ভব। কিন্তু যাঁরা সেই সর্বব্যাপী, সর্বময় সত্তাকে ধারণা করতে পারেন না—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, আর যাঁরা জানেন ঈশ্বর সর্বব্যাপী অথচ তাঁকে ধারণা করতে পারছেন না—তাঁরাই মূর্তিপূজা বা প্রতীক উপাসনার অধিকারী। বস্তুত মূর্তিপূজা বা প্রতীক উপাসনা শুধুমাত্র প্রতীক উপাসনাই নয়, তা পরমেশ্বরেরই উপাসনা মূর্তিকে মাধ্যম করে। প্রতীক উপলক্ষ্য বা মাধ্যম মাত্র। যাঁরা মন্দিরে বা বিগ্রহে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আর কোথাও তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁরা আধ্যাত্মিক রহস্য অবগত নন।
প্রিয় আত্মন্, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। ঈশ্ববের সর্ব- ব্যাপকতা হেতু বিগ্রহে তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করে মূর্তিকে উপলক্ষ্য করে পরমেশ্বরের উপাসনাই মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য । বস্তুত মূর্তিপূজা উদারচিত্ত মনেরই প্রকাশ—সংকীর্ণচিত্ত মনের কল্পনা-প্রসূত নয়। মূর্তিটি সেই সর্বব্যাপী, সর্বময় পরমেশ্বরের প্রতীক মাত্র। পক্ষান্তরে পরমেশ্বরেরই উপাসনা। এটাই মূর্তিপূজার রহস্য বা তাৎপর্য। পরমেশ্বর সর্বব্যাপী — সর্বত্র বিরাজমান, মানুষের মাঝেও তাঁর প্রকাশ । শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রতীক বা বিগ্রহ ভাবাত্মক। এই ভাবাত্মক মূর্তিকে অবলম্বন করে এবং লঙ্ঘন করে যেতে হবে অসীমে । আর অসীমে যাওয়াই সাধকের লক্ষ্য বা কর্তব্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি এর সম্পূর্ণ বিপরীত, অমানবিকতা, অপকর্ম ও হাস্যকর সংকীর্ণতার প্রসার। আজ বিচারবিহীন আচার-অনুষ্ঠানই সত্য হয়েছে। মানবের বিচারবোধ ও বুদ্ধিমত্তা—অজ্ঞান ও নির্বুদ্ধিতায় সমাচ্ছন্ন হয়েছে। সংকীর্ণ চেতনা ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞতার ফলে সমাজে শ্রেণীচেতনা, সম্প্রদায় চেতনা, গোষ্ঠী চেতনা ইত্যাদি প্রকাশ পাচ্ছে।
প্রিয় আত্মন্ ! জীবন তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁকে জানো—তাঁকে ভালবাস—তাঁকে সেবা করো। মস্তিষ্ক দিয়ে তাঁকে জানো, হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালবাস ও শরীর দিয়ে তাঁকে সেবা করো।