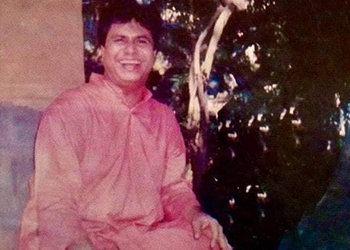স্থান ~ বনগ্রাম, পরমানন্দ মিশন ৷ সময় ~ ১৯৮৬ সাল । উপস্থিত ব্যক্তিগণ ~ নগেন, তপীমা, সব্যসাচী মান্না ইত্যাদি ।
জিজ্ঞাসু :– বর্তমানে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন রকমের সৎসঙ্গের কথা শোনা যায় এবং সেই সব সংঘ থেকে কিছু শিক্ষাও দেওয়া হয়— এরাও কি সমাজকল্যাণ করছে না?
গুরুমহারাজ :–দ্যাখো, আমি ‘সৎসঙ্গ’ বলিনা, আমি বলি — ‘সাধুসঙ্গ’। ‘সৎসংঘে’_ যোগদান করতে হয় ,আর সাধুব্যক্তির সঙ্গ করতে হয়। সৎসংঘে যোগদান করবে কেন — করবে এই কারণে যেহেতু_ সেই সংঘে অনেক সৎ ব্যক্তি রয়েছেন এবং তাঁদের দ্বারা নানান সামাজিক কল্যাণকর কাজ হয়ে থাকে! তুমি নিজে যদি ভালো মানুষ হয়েও থাকো, তবু ব্যক্তিগতভাবে আর কতটাই বা সমাজকল্যাণ করতে পারো? তুমি গৃহস্থী মানুষ, তোমার Limited রোজগার, তোমার উপর সংসারের অনেকে নির্ভরশীল — হয়তো স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছাড়াও বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা-মাতা রয়েছেন, কিন্তু মানুষের জন্য কিছু করার বাসনাও রয়েছে তোমার। সেক্ষেত্রে তুমি যদি কোন সৎসংঘে যোগদান করো_ তাহলে তুমি তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেখানকার বিভিন্ন প্রকার কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে এবং তোমার দ্বারাও জগতকল্যাণমূলক কাজ হয়ে চলবে। ‘নিষ্কাম কর্ম’- করার এর থেকে সহজ রাস্তা আর কি হতে পারে! আর প্রতিটি মানুষেরই তো নিষ্কাম কর্ম করা প্রয়োজন_ কারণ জন্ম-জন্মান্তরের যে কর্মফল তার কতটুকুই বা ব্যক্ত (অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। গীঃ — ২/২৮) বেশিরভাগটিই অব্যক্ত, যা সঞ্চিত কর্মরূপে জমা রয়েছে। সেই সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করার একটাই উপায় আর তা হলো নিষ্কাম কর্ম করে যাওয়া।
এছাড়া আর কি করবে _ সাধুব্যক্তির সঙ্গ করবে। সাধু কে? — যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। নিত্যানিত্যের বোধ যাঁর হয়েছে, যাঁর বিবেক সদাজাগ্রত! সাধুসঙ্গে মানুষের বিবেকের জাগরণ ঘটে। বিবেক সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু প্রসুপ্ত আছে — তা সাধুর সংস্পর্শে জেগে ওঠে। বুঝেছ ব্যাপারটা ! এবার শিক্ষাগ্রহণ করার বিষয়ে বলি — যে শিক্ষা তোমার চেতনার উন্মেষ ঘটাবে, তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করবে, যা তোমাকে সমস্ত রকম অন্যায় কার্য থেকে দূরে রাখবে__ তাই গ্রহণীয়। কু-শিক্ষাও শিক্ষা কিন্তু তা গ্রহণীয় নয়।
এবার কথা হচ্ছে — সু-শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত শিক্ষকের। নাহলে যে কোন শিক্ষাই কুশিক্ষায় পরিণত হতে পারে। যিনি সুশিক্ষা দেন, তিনিই 'আচার্য' — অর্থাৎ যিনি সেই সকল শিক্ষাকে জীবনে আচরণে এনেছেন। যেমন একটা শিক্ষার কথা ধরা যাক — "বাঁচা-বাড়ার মর্মই ধর্ম"। এবার এই শিক্ষাকে যদি স্থূলভাবে গ্রহণ করো তাহলে মনে হবে যেন — মানুষকে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করতে হবে। কারণ বাঁচতে গেলে বলিষ্ঠ হতে হবে _আর বাড়তে গেলে প্রচুর বংশবিস্তার করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তো সত্য নয়। 'আহারনিদ্রামৈথুনঞ্চভয়ম্'। — আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয় — এটা সাধারণত জীবের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য হলেও __মানুষের বৈশিষ্ট্য এটা হতে পারে না। মানুষ পৃথিবী-গ্রহের শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু সে শ্রেষ্ঠ কেন — তার বুদ্ধি বা শক্তি বেশি বলে? — না। এগুলি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হতে পারেনা। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর দাস নয়, সে আহার-নিদ্রা-মৈথুন বা ভয়ের দাসত্ব করতে বাধ্য নয় — সে এগুলিকে অতিক্রম করতে পারে, তাই সে শ্রেষ্ঠ। মহামানবরা তাঁদের জীবনে এগুলিকে অতিক্রম করে দেখিয়ে গেছেন, তাই আজও তাঁরা আমাদের আদর্শ।জেনে রাখবে, সৎসংঘেই সদব্যক্তিরা থাকেন। সৎসংঘের পরম্পরা কখনই বংশানুক্রমিক নয়। জীবন-বিজ্ঞান কি বলছে — মানুষের দেহ অর্থাৎ আকৃতি বংশানুক্রমিক কিন্তু প্রকৃতি বা স্বভাব নয়। এটি মানুষের পূর্বপূর্ব জন্মের সংস্কার থেকে পাওয়া। তাই রবীন্দ্রনাথের ছেলে বিখ্যাত কবি হলেন না, আবার বিদ্যাসাগরের ছেলে বিদ্যাসাগর হলেন না! কোন কোন পরিবারে উন্নত সন্তানেরা বংশানুক্রমিকভাবে যে জন্ম গ্রহণ করে — সেটা তাদের সংস্কার, কিন্তু ‘স্বভাব বা প্রকৃতি পিতামাতা অনুযায়ী হবেই’ — এটা যদি জীবনবিজ্ঞান-সম্মত হোত, তাহলে সকলের ক্ষেত্রেই এইরমটা ঘটত! কিন্তু বাস্তবে আমরা তা দেখিনা। ঋষি পরম্পরার বন্দনায় যে ঋষিদের নাম রয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন বংশপরম্পরার গূরু এবং বেশিরভাগই রয়েছেনগুরু-শিষ্য পরম্পরার গুরু। যেমন — “ওঁ নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্ত্রিং চ তৎপুত্র পরাশরং চ। ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্।।’
সুতরাং, যে কোন শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত শিক্ষকের। প্রায় ১৫০০ বছরের বিদেশী শাসনের সময় বিদেশীরা ভারতবর্ষের আচার্যকুলের উপর চরম আঘাত হেনেছিল। ইউরোপে নবজাগরণের ফলে ওদের উন্নতি হতে থাকল কিন্তু ভারতবর্ষ যথার্থ আচার্যের অভাবে ততটাই পিছিয়ে পড়তে থাকল। এই সুযোগে ভারতবর্ষেরই জ্ঞানরাজি নিয়ে ওরা পৃথিবীকে ঋষিদের শিক্ষার নানান অপব্যাখ্যা শেখাতে লাগল। উপযুক্ত আচার্যের অভাবে সেইসব শিক্ষাই আবার ফিরে এসেছে ভারতবর্ষে। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম আধুনিক ঋষি-পরম্পরার প্রতিনিধি, যিনি সদর্পে সনাতন ধর্মের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং ভারতবর্ষের সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরলেন। এমনকি ইউরোপের অনেক ভুল তথ্যকে শুধরে দিলেন। জীবনের উদ্দেশ্য কেবল 'বাঁচা ও বাড়া'ই নয়। স্বামীজী বললেন — "ওঠো, জাগো", অর্থাৎ চেতনার উত্তরণ আর বিবেকের জাগরণই ধর্মরাজ্যে প্রবেশের সোপান। যাইহোক, এরপর দেখা যায় আরও অনেক আচার্য দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, পরে আরও অনেকে যাবে এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পৃথিবীকে সঠিক ইতিহাসের সন্ধান দেবে। এঁরাই বেদান্তের শিক্ষাকে অধিকতর গ্রহণীয় করে Practical বেদান্ত হিসাবে বিশ্বের সব দেশের সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবে। এর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তোমরা যারা এখনও ছোট আছো_তারা, বা তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মেরা ভারতবর্ষের সুদিন দেখতে পাবে।জিজ্ঞাসু :– ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, দশবার ‘গীতা’ উচ্চারণ করলে যা হয় গীতার মর্মার্থ তাই। কিন্তু তৎকালীন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ভেবেছিলেন গীতার মর্মার্থ ‘ত্যাগী’ হতে পারে – ‘তাগী’ নয়। কিন্তু পরে ব্যাকরণগতভাবে ভেঙে দেখা গেল ‘তাগী’ শব্দটাও ত্যাগীর সমার্থক শব্দ এবং ব্যাকরণসম্মত! আপনার ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ প্রায়শই দেখতে পাই। এখন আমারে জিজ্ঞাসা এই যে, এরূপ হয় কেন? তাহলে কি আমরা এটা বুঝব যে, মহাপুরুষরা যা বলেন সবই সত্য?
গুরুমহারাজ :— দ্যাখো মহাপুরুষদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু অবতারসমূহ বা ভগবান যখন নিজে আসেন __তখন তাঁর Activities, তাঁর চাল-চলন কোনকিছুই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। ঐ জন্যই বলা হয়েছে ‘লীলা বোঝা ভার’। তিনি সর্ব রসের রসিক, সর্ব জ্ঞানের জ্ঞানী – আরও কত কি! তিনি ফিচলেমি, হালকা হাসি-ঠাট্টাতেও ‘মাষ্টার”আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহকে সহজভাবে উপস্থাপন করারও “মাষ্টার”। সাধারণ গেঁয়ো অশিক্ষিত-দরিদ্র মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী, আবার সমাজের মহাপণ্ডিত-বিজ্ঞানী-গবেষকদেরও আচার্য —- এরকম আরও বহুকিছু বলতে পারো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন – তিনি শুঁটকো সাধু হতে চাননা, সানাইয়ের পোঁ-ধরা নয়, তিনি রাগ-রাগিণী বাজাবেন – অর্থাৎ বৈচিত্রের কথাই বলতে চেয়েছেন।
তাই ভগবানকে ‘কোন একটা কিছু’ দিয়ে তুমি মাপতে যেয়ো না বা বুঝতে চেয়ো না। সবটা মিলেই ঈশ্বরতত্ত্ব! তাঁর ভুল – তাঁরই ঠিক, তাঁর সত্য – তাঁরই মিথ্যা – কোনকিছুই তো তাঁকে বাদ দিয়ে নয়! শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পালাচ্ছেন, সেটাও লীলা – তাই তিনি ভক্তদের কাছে আজও “রণছোড়জী”-রূপে পূজিত। আমার কথার মর্মার্থটাকে বোঝার চেষ্টা কর। তবে হ্যাঁ, যখন তিনি কোন তত্ত্ব পরিবেশন করছেন, তখন একশভাগ সঠিক। কোন উদাহরণ টানছেন – একশ শতাংশ appropriate. ওখানে কোন ফাঁকি পাবে না। যেমন দ্যাখোনা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই “একশ ভাগ” কথাটা বোঝাতে “পাঁচসিকে পাঁচআনা” কথাটাব্যবহার করতেন। অনেকেই এমন ধারণা করে যে, ওটা অতিরিক্ত বোঝাতে বা খুববেশি বোঝাতে ঠাকুর একটা “কথার কথা” -রূপে ব্যবহার করতেন, কিন্তু তা সত্যি নয়। এরও একটা কারণ এবং মানে আছে।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ছোট, সেই সমসাময়িক কালে 'নয়া' আর 'পয়সা' নিয়ে মানুষের মধ্যে হিসাবে খুবই গণ্ডগোল হত। হিসাবটা ছিল ২ পয়সায় ৩ নয়া, অর্থাৎ ৪ পয়সায় ৬ নয়া। আবার ৬ নয়ায় ১ আনা, অর্থাৎ ৪ পয়সায় ১ আনা। এইভাবে ৪ আনায় ১ সিকে অর্থাৎ ১৬ পয়সায় ১ সিকে। আবার ৪ সিকায় ১ টাকা অর্থাৎ ৬৪ পয়সায় ১ টাকা।তাহলে ‘নয়া’-র হিসাবে ১০০ নয়ায় ১ টাকা কিন্তু ‘পয়সা’-র হিসাবে ৬৪ পয়সায় ১ টাকা। এই যে গণ্ডগোলের হিসাব – এটাকেই ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে “গিরিশের ভক্তি’ কিম্বা ‘কৃষ্ণকিশোরের ভক্তি’বোঝাতে! যেন পাঁচসিকে পাঁচআনা।” অর্থাৎ ‘নয়া’র হিসাবে ১০০ নয়, পয়সার হিসাবে ১০০। কেননা পাঁচসিকে মানেই ৫×১৬ = ৮০ পয়সা আর পাঁচ আনা মানে ৫×৪ = ২০ পয়সা অর্থাৎ মোট ১০০ পয়সা। এই হিসাবে ১০০ নয়া নয়_ যেন ১০০ পয়সা ভক্তি! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের কাছে বিরাট বিস্ময়। যে কোন সময় যে কোন মানুষ যদি ঠাকুরকে চিন্তা করে – তাঁর জীবন পর্যালোচনা করে, তাহলে শুধু বিস্মিতই হবে – শ্রদ্ধান্বিতই হবে _তা ছাড়া সে আর কি-ই বা করতে পারে! দ্যাখো প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের শরীরধারণ, নররূপে লীলা করা এই সমস্ত ব্যাপারটাই তো বিস্ময়ের!