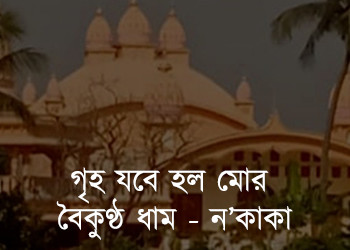ঈশ্বর চির প্রকাশমান। তাঁর প্রকাশটা নরলীলায় বেশী বােঝা যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, দেখাে সূর্যের প্রকাশ সর্বত্রই কিন্তু কাঁচের মধ্যে দিয়েই সেটা বেশী প্রতিফলিত হয়। তাই এই নরলীলাকে অবলম্বন করেই তিনি বেশী প্রকাশিত হন। এই মনুষ্যশরীরে এসেই তিনি ভগবানের জয়গান করে যান, নিজে সাজেন, মানুষকে সাজান।
যখনই ধর্মের মধ্যে গ্লানি আসে তখনই তিনি আবির্ভূত হন, ধর্মের গ্লানি অপসারিত করে ধর্মের পুনঃস্থাপন করতে। গৌরসুন্দর লীলা শুরু করেছিলেন নবদ্বীপে আর শেষ করেছিলেন নীলাচলে। তাঁকে নিয়ে যে “পঞ্চতত্ত্ব”, তাঁদের মধ্যে সবচাইতে আগে আগমন ঘটেছিল অদ্বৈত আচার্যের। তিনি যেন ক্ষেত্র-প্রস্তুত করার জন্য, আসর সাজাবার জন্য আগেই চলে এসেছিলেন। ফলে নিতাই, গৌরসুন্দর এবং গদাধর বয়সে নবীন হলেও আচার্য ছিলেন প্রৌঢ়। কিন্তু আচার্যের শরীর শক্ত-সমর্থ ছিল। যে কোন নৃত্যের আসরে অথবা সুরধনীর জলে জলকেলি করার সময় নিত্যানন্দের সঙ্গে আচার্যের যে কৃত্রিম প্রতিযােগিতা ও মশকরা চলত—যা দেখে মহাপ্রভুও মৃদু মৃদু হাস্যে উপভােগ করতেন, তাতে কিন্তু কখনই অদ্বৈত আচার্য ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়তেন না।
প্রায় ৬০০ বছর আগেতে এই ধর্মের অবক্ষয়ের সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য অদ্বৈত। ধর্মের কলুষতা দেখে তিনি সবসময় তাঁর প্রাণের দেবতা বিষ্ণুকে চোখের জলে ডাকতে থাকেন। কখনাে দেখা যায় কোশাকুশি নিয়ে বিষ্ণুমন্দিরে দিনরাত চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। আর শুধু প্রার্থনা করছেন, ‘প্রভু, কবে তুমি শরীরে এসে মানুষের ক্লেশের অবসান করবে। জীবকুল আজ ভ্রষ্টাচারসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। প্রভু, আমি তােমার আগমন বার্তার পথ চেয়ে বসে আছি। হে অনন্তশায়ী বাসুদেব, আমার এই মহতি আশা কবে পূরণ করবে। কবে আসবে নবযুগের ভগীরথ নূতন শান্তিবারিতে তৃষিতের আশা পূরণ করতে।’
ভাবের ঘােরে আচার্য দেখলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুর অনন্তবাসুদেব স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে কারণ থেকে রূপ পরিগ্রহ করলেন। ঐ রূপ দেখতে দেখতে আচার্যদেব আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। আনন্দে অভিভূত হয়ে আচার্য সকলকে বলতে লাগলেন—তাঁর মনের মানুষ আসছে। আর আনন্দে দিন গুনতে লাগলেন। অবশেষে অদ্বৈত প্রেমহুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন। তাঁর প্রেমহুঙ্কারেই গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ! কে এই অদ্বৈত ? শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামের কুবের পণ্ডিতের পুত্র। মায়ের নাম নাভা দেবী। লাউড়ে বাড়ি বলে সবাই ডাকে ‘নাড়াবুড়া’ বলে। গৌরাঙ্গের কাছে নাড়া। অদ্বৈতের যখন ৫২ বছর বয়স তখন গৌরাঙ্গের জন্ম হয়।
কুবের আচার্য রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পূর্বে হিন্দু রাজাদের খাস পরিচারকদের মাথা ন্যাড়া থাকত। সেই থেকে সমস্ত প্রিয় পার্শ্বচরদের নাম হয়ে গিয়েছিল “নাড়া”। এইজন্য অদ্বৈতকে “নাড়া” বলে ডাকা হত। বাল্যনাম কমলাক্ষ। হাতেখড়ির পর কমলাক্ষ পাঠশালায় ভর্তি হলেন। সেখানে সহপাঠী পেলেন স্বয়ং রাজপুত্রকে। রাজপুত্র কমলাক্ষের দৌরাত্ম্যে জবুথবু। শিশু কমলাক্ষের ব্যবহার ছিল মধুর। তাই তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। সহপাঠী বলে রাজকুমার কমলাক্ষকে একদিন তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। রাজা দিব্যসিংহ জিজ্ঞাসা করেন—’ও কে ?’ রাজকুমার বলে—’আমার সহপাঠী।’ আর বড় পরিচয় তাঁর সভাপণ্ডিতের ছেলে। বালককে দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শােনা যায় রাজা দিব্যসিংহ ছিলেন শক্তি-উপাসক। অদ্বৈতের প্রভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিষ্ণু উপাসক হয়ে যান। কমলাক্ষের বয়স যখন ১২ বৎসর তখন অধ্যয়নের জন্য কুবের পণ্ডিত পুত্রকে শান্তিপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর কিশাের শিক্ষার্থী কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি এবং ষড়দর্শনের পাঠ আয়ত্ত করে নিলেন।
কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট্ট হতে পুত্রের সঙ্গে একত্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে বসবাস করতে থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁর পিতা-মাতার দেহত্যাগ হয়। পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এরপর থেকেই তীব্র বৈরাগ্য শুরু হয়। স্থির করলেন গয়ায় গিয়ে পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করবেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে বের হবেন তীর্থ পর্যটনে।
ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্খা তাঁর অন্তরে তীব্র আকার ধারণ করল। গয়ার কার্য শেষ করে কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে বের হলেন। মনের একান্ত ইচ্ছা এবং খোঁজ—“কোথায় আমার সদগুরু যাঁর চরণে এই দেহ-মন সমর্পণ করব।”
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে একদিন তিনি একদল মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ী সাধুর সভায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে নারদীয় সূত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তিনি ভাবাবেশে মূৰ্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁর সারা অঙ্গে দিব্যভাবের লক্ষণ দেখা দিল। ঐ সভাতে উপস্থিত দাক্ষিণাত্যের পরম ভক্তি-সাধক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী কমলাক্ষের ভাবাবেশ লক্ষ্য করে বিস্ময়ান্বিত হলেন। অন্যান্য সমবেত ভক্তরাও ঐ ভাব দেখে উচ্চস্বরে নামকীর্তন করতে লাগলেন। কমলাক্ষের সম্বিত ফিরলে সামনে দণ্ডায়মান মাধবেন্দ্রকে দেখে তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন এবং তাঁর কাছে আশ্রয় ও দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। মাধবেন্দ্র পুরী তখন তাঁকে কৃপা করলেন–বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।
দীক্ষাতে কমলাক্ষের জীবনে দ্রুত রূপান্তর ঘটতে লাগল। পরিব্রাজক কমলাক্ষ একে একে বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা সমাপন করে অবশেষে শান্তিপুরে ফিরলেন নিজ আবাসস্থলে। শান্তিপুরে ফিরে তিনি চতুম্পাঠী খুললেন। এইসময় বহু প্রতিভাধর বিদ্যার্থীরা আসে অদ্বৈত আচার্য্যের সান্নিধ্যে। এই মহাত্মার জীবনকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে লাগল।
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী কমলাক্ষকে একটি কথা বলে দিয়েছিলেন—‘বৎস, তুমি এবার বিবাহ করে সংসারী হয়ে সংসার থেকে কৃষ্ণনাম প্রচার কর, জীবের কল্যাণ হবে।’ যথাসময়ে গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর ইচ্ছায় অচিরেই বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটে গেল। নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ী ধর্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর দুটি যমজ কন্যা সীতা ও শ্রীরূপা। এই দুই কন্যাকে তিনি অদ্বৈতের কাছে সম্প্রদান করলেন। শান্তিপুরে তখন অদ্বৈতের খুবই প্রভাব প্রতিপত্তি। বহু শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে ভক্তিশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অধিকার। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির কথা শুনে বহু জ্ঞানী-গুণী ছাত্র তাঁর সান্নিধ্যলাভ করার জন্য আসতে থাকে এবং তারা প্রত্যেকেই কম-বেশী আচার্যের কৃপাও পেল। আচার্যের গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের খ্যাতিও এই সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।
পরম ভাগবত প্রেমিক হরিদাস সেদিন অদ্বৈতের সঙ্গ করতে এসেছেন। হরিদাসের আগমনে আচার্য্যের অন্তর আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। শান্তিপুরের ব্রাহ্মণেরা যবন হরিদাসের কথা জানতেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথাও তাদের জানা ছিল। কিন্তু এক শ্রেণীর নিন্দুক থাকে, যারা মহতের মহানুভবতা সহ্য করতে পারে না। তাই হরিদাস তাদের চক্ষে অবজ্ঞেয়। তারা আচার্যদেবকে বললেন– “আপনি যদি হরিদাসের সঙ্গ না ত্যাগ করেন তাহলে আপনাকে একঘরে করা হবে।”
ইতিমধ্যে শান্তিপুরে একটা ঘটনা ঘটে গেল। এক ধনী বিত্তবানের বাড়িতে সেদিন উৎসব চলছিল। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত। আহারের আয়ােজন হয়েছে। এমন সময় এক সন্ন্যাসী সেখানে হাজির হলেন যিনি দিব্যজ্যোতির্ময় সাধক—পরম ভাগবত প্রেমিক পুরুষ। সেই কল্পতরুসদৃশ সন্ন্যাসীর কাছে যে যা ভিক্ষা চাইছে তাই পাচ্ছে। তাঁর পদধূলি গায়ে মাথায় মেখেই মানুষের দুরারােগ্য ব্যাধিও সেরে যেতে লাগল। কল্প বৃক্ষতলে বিশাল লােকের ভিড়। উৎসব গৃহের কর্মকর্তারা এতবড় মহাত্মার সেবার উদ্দেশে সেখানে ছুটে এলেন। গলবস্ত্র হয়ে মহাজনের নিকট নিবেদন করলেন– “আপনি দয়া করে। আমার গৃহে অনুগ্রহণ করুন।” সন্ন্যাসী ভাবাবিষ্ট অবস্থায় উত্তর দিলেন, “বাবা, আমি বিষ্ণুর প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করি না।” তখন গৃহে নারায়ণ শিলা ছিল, সেখানে ভােগ নিবেদন করে ঐ প্রসাদ তাকে দিতেই তিনি। তা সানন্দে গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে অদ্বৈত আচার্য সেখানে উপস্থিত। সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীকে ডেকে বললেন। –‘একি হরিদাস, তুমি এখানে ! এ বড় আশ্চর্যের বিষয় ! গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা তােমাকে নিয়ে পঙক্তি ভােজনে বসেছেন। এ তােমার কোন ঐশ্বর্যের প্রকাশ?’ অদ্বৈতের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের ভাবাবেশ কেটে গেল। বাহ্যজ্ঞান পেয়ে হরিদাস বললেন, ‘প্রভু, আমার দোষ নেবেন না। কৃষ্ণকৃপায় এই এঁরা আমার কি দৃষ্টান্ত দেখেছে জানিনা। তাই পঙক্তি ভােজনের মধ্যে বসিয়েছেন।’ আচার্যের চরণতলে পড়ে হরিদাস-ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন, তার দু’চক্ষে প্রেমাশ্রু বইতে লাগল। আর অবিরল অশ্রুপাতে আচার্যের চরণদ্বয় বন্দনা করে ভাব বিহ্বল অবস্থায় আচার্যের স্তব করতে লাগলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন এবং হরিদাসের শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রশংসা করতে লাগলেন। পূর্বে কিছু লােক হরিদাসের অলৌকিক কাহিনী শুনেছিলেন। কিন্তু আজ তারা প্রত্যক্ষ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করলেন। হরিদাসের এই লােকোত্তর কাহিনী দেখে তারা পূর্বের অপরাধ মার্জনার জন্য আচার্যের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিলেন। হরিদাসের প্রকৃত মহিমা সঠিক বুঝলেন একমাত্র অদ্বৈতাচার্য — পরম ভগবৎপুরুষ। তাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রথম ভােজ্যপত্র ভক্তিসিদ্ধপুরুষ যবন হরিদাসকেই নিবেদন করেছিলেন। আসলে মহাপুরুষ ছাড়া মহাজনের লীলা কে বুঝবে! এই হরিদাস ও অদ্বৈতের মিলনে ভক্তিজগতে মানুষে মানুষে ব্যবধান রইল না।
অদ্বৈতের মনে শুধু প্রশ্ন উঠতে লাগলাে মানুষ শুধু কৃত্রিম অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। মূল তত্ত্বে উপনীত হবার প্রচেষ্টা কেউ করে না, এটাই শুধু দুঃখ। কিভাবে মানুষের এই মােহঘাের কাটবে! প্রার্থনা করতে লাগলেন, “এর সমাধান কর প্রভু।” তাইতাে অদ্বৈত তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়ে কৃষ্ণের পুজো করেন আর প্রেমাপ্লুত হয়ে প্রেমময়কে ডাকেন,“প্রভু, কবে তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তের মনস্কামনা পূরণ করবে!”
অবশেষে অদ্বৈত নবদ্বীপেও টোল খুললেন, সেখানে দলে দলে ছাত্র আসতে লাগলাে। অদ্বৈতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলাে। শুভ ফাঙ্গুনী পূর্ণিমায় গৌরহরি আবির্ভূত হলেন। ধরণীর গ্লানি অপনােদন করার জন্য। আচার্যদেব সীতাদেবীকে শচীমাতার গৃহে পাঠালেন ধান-দূর্বা দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করতে যাতে অপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে। তাঁর নাম রাখা হল নিমাই। ভালাে নাম বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত বালককে দেখলেন, দেখে শুনে বুঝলেন এই সেই যুগপুরুষ পরিত্রাতা, যাঁর জন্য এত প্রতীক্ষা। সে যাইহােক, প্রভু নিজে ঘােষণা না করলে কি ভাবে আমি নিঃসংশয় হই। অদ্বৈতের মন্দিরে বড় ভাই বিশ্বরূপের সঙ্গে নিমাই মাঝে মাঝে আসেন। একজন আসে শাস্ত্র শিখতে আর একজন আসে দেখা দিতে ৷ এই শুরু, তারপর দিন যায়, ভাগীরথীর জলধারা সময়ের সঙ্গে বয়ে যায় সাগরের দিকে। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নেবার পর শচীমাতা অদ্বৈতের উপর চটে আগুন। ফলে নিমাই-এরও যাওয়া বন্ধ। তাই এখানকার দেখাশুনা ঠারেঠোরে লুকিয়ে-চুরিয়ে।
নিমাই-এর পিতৃবিয়ােগের পর থেকেই সে কেমন যেন অন্যমনস্ক। গুরুস্থানীয়ের পরামর্শে গয়ায় পিণ্ডদান করতে গেলেন নিমাই। গয়া থেকে ফিরে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হলেন। রামাই পণ্ডিতকে বললেন, ‘অদ্বৈতকে খবর দাও তিনি যেন সন্ত্রীক পূজার দ্রব্যাদি নিয়ে এখানে চলে আসেন।’ রামাই পণ্ডিতের কথা শুনে অদ্বৈত বললেন, “আমি নন্দন আচার্যের বাড়ি লুকিয়ে থাকবাে। তুমি গিয়ে প্রভুকে বলবে আচার্য এলাে না।” ফিরে গিয়ে রামাই প্রভুকে বলল, ‘অদ্বৈত আচার্য এলেন না’। অন্তর্যামী প্রভু সরাসরি রামাইকে বললেন, “যাও, নন্দন আচার্যের বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে এস।” রামাই তখনই নন্দন আচার্যের বাড়ি গিয়ে অদ্বৈতকে বলল, “চলুন ধরা পড়ে গেছেন।” অদ্বৈত ভাবলেন কে ধরা পড়ল আমি না প্রভু! তিনি শ্রীরামের ঘরে গিয়ে দেখলেন বিষ্ণু খট্টায় বসে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ছত্র ধারণ করে আছে আর গদাধর তাম্বুল দানে রত। দৃশ্য দেখে অদ্বৈত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর গৌরাঙ্গ তাঁর মাথায় পা রেখে নিজের গলার মালা তাঁর গলায় পরিয়ে বললেন, “নাড়া, তুমি বর চাও।” অদ্বৈত বললেন, “তােমার দর্শনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে। তারপর কি বর আছে প্রভু !” গৌরহরি বললেন, “তােমার সকাতর আহ্বানেই আমার এবার কাজ মানুষের মধ্যে ভক্তিভাব বিতরণের।”
অদ্বৈতে গৌরাঙ্গের গুরুবুদ্ধি। লৌকিক আচারে মাধবেন্দ্র গৌরাঙ্গের গুরুর গুরু, আর অদ্বৈত মাধবেন্দ্রর শিষ্য। এই হিসাবে অদ্বৈত গৌরাঙ্গের গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই হচ্ছেন। সেজন্য অদ্বৈত গৌরাঙ্গের প্রণম্য। গৌরাঙ্গ তাই প্রাণভরে অদ্বৈতকে প্রণাম করেন।
অদ্বৈতের এটা ভালাে লাগে না। তাঁর কাছে গৌরাঙ্গপ্রভু কৃষ্ণ আর কৃষ্ণদাস হবার আনন্দ কোটি ব্রহ্মানন্দের চেয়েও আনন্দের। অদ্বৈতের ইচ্ছা প্রভুর পদতলে ধূলায় ধূসরিত হয়ে যায়। অন্তর্যামী প্রভু তাঁর অন্তরের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবেন না। তাই যখন প্রভু শুনলেন আচার্যদেব ভক্তির চেয়ে জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে বড় করছেন তখন তিনি ছুটলেন শান্তিপুরে, অদ্বৈতকে শাসন-পীড়ন করতে। প্রভুর লীলাকে আরো প্রগাঢ় করার জন্য আচার্যদেব পিঁড়ার উপর বসে অধিক উৎসাহে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।
প্রভু গর্জন করে বলে উঠলেন, “নাড়া বলাে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?” আচার্যদেব বললেন, “জ্ঞান বড়। কারণ যার জ্ঞান নেই তার শুধু ভক্তিতে কি হবে !” প্রভু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পিঁড়া হতে আচার্যদেবকে টেনে নীচের উঠানে ফেলে প্রবলবেগে প্রহার করতে লাগলেন। অদ্বৈতের ইচ্ছা পূর্ণ হল। এরপর তিনি পরম সুখে নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন, “আমার ইচ্ছা পূরণ করে তুমি তাে ঠাকুরের ঠাকুরালি দেখালে।” তখন আচার্যদেব বলতে লাগলেন, “ভক্তি বড়, ভক্তি বড়, ভক্তি দিয়ে সব জয় করা যায়।” শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রকাশের দিনে মহাপ্রভু সকলকে প্রেম-ভক্তি দান করলেন একমাত্র শচীমাতা ছাড়া, কারণ শচীমাতার বৈষ্ণব অপরাধ হয়েছে। তবে এই শাস্তির খণ্ডন হয়, উপায় হচ্ছে একটি মাত্র প্রণাম মহাজনকে। পরম বৈষ্ণব অদ্বৈতকে শচীমাতা পূর্বে তিরস্কার করেছিলেন বলেই শচীমাতা অপরাধিনী। কি অপরাধ ? না বড় ছেলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হওয়ার পর ছােটছেলেও বুঝি সন্ন্যাসী হয় এই অদ্বৈতের জন্য, এইজন্য তাঁর উপর দোষারােপ করেছিলেন তিনি।
শচীনাতা অদ্বৈতকে প্রণাম করে পদধূলি নিতে গেলে আচার্য রাজি হলেন না। বললেন–’কি করে আমি মা যশােদাস্বরূপিণী মায়ের প্রণাম নিই।’ তারপর শচীমাতার মহিমা কীর্তন করতে করতে তিনি আবেশে মূৰ্ছিত হয়ে গেলেন আর ঐ সুযােগে তাঁকে প্রণাম করে নিলেন শচীমাতা। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের খণ্ডন হয়ে গেল। শচীমাতার দেহ-মনে ভক্তিরসের প্রবাহ বইতে শুরু করল–তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলেন।