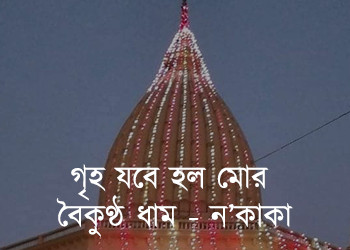ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। যুগে যুগে কালে কালে অসংখ্য ঋষি, মুনি, তাপস, যােগী, মহাযােগী ও সাধক-মহাপুরুষেরা এসেছেন পরম্পরায়। মহাপুরুষদের জীবন লােকোত্তর। তাঁরা আবির্ভূত হন মানুষের জীবনে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ তাপ নাশ করার জন্য। মনের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা দূর করে সমাজকে ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হন তাঁরা কালে কালে। কালকে জয় করেছেন এমন কিছু মহৎ ব্যক্তি, তাঁরাই হলেন কালজয়ী পুরুষ। এইসব ব্যক্তিরা বনে-জঙ্গলে, গিরি-গুহায়, লােকচক্ষুর অন্তরালে বা কোন নির্জনস্থানে বসে করেন প্রেমময়ের সাধনা। সেই অনন্ত প্রেমিকপুরুষকে উপলব্ধি করার জন্যই করেন নিরন্তর সাধনা। যখন তাঁরা সাধনায় সিদ্ধ হন, তখনই তাঁদের উপলব্ধির কথা মানুষজনকে বলতে থাকেন। তাঁদের উপলব্ধি হল মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব কারণ এই মনুষ্যশরীর দিয়েই ভগবানকে জানা যায়। এক মহাজন পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের পর মনুষ্যজগৎকে শােনালেন– “শােনরে মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” এই শাশ্বত বাণী শুনে মনুষ্যসমাজ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল—কে এই মহান ? এই মরমিয়া সাধক হলেন প্রেমিকপুরুষ চণ্ডীদাস। তিনি ছিলেন বীরভূম জেলার অন্তর্গত নানুর গ্রামের বাশুলী দেবীর পূজারি। বাল্যকাল থেকেই এই ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন সরল ও উদাসীন। অল্প বয়সে চণ্ডীদাসের বাবা, মা মারা যায়। ফলে নিঃসম্বল চণ্ডীদাসের পক্ষে নিয়মমাফিক লেখাপড়া শেখার কোন সুযােগ হয়নি। তাঁর নিজের রচনা থেকেই জানা যায়, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর যদিও তাঁর গ্রামে কয়েক জন নিকট আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু দুর্দশাপীড়িত চণ্ডীদাসের ভরণপােষণ নিতে কেউ সম্মত হয়নি। সে কারণে তাঁকে কষ্টের মধ্যেই দিন অতিবাহিত করতে হয়। শেষে গ্রামবাসীদের অনুগ্রহে উপনয়নের ঠিক পরেই, তিনি বাশুলীদেবীর সেবার ভার প্রাপ্ত হন। এতে তাঁর কষ্টের কিছুটা লাঘব হয়। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এবং জন্মতারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এক দলের মত হচ্ছে তিনি বীরভূম জেলার নানুর গ্রামে জন্মেছিলেন, অপর দলের মত তিনি বাঁকুড়া জেলায় ছাতনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ সম্পর্কেও একই মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্মেছিলেন, আবার কারাে মতে তাঁর জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে। চণ্ডীদাস বিবাহিত ছিলেন কিনা সে ব্যাপারেও কারাে পক্ষেই কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। ফলে অনেকেই মনে করেন তাঁর সঙ্গে রামীর প্রণয়ঘটিত যে কাহিনী বহুদিন ধরে জনমুখে রটে আসছে সেই কাহিনীর মধ্যে নিশ্চয় কিছুটা সত্যতা রয়েছে। কাহিনীটা হচ্ছে এইরূপ :–
নানুর থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে তেহাই নামক একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বাস করত এক রজক। সেই রজকের এক মেয়ে ছিল, নাম রামমণি। সেই রামমণিকেই সকলে রামী বলে ডাকত। রামী যখন পূর্ণ যৌবনা তখন হঠাৎ একদিন তিনি নানুরের বাশুলী বা বিশালাক্ষীর মন্দিরে এসে হাজির হলেন। চণ্ডীদাসের কাছে তাঁর আবেদন, ঐ মন্দিরে তাঁকে আশ্রয় দিতে হবে। এই আবেদনে এতটাই জোর ছিল যে, চণ্ডীদাস শেষপর্যন্ত তা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।
কেউ কেউ বলেন যে, রামী মন্দিরে থাকতেন না কিন্তু তিনি নাকি প্রতিদিন কাপড় কাচার জন্য তেহাই থেকে নানুরে আসতেন। তিনি যখন কাপড় কাচতেন তখন চণ্ডীদাস সেই পুকুরের অপর প্রান্তে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। এভাবেই দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হন, একের সঙ্গে অপরের মন বিনিময় ঘটে। সেই প্রেমের অবিসংবাদিত ফলশ্রুতি হিসাবে রামীর উপর শুরু হয়েছিল তার পরিবারের লোকজনদের অত্যাচার, গঞ্জনা। শেষ পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রিয়তমের কাছে। ফলে সেদিন প্রেমিক চণ্ডীদাসের পক্ষেও সম্ভব হয়নি তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া। তিনি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মনের মানসীকে, আশ্রয় দিয়েছিলেন বাশুলী-মন্দিরে। চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে, ব্রাহ্মণসন্তান চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকনন্দিনী রামীর হৃদয়- বিনিময় সমাজকর্তা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী—কারাে পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে চণ্ডীদাসকে যে শুধু বাশুলী-মন্দিরের পুরােহিতের কাজটাই হারাতে হয়েছিল তাই নয়, তিনি সমাজচ্যুত হয়ে একঘরে হতেও বাধ্য হয়েছিলেন। নানুর গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তেহাই গ্রামের প্রান্তবর্তী রামীর কুটিরে। চণ্ডীদাস সহজমার্গে পরকীয়া সাধনের উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁর দীক্ষা হয়েছিল, কে দীক্ষা দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে কারাে কিছু জানা নেই। তাই মনে হয়, সম্ভবত তাঁর রচিত পদাবলীতে বৈষ্ণবধর্মের মাধুর্য এবং প্রভাব বিদ্যমান থাকার কারণেই অনেকে তিনি যে সহজিয়া মতে দীক্ষিত সেই অনুমানটিকেই বাস্তব বলে ধরে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পরম বৈষ্ণব।
চণ্ডীদাসের পদাবলী তৎকালীন বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চৈতন্যদেবও কখনাে কখনাে তাঁর পদকীর্তন করতেন বলে জনশ্রুতি আছে। চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যাপতি তখন জীবিত ছিলেন। যখন তিনি চণ্ডীদাসের পদাবলী রচনার কথা শুনলেন তখন তিনি চণ্ডীদাসকে দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুযােগ মিলে গেল। বিশেষ কার্য উপলক্ষ্যে মহারাজ শিবসিংহ বাংলাদেশের বর্ধমানের মঙ্গলকোটে এসেছিলেন। বিদ্যাপতিও সঙ্গী হলেন মহারাজের। কিন্তু মঙ্গলকোটে তাঁর মন টিকল না। তিনি চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপনের উদ্দেশ্যে রূপনারায়ণ নামক জনৈক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন চণ্ডীদাসের গ্রামের উদ্দেশ্যে। চণ্ডীদাসও লােকমুখে খবর পেলেন বিদ্যাপতির মঙ্গলকোট আগমনের। তিনিও এ সুযােগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তাই মঙ্গলকোটের দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু মঙ্গলকোট পর্যন্ত তাঁকে যেতে হল না, পথিমধ্যে তাঁর সাথে বিদ্যাপতির দেখা হল। প্রবীণ কবি নবীনকে অভ্যর্থনা করলেন। উভয়ের মধ্যে ভাব বিনিময় হল রূপ-অরূপের মধ্যে দিয়ে। একজন রূপের পূজারি অন্যজন বিরহের। তাই উভয়ের মধ্যে যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে। চণ্ডীদাস ছিলেন পরকীয়া প্রেমের পূজারি। তাই পরকীয়া সাধকের নিগুঢ় তত্ত্ব চণ্ডীদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের যে আসক্তি তা অপার্থিব প্রেম। তাতে কোন জৈবিক লিপ্সা নেই—তাতে আছে উভয়ের উভয়কে নিবিড় করে পাওয়ার চেষ্টামাত্র। সে প্রেম নিকষিত হেম বা অনন্ত প্রেম। কিন্তু সমাজ-সংসার তাই কি মেনে নেবে ! তাদের কাজ জটিলা কুটিলার মত, পরছিদ্রান্বেষণ করা। কিন্তু যিনি মহৎ তাঁর বাক্য এবং কার্য এক। তাঁরা সমাজ-সংসারে বাস করেও সামাজিক নিয়মকে উপেক্ষা করে এক আনন্দময়লােকে বিরাজ করেন। তাই তাঁরা অনন্ত প্রেমের অধিকারী, কালজয়ী পুরুষ। রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের যে প্রেম তা দেশ-কালের গণ্ডীর অতীত। চণ্ডীদাসের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত না আসলে তিনি রাধার বিরহ-বিধুর বেদনা কি তা অনুভব করতে পারতেন না। চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্বাভাস চণ্ডীদাসের কবিতায় পাওয়া যায় :–
‘অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ।৷
পায়ে ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়।
সােনার পুতুলি যেন ধূলায় লুটায়।৷’
পদকর্তা বা মহাজন চণ্ডীদাস দেখেননি—শুধু সেই প্রেমিক পুরুষের পদধ্বনি শুনেছিলেন, সেইজন্য লিখলেন– “সােনার পুতলি যেন ধূলায় লুটায়।” গৌরলীলার পূর্বাভাস চণ্ডীদাস মানসদৃষ্টিতে অবলােকন করেছিলেন। এই একই কথা গৌরপ্রেমিক বৈষ্ণবগণ বলেন, “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে গােরা ধূলাতে লুটালাে গো।”
চণ্ডীদাসের শেষজীবন সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। একদল বলেন বৃন্দাবনে বাসকালে তিনি স্বাভাবিকভাবেই লীলা সংবরণ করেন। আজো বৃন্দাবনের পাণ্ডারা কেশীঘাটে একটি সমাধি দেখিয়ে বলেন সেটিই নাকি চণ্ডীদাসের সমাধি। আর একদলের মত কবি একদিন নানুরের নিকটবর্তী কীর্ণাহার নামক গ্রামে রজকিনী রামীকে সঙ্গে নিয়ে একটি নাটমন্দিরে কীর্তন করছিলেন, হঠাৎ মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়ায় রামীর সঙ্গে কবিও সমাহিত হন। সুতরাং এই অসামান্য প্রতিভাবান কবির মৃত্যুরহস্য চিরকালের জন্য অন্ধকারের আড়ালেই থেকে গেছে।
চণ্ডীদাসের জীবন ও জীবনী থেকে সমাজ কি পেল, শুধুই কি এক গুচ্ছ পদাবলী ? না তা নয়। রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেম, অপার্থিব প্রেম কাহিনী-আকারে ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয়কন্দরে স্থান করেছে। কোন কবি বলেছিলেন, ‘কানু বিনা গীত নাই’। চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে রামী-চণ্ডীদাস যেন সেই পরকীয়া প্রেমের মূর্তপ্রকাশ। যেখানে বলা হয়েছে—“রজকিনীর প্রেম নিকষিত হেম—কামগন্ধ নাহি তায়।” মানুষ তাে বহু কথাই বলতে পারে—সমালােচকগণ সমালােচনাও করতে পারে, কিন্তু সত্য চিরন্তন। সমালােচক কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যায় কিন্তু মহাজনগণ ঠিকই কালের বুকে স্থান করে নেন। চণ্ডীদাস প্রকৃত অর্থেই চরম ত্যাগী ও মহাযােগী ছিলেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের অন্তরসত্তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি রাধাকে বিলাসময়ীরূপে কল্পনা না করে কৃষ্ণবিরহে যােগিনীরূপে দেখেছেন। ‘জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো’….. ‘বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমতি যােগিনীপারা।’ আবার কৃষ্ণ তদ্গতপ্রাণ রাধার বর্ণনা দিয়েছেন, “ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।” আত্মসমর্পণের ভাব বর্ণনা করেছেন, “কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল তুলসী দিয়া”, অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, “দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।” এত ভালবাসা, এত সমর্পণ তবু ভয়—“এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে। না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন ছুটে।” জীবন-দর্শন শুনিয়েছেন, “সুখ দুঃখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুঃখ যায় তার ঠাঁই।”
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “মুলো খেলে মুলাের ঢেকুর ওঠে”। মানুষ যা করে, তাই বলে। মহাকবি রসিকশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস মাতৃসাধক হয়েও বাউলস্বভাৰ ছিলেন। তাই তিনি শ্যামা ও শ্যামকে একই আসনে বসাতে পেরেছেন। বাশুলীর পুজো করছেন আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী রচনা করেছেন। এই বৈপরীত্য সাধন মহাসাধক ছাড়া কি সম্ভব ! গুরুমহারাজ স্বামী পরমানন্দ বলেছিলেন– বাউল-সাধন বা সহজিয়া সাধনার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন চন্ডীদাস। তাই আজও সহজিয়া মরমিয়া বাউল গান গেয়ে ফেরে, “আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।” ধন্য রাঢ়বাংলার মাটি, ধন্য নান্নুর গ্রাম, যেখানে ভগবৎশক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল মাত্র কয়েকশত বছর আগে। বীরভূমের সেই রাঙামাটিকে আমাদের শতসহস্র প্রণাম, প্রণাম ভক্তজনেদের যাঁরা এই রস-সাধকের সাধনার ধারাকে আজও ধরে রেখেছেন।