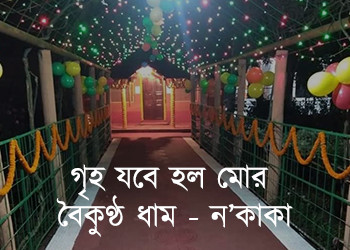‘‘মাধব বহুত মিনতি করি তােয়।
দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছােড়বি মােয়।৷
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ।৷”
জিজ্ঞাসা— আচ্ছা মহাশয়, বিদ্যাপতির পরমেশ্বরের কাছে এই যে সকাতর প্রার্থনা তাঁর কৃপাপ্রাপ্তির জন্য, এই প্রার্থনা কি দীনবন্ধু পূর্ণ করেছিলেন? এই বিদ্যাপতির বিশেষ পরিচয় কি ?
উত্তর— যে বিদ্যাপতির কথা বলছো ইনি একজন, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিক প্রাচীন মৈথিলী কবি, ভক্ত এবং সুপণ্ডিত। তাঁর জন্মস্থান ও জন্মকাল সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। তবে অনুমান করা হয় ১৩৭৪ খ্রীঃ অব্দে মিথিলার অন্তর্গত সীমামারী মহকুমার অধীন বিফসী নামক গ্রামে এক বিদ্বান সন্ত্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁর জন্ম হয়।
বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি হলেও তাঁকে বাঙ্গালী বলা যেতে পারে। কারণ তৎকালীন বল্লাল সেন বাংলাকে যে ৫ ভাগে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে মিথিলা একটি। লক্ষ্মণ সেন প্রতিষ্ঠিত অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে চালু ছিল, অবশ্য বর্তমানেও অব্দ চালু আছে। সে দিক থেকে সেই দেশের অধিবাসিগণকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় হবে না। তাছাড়া বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালীর হৃদয়ের মত ছিল প্রসারিত এবং সার্বজনীন। তিনি যে রসের রসিক সে রস তিনি বাঙ্গালী কবি জয়দেবের নিকট থেকে পেয়েছিলেন এবং সেই রস চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তগণের সময়ে মূর্তিমান হয়ে বাঙলাকে প্লাবিত করেছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী আজও সাদরে বঙ্গ রসিক সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে।
বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান ও যশস্বী ছিলেন। পিতা গণপতি ঠাকুর মিথিলার রাজা গণেশ্বরের পরম বন্ধু ছিলেন। পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ধার্মিক ছিলেন। এই কারণে তিনি যােগীশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যের গুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হতে বিশেষ বৃত্তিলাভ করেছিলেন। এই বীরেশ্বর প্রণীত “বীরেশ্বর পদ্ধতি” অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁদের দশকৰ্ম্ম করে থাকেন। এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির ঊর্ধ্বতন ৬ষ্ঠ পুরুষ ধৰ্ম্মাদিত্য হতে সকলেই মিথিলারাজের রাজমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিদ্যাপতির রচনাকাল ১৪০০-১৪২৫/৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনি কীৰ্ত্তিলতা, পুরুষ পরীক্ষা, লিখনাবলী, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, গয়াপত্তন, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী ও কীর্তিপতাকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সংস্কৃতগ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁর হিন্দিতে রচিত কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর রচিত বিশেষ বৈষ্ণব পদাবলী এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপি পুঁথি আকারে পাওয়া গেছে। বিদ্যাপতি মহাপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন। ছােটবেলায় তিনি হরিমিশ্রের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাপন যখন হ’ল তখন রাজা ছিলেন গণেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র কীৰ্ত্তিসিংহ। কীৰ্ত্তিসিংহ সিংহাসনে বসেই বিদ্যাপতিকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। সেই সময় কীৰ্ত্তিসিংহের সঙ্গে তার খুল্লপিতামহ ভবসিংহের রাজ্যলাভ বিষয়ে কিছু গােলযােগ হয়েছিল। বিদ্যাপতি এই ঘটনা উপলক্ষ্যে “কীৰ্ত্তিলতা” নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতি দীর্ঘায়ু ছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘজীবনকালে তিনি অনেকগুলি রাজার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কীর্ত্তিসিংহ ছাড়াও ভবসিংহ, দেবসিংহ এবং শিবসিংহের নাম উল্লেখযােগ্য। শিবসিংহ বয়সে সামান্য বড় হলেও তিনি ছিলেন কবি বিদ্যাপতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিবসিংহ রাজা হয়েই দিল্লীশ্বরের রাজস্ব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দিল্লীশ্বর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে পরাজিত করেন ও বন্দী করে দিল্লী নিয়ে চলে যান। এই চরম সংকটের দিনে বিদ্যাপতি রাজার পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি একাকী দিল্লী গমন করে দিল্লীশ্বরের দরবারে স্বরচিত পীযুষবর্ষী সঙ্গীত পরিবেশন করে সম্রাটকে খুশী করেন এবং উপহারস্বরূপ শিবসিংহকে মুক্ত করে নিয়ে যান। এই ঘটনার পর শিবসিংহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং তাঁর কবিত্বের যশও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শিবসিংহ তার স্বগ্রাম বিস্ফী বা বিসপী কবিকে দান করেন। আর সভাকবির রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশেরও ছাড়পত্র মেলে। শিবসিংহ-ঘরণী লছিমাদেবী বা লছমীদেবী ছিলেন অসামান্যা রূপবতী এবং তেজস্বিনী। তিনি যেমন বিদূষী ছিলেন, রাজনীতি বা কুটনীতিও বুঝতেন আবার তেমনি ছিলেন কাব্যরসিকা। কবি বিদ্যাপতির অপূর্ব কাব্যপ্রতিভা রাজমহিষীকে তাঁর প্রতি অনুরক্তা করে তুলেছিল। শিবসিংহ নিজেও ছিলেন কাব্যরসিক। ফলে এই সময় তাদের চাহিদা পূরণের নিমিত্তই কবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী নিয়ে পদাবলী লিখতে শুরু করেন। এমন কথিত আছে যে, রাণী লছমীদেবী স্নানান্তে শৃঙ্গার করে মনােমােহিনী বেশে কবির সামনে স্বর্ণসিংহাসনে এসে বসতেন আর কবির কলম দিয়ে কাব্যরস-স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে আসত। পদ লেখা হলে সেই পদ ছন্দবদ্ধভাবে আবার পঠিত এবং গীত হােত, আর রাণী অবাক বিস্ময়ে কবির দিকে চেয়ে রইতেন। এই সময়কালীন রচনাসমূহই কবি বিদ্যাপতিকে অমর করে রেখেছে। আজও জনমানসে এই পদাবলী সমান আদরণীয়। বিদ্যাপতি রাধার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তাঁর অনুরাগের কথা—‘’হে কৃষ্ণ তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, তা হতেও বেশী, তুমি আমার নিকট পাখীর পাখা, তােমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই। মাছের পক্ষে জল যেমন, তুমি আমার কাছে সেরূপ। জল হতে তুললে সে তখনই মারা যায়। আমি তােমাকে সব দিয়েছি। কিন্তু মাধব ‘তুঁহু কৈছে কহবি মােয়’—আমার সর্বস্ব দিয়েও তােমাকে চিনতে পারিনি। মাধব বল তুমি কে এবং কেমন।” সর্বস্ব দিয়ে শেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা—এ মন্দ কথা নয়। প্রেমিকা এত তপস্যার পর বুঝতে চাইছেন—যাঁকে তিনি আপন মনে করেছিলেন, তিনি পরাৎপর, অবাঙমনসাে গোচরম্। বিদ্যাপতির কাব্যের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি জানা পথ দিয়ে নিয়ে গিয়ে যেন অজানার রাজ্যের সন্ধান দেন। সসীম থেকে অসীমে যাওয়া, রূপকে ধরে অরূপে যাওয়া—এই সাধনাই তাে রস-সাধনা। কবিবর রাণী লছমীকে দেখে নায়িকাশ্রেষ্ঠা রাধাকে কল্পনা করতেন আর কবিত্বশক্তির প্রভাবে তাঁর মুখে কথা বসাতেন। আর লছমীদেবী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবির সামনে বসে তাঁর অপূর্ব কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন, তন্ময় হয়ে যেতেন, তার মধ্যেও ভাবজগতের পরিবর্তনের লহরী খেলত। এইভাবে কাব্যরচনা যত পরিণতির দিকে এগােতে লাগল, উভয়ের রসসাধনাও ততই উৎকর্ষতালাভ করতে লাগল।
বিদ্যাপতিকে কেউ কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবি নামে আখ্যাত করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিবাসরে বিদ্যাপতির গান সর্বদাই গীত হােত। মহাপ্রভু সেই গান শুনতে শুনতে ভাবস্থ হয়ে যেতেন। বিদ্যাপতির ন্যায় প্রতিভার বিস্তৃতি আর কোন বৈষ্ণবকবির নেই। দর্শন, মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, বিরহ, কল্পিত মিলন, প্রার্থনা—সকল ভাবেরই পরাকাষ্ঠা বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রদর্শিত হয়েছে। আবার সংস্কৃত, হিন্দী ছাড়াও কবি মৈথিল ভাষায় কাব্যরচনা করলেন,
“দেসিল বসনা সব জন মিঠটা।
তেঁ তইসন জম্পও অবহঠটা।”
– ‘দেশীকথা সকলের প্রিয়, তাই অবহট কল্পনা করছি।’ মৈথিল ভাষার নামকরণ করলেন অবহঠ। এইভাবে বিদ্যাপতি সংস্কৃত, হিন্দি, মৈথিল বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে যে অপূর্ব কাব্যপ্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন তা সত্যিই অনন্য। তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর বর্ণনা বা প্রকাশভঙ্গি এতটাই নিখুঁত যে, তাঁকে-শ্রেষ্ঠ কবি না বলে উপায় থাকে না। রাধার কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ যখন দৃঢ় অনুরাগে পরিণত হল, তখন কবি বর্ণনা করেছেন–
“সখিহে আজ জাএব মােহী।
ঘর গুরুজন ডর না মানব
বচন চুকব নহী ৷৷”
অর্থাৎ—’হে সখী, আজ আমি কৃষ্ণ দরশনে যাব, ঘরের গুরুজনদের মানব না, প্রতিশ্রুতি ভ্রষ্ট হব না।’ আবার বিরহাকাতরা রাধা যখন স্বপ্নে মাধব দর্শন করে সেই কথা সখীকে বলছেন—
“সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে।৷…
রহলি লজ্জা সুনি সেজ হেরী।”
–সখি, পরম প্রিয় আমার নিকটে এসেছিল সে সময়কার হৃদয়ের উল্লাসের কথা আর কি বলব ? (পরে বলছেন) –ঘুম ভেঙ্গে শূন্য শয্যা দেখে লজ্জিত হয়ে গেলাম। এই ধরণের বিষয়ের গভীরে ঢুকে তার যথাযথ বর্ণনা দেবার শক্তিতেই বিদ্যাপতি মহান নন, তিনি মহান যখন তিনি রাধার তন্ময়তার বর্ণনা করছেন, যা ভেদাভেদজ্ঞান ভাব, অদ্বৈতভাব বা সমাধি অবস্থা।
“অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দর ভেলি মধাই।”
—অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করতে করতে সুন্দরী রাধা স্বয়ং মাধব (তদ্ভাবাপন্ন) হয়ে গেল। এত উচ্চভাবের পদ বা অদ্বৈতভাবের পদ আর কোন বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই। রাধার মুখে তিনি বলেছেন—
‘জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
………………………………………..
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল ৷৷’
রাধা অর্থাৎ ভগবৎ ভক্ত জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমের ভিখারিণী, প্রেম-সাধনার অন্ত নেই, তাই তৃষারও শেষ নেই। ধন্য এই প্রেম, ধন্য এই ধ্যান, ধন্য এই তন্ময়তা! আর ধন্য সেই কবি যিনি নিখুঁত বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন এই সব দিব্যোন্মাদ অবস্থা। যাঁর নিজের তন্ময়তা আসেনি তিনি কি কখনও এই তন্ময়তার রূপ পরিস্ফুট করতে পারেন ! কবি বিদ্যাপতি গ্রন্থশেষে অতি বিনীতভাবে মাধবের বন্দনা করেছেন আর ঘােষণা করেছেন সেই এক ও অদ্বিতীয়-ই সর্বকালে সর্বত্র বিরাজমান, তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত।
“কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তােহে জনমি পুন তােহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা।”
ব্রহ্মাদির যা হতে উৎপত্তি তাতেই লয় হচ্ছে। সাগরের তরঙ্গের ন্যায়। আদি-অন্তহীন কেবল তুমিই। রস-সাধকের এই যে অদ্বৈতভাবনা—এটা সত্যিই বিস্ময়ের। দ্বৈততত্ত্বের মধ্যে দিয়েই যে অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, বিদ্যাপতি উত্তরসূরিদের জন্য সেই সন্ধানই দিয়ে গেলেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।৷