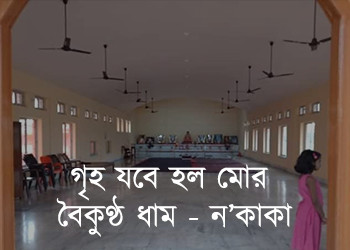" বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলায় সুরধুনীর তীরে তীরে, তাঁর তরঙ্গের সুরে সুরে — উদাত্তকণ্ঠে মধুর নাম গান করতে করতে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতেন উন্মাদের মতো। পরে যখন প্রভুর চিত্ত শান্ত হতো তখন তিনি দেখতেন সেই মনােমােহন কীর্তনের সুরকে অনুসরণ করে ভক্তবৃন্দেরা এসে জড়াে হয়েছে তাঁর চারপাশে। প্রভুর প্রেমে আর নামের মহিমায় তারাও মাতােয়ারা, নৃত্যরত।
গুরুজী মহাপ্রভুকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলোচনা করেছিলেন — সে আলোচনায় মন চলে যেতো নবদ্বীপ-শান্তিপুরের পথে পথে। ভগবান ছাড়া ভগবানের কথা এত মধুর করে আর কে বলতে পারে। একটা বিবেকানন্দই পারে আর একটা বিবেকানন্দকে বুঝতে! সেইসব আলােচনার গভীরে যাওয়া অসম্ভব, তবু তাঁর শ্রীমুখ থেকে তত্ত্ব এবং তথ্য যা শুনেছি এবং মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিভিন্ন মহাজনকৃত গ্রন্থপাঠ করে যা অনুধাবন করেছি সেইসব থেকে কিছু ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিরস পাঠকদের পরিবেশন করার চেষ্টা করছি।
গঙ্গা-বিধৌত এলাকায় প্রেমের প্রবাহ বেশী হয়, স্রোতস্বিনীর স্রোত বা প্রবাহ মানুষের জীবনে গতির সঞ্চার করে। সমাজ-জীবনেও উন্নতির মূলে স্রোতস্বিনীর ভূমিকা প্রধান। তাই প্রেমাবতার মহাপ্রভুর প্রেমের প্রবাহ সুরধুনীর প্রবাহের মতই সতত গতিশীল। মহাপ্রভুর প্রেম জ্ঞানমিশ্রিত। সেই প্রেমের প্রবাহে জ্ঞানী, গুণী, বৈদান্তিক, শাক্ত সকলেই ভেসে যেতাে। কৃষ্ণকীর্তন বা হরিনাম বহু পূর্ব থেকেই ছিল কিন্তু মহাপ্রভু যেন তার পুনর্জাগরণ ঘটালেন। যুগধর্ম হিসাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই কৃষ্ণমন্ত্রের প্রচার ও প্রসার ঘটালেন। মহামায়া বা যােগমায়ার ইচ্ছাতেই সবকিছু ঘটে চলেছে। যুগধর্ম প্রচার, অবতরণ এসবও যোগমায়ার ইচ্ছাতেই ঘটে থাকে। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে নেচে নেচে খােল-করতাল বাজিয়ে হরিনাম করা — এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। কিন্তু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মান্তরীকরণ রোধ করা, সাধারণ মানুষের অভাব, দুঃখ-দুর্দশা দূর করা ও চেতনার উত্তরণ ঘটানােই ছিল যুগধর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীব-জগতের ঐ সমস্যা দূর করার জন্য প্রেমের ভাব নিয়ে চৈতন্যগোঁসাইরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন। প্রচার করলেন মহামন্ত্র “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে”।৷ কৃষ্ণ কে? –না যিনি সর্বময় কর্তা,–সর্বজীবের চিত্তকে কর্ষণ করছেন বা আকর্ষণ করছেন তিনিই কৃষ্ণ। আর রাম কে–না যিনি জীব-জগৎকে রমণ করে চলেছেন অর্থাৎ এই সমস্ত রূপ-রসাদির আস্বাদ গ্রহণ করে চলেছেন, তিনিই রাম। তত্ত্বগতভাবে রাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নেই– পার্থক্য নেই, স্থূলেই ভেদ, তাই বলা হয়–
‘যেই রাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি
সকল ভক্তের মাঝে আছেন শ্রীহরি।’
কলিযুগে রাম ও কৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব বােঝাতে রামকৃষ্ণ রূপে ভগবান এইতো ক’দিন আগে লীলা করে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেন নামাবতার। তিনি বললেন কলিহত জীবকে উদ্ধারের জন্য একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু দুইবাহু তুলে নৃত্য করতে করতে বলতেন একই শ্লোক
‘ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।’
কলিকালে অন্য গতি নেই — হরিনামই একমাত্র সাধন। হরিনাম পরমপাবন, অশুচিকে শুচি করে, অতীর্থকে তীর্থ করে। হেলায় অশ্রদ্ধায় এমনকি নিজের অজ্ঞাতে বাক্যপূরণেও ফললাভ হয়। শুধু নামে নয়, নামাভ্যাসেও কাজ হয়। রত্ন যেখানেই রাখা হোক সিন্দুকে বা ছাইগাদায় তার মূল্য সমান। তারকব্রহ্ম নামের প্রতিটি শব্দ অপ্রাকৃত চিন্ময়, তাই নাম বা নামাভ্যাসের প্রচণ্ড শক্তি। শুকরের দাঁতে
আহত হয়ে যবন ‘হা-রাম’ ‘হা-রাম’ বলে ডেকেও মুক্তি পেয়েছিল। হারাম অর্থে শুকর, আবার ‘হা–রাম’ অর্থে রামকে কাতর হয়ে ডাকা হচ্ছে। এই নামাভ্যাসেও মুক্তি ঘটে। নামের উচ্চারণ যদি অশুদ্ধ হয় বা অসম্পূর্ণ হয় তাতে কিছু এসে যায় না। সমস্ত প্রারব্ধ-পাপের নাশ হয় এই নামে। নাম-নামী অভেদ, অভিন্ন, তাই নামীর যেমন মহিমা–নামেরও তেমনি মহিমা। তাই ভক্ত বলেছে–
‘ সত্যভামা ব্রত করে নামের মর্ম পেয়েছে
হরিনামের তুল্য কি ধন জগতেতে রয়েছে?’
ভগবানের কথা যেখানে থাকে, তাই ভাগবত। পুরাণে রয়েছে — শৌনক প্রশ্ন করলেন সুত-কে? “যােগ-যােগেশ্বর কৃষ্ণ স্থূল শরীর ছেড়ে যখন নিত্যধামে প্রস্থান করলেন তখন ‘ধর্ম’ কার শরণাপন্ন হল? ” উত্তরে সূত বলেছিলেন,“ কৃষ্ণ স্বধামে প্রস্থান করলে কলিহত ধর্ম-জ্ঞানহীন জীবের উদ্ধারের জন্য সৃষ্টি হ’ল ভাগবত।” মহাপ্রভু সেই ভাগবতই শোনালেন সংসারকে। কখনাে নিজমুখে কখনো ভক্তমুখে। তাই গৌরাঙ্গলীলায় ডুব দিতে পারলেই কৃষ্ণলীলায় উত্তরণ। অনেকে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে শ্রীচৈতন্যই কি শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবৃত্তি? কিন্তু ভগবানের লীলা বােঝার সাধ্য কি মানুষের! তাঁর আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্ব সবই লীলা, সবই ব্যতিক্রম। তিনি কখনাে একঘেয়ে হন না। যুগােপযােগী তাঁর সবকিছু। চাল-চলন, পােশাক-আশাক, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, জীবনচর্চা সবই নিত্যনতুন। ‘ নবরে নব, নিতুই নব।’ মহাপ্রভুর জীবনে দেখা যায়, প্রচণ্ড জ্ঞানীও কিভাবে বিশুদ্ধ প্রেমিকে পরিণত হতে পারে। জ্ঞান-ভক্তির দ্বন্দ্ব মেটাতে এবং ভক্তি ও প্রেমের মহিমা জগতে প্রচার করতেই প্রভু যেন জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি বা প্রেমের প্রতীক এখানে জিজ্ঞাসা আসে — ভগবানের আবার শরীর ধারণের প্রয়ােজন কি? কারণ তাঁর নাম উচ্চারণেই সংসারণ্যে পথভ্রান্ত মানুষ মুক্তিলাভ করে, স্বয়ং যমরূপী ভয় যার ভয়ে ভীত, ত্রিলােকপাবনী সুরধুনী যাঁর চরণ থেকে নির্গত হয়ে সর্বজগৎকে পবিত্র করছে—তাঁর আবার শরীর নিয়ে কষ্ট করতে আসা কেন? তাঁর মজতে আর মজাতে আসা। যুগধর্ম প্রচারটা এই ভাবেই হয়। মহাপ্রভুকে তখন সবাই বলত, ‘ যজানে গোঁসাই ’ কারণ তিনি সকলকে এক রসে মজিয়ে দিয়েছিলেন, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা সর্বদা নাম করা, শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম। শ্রবণ-কীর্তন, ধ্যান, আরাধনায় হরির নাম করাে, হরির সেবা করাে। হরিসেবা থেকেই ধর্মে শ্রদ্ধা এবং নামে ভক্তি জন্মাবে। হরিকথায় যদি ভক্তিই-না জন্মায় তবে ধর্মাচরণ পণ্ডশ্রম মাত্র। ভক্তি, শরণাগতি, সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে কৰ্মাৰ্পণই তাপত্রয় থেকে নিরাময়ের মহৌষধ। নাম কীর্তনই ক্রমানুযায়ী ভক্তি-শরণাগতির পথ প্রশস্ত করে, তাই কলিহত জীবের নামই নিস্তারের একমাত্র পথ।
মহাপ্রভু ভক্তদের বললেন, ‘ নাম ছাড়া গতি নাই। গুরুর আদেশে নিরন্তর নাম নিচ্ছি, নাম নিতে নিতে অন্যবিষয়ে আমার ভ্রান্তি জন্মেছে–লােকে পাগল বলছে। কৃষ্ণনামে নাচি, গাই, হাসি, কঁদি, সমস্ত বাহ্যজ্ঞানসমূহ কৃষ্ণনামে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।’ তখন অদ্বৈতাদি ভক্তগণ বললেন, ‘না না প্রভু, তুমি পাগল হওনি। তুমি কৃষ্ণনামের ফল যে প্রেম, সেই প্রেমলাভ করেছ, আর এটাই পঞ্চম পুরুষার্থ।’
প্রভু যখন কাশীধামে নামপ্রচারে ব্যস্ত তখন কাশীধামে বেদান্ত শিরোমণি প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন সাধু-সমাজের মাথা। তিনি মহাপ্রভু দশনামী সম্প্রদায়ের সাধু হওয়া সত্ত্বেও বেদান্ত আলােচনা না করে নেচে-গেয়ে নামকীর্তন করছেন শুনে মহাপ্রভুর প্রচও নিন্দা করতে শুরু করলেন। প্রভুর নিন্দা শুনে ভক্তদের অন্তরে খুব কষ্ট হতে লাগল। তারা প্রভুকে নিবেদন করলেন, ‘ প্রভু এর একটা ব্যবস্থা করুন।’ প্রভু হেসে বললেন, ‘ কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব ঠিক হবে।’ কিছুদিন পর একদিন এক মহারাষ্ট্র বিপ্রের বাড়ীতে প্রকাশানন্দ সহ যখন কাশীর সাধুসমাজ নিমন্ত্রিত হয়ে সমবেত হয়েছে তখন ভক্তের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রভুও মায়াবাদীদের আসরে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন প্রকাশানন্দ সহ অন্যান্য সন্ন্যাসীরা গর্বোদ্ধত ভঙ্গিমায় বিরাজমান। মহাপ্রভু অত্যন্ত বিনয় সহকারে দূর থেকে সকলকে নমস্কার জানিয়ে পা ধুয়ে সেই নােংরা স্থানেই বসে পড়লেন। মায়াবাদীরা তাঁকে দেখেও কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। প্রভু ওঁদের আকর্ষণ করতে বা কৃপা করতে তেজোময় শরীর ধারণ করলেন। সন্ন্যাসীদের টনক নড়ল। প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি ঐ নােংরা স্থানে বসেছেন কেন?’ প্রভু বললেন, ‘ আপনাদের ঐ সভায় বসার যােগ্য নই আমি।’ প্রকাশানন্দ–’আপনিই কি কেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য? তা আপনি সন্ন্যাসী হয়ে বেদান্তপাঠ ও বেদান্ত চর্চা করেন না কেন?’ প্রভু বিনীতকণ্ঠে বললেন, ‘আমি মূর্খ, তাই আমার গুরু বেদান্তের অনধিকারী ভেবে আমাকে শুধু কৃষ্ণনাম জপ ও কৃষ্ণনাম-গান করতে বলেছেন। আর কৃষ্ণমন্ত্রই তো বেদান্তের সার।’ প্রকাশানন্দ–’তা কি করে সম্ভব?’ মহাপ্রভু – ‘হ্যাঁ, এই মহামন্ত্রেই জ্ঞান, প্রেম সবই সম্ভব। কলিকালে এই নাম ছাড়া গতি নেই। এই নামের যাদুতেই আমি উন্মত্তবৎ নাচি, কাঁদি, হাসি। এজন্য অনেকে অনেক কিছু বললেও গুরুদেব কিন্তু বললেন — আমার মহাপ্রেমের — মহাভাবের উদয় হয়েছে। তাই আমি গুরুবাক্য শিরােধার্য করে এই হরিনাম করি।’ প্রকাশান তখন বলে উঠলেন, ‘ ঠিক আছে, আপনি বেদান্ত না বুঝলেও শুনতে তো দোষ নেই!’ মহাপ্রভু তখন বললেন, ‘বেদান্তসূত্ৰই তাে ঈশ্বরবাক্য, যা নারায়ণ ব্যাসদেবের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাই এটা চর্চায় দোষ নেই। মুখ্য অর্থে সবই ঠিক, গৌণার্থে যত গরমিল। ভক্তিমার্গে সেব্য-সেবকের ভাবই মূল। শঙ্করাচার্যের জীব ও ব্রহ্মের অভেদভাব ধরলে সবই সমান হয়ে যায় — সেখানে ভক্তিভাব থাকে না। অবশ্য শঙ্করাচার্য যুগপ্রয়ােজনে ঈশ্বর ইচ্ছায় মূখ্যার্থ ছেড়ে গৌণার্থ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে যে নিরাকার বলেছেন, তা ব্ৰহ্ম তাে শুধু নিরাকার নন, তিনি সাকার, নিরাকার এবং দুয়ের অতীত। ব্ৰহ্ম সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপ, ‘রসো বৈ সঃ’ — তিনি রসম্বরূপ। আর আচার্যের জীব ও ঈশ্বরের অভেদতত্ত্ব মেনে নিয়েও বলা যায় যে, উভয়ের (জীব ও ব্ৰহ্ম) মধ্যে পরিমাণগত ভেদ আছে, জীব অণুচৈতন্য, ঈশ্বর বিভুচৈতন্য। জীবের ইচ্ছা হলেও তার ব্ৰহ্মাণ্ডসৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই — যা ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। তাই শক্তিভেদ আছে। তাছাড়া শঙ্করাচার্য বেদের মুখ্য মহাবাক্য ‘প্রণব’কে বাদ দিয়ে ‘তত্ত্বমসি’কেই মহাবাক্য বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। প্রণবই ওঙ্কার, এর সঞ্চালনেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপে জগৎ-সংসার ত্রিগুণের প্রবাহ দ্বারা আবর্তিত হচ্ছে। প্রণবই সমস্ত কিছু ব্যাপ্ত হয়ে আছে।’
প্রকাশানন্দের ভুল ভাঙল ভাঙল।। জ্ঞান ও প্রেমের মূর্তপ্রকাশ মহাপ্রভুকে নিন্দা করার জন্য ক্ষমা চাইলেন। মহাপ্রভু তখন তাদের কৃষ্ণনাম করতে বললেন। এই সময় একদিন মহাপ্রভু বিন্দুমাধব মন্দিরে গিয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে উদ্দামভাবে প্রেমােন্মত্ত হয়ে নাচতে-গাইতে লাগলেন। চতুর্দিক হতে হাজার হাজার লােক ঐ ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে কীর্তনে যােগ দিল। মন্দির হতে কাছেই প্রকাশানন্দের আশ্রম। তারাও ঐ নামধ্বনি শুনে — তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণে ছুটে এলেন মন্দিরে। মহাপ্রভুর ঐ রূপ ও মহাভাব দেখে আত্মহারা হয়ে গেলেন প্রকাশানন্দসহ সকল সন্ন্যাসী। প্রকাশানন্দের দেহে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হল, তিনি অভিমানমুক্ত হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন — শেষে নৃত্য শুরু করলেন। শুষ্ক বেদান্তীর পরিবর্তন দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। সত্যই আজ তিনি প্রকাশানন্দ ! ভগবানের কৃপায় তাঁর জীবন সার্থক হল।