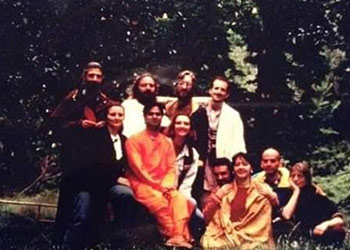গুরুমহারাজ স্বামী পরমানন্দ অঙ্গুলীমাল সম্বন্ধে বলেছিলেন – সে বিশাল চেহারার মানুষ ছিল ৷ জঙ্গল থেকে সেই বিশেষ দিনটির ভোরবেলায়, ভগবান বুদ্ধের পিছন পিছন যখন সে নতমস্তকে হেঁটে আসছিল , তখন ভগবান বুদ্ধের থেকেও তার উচ্চতা বেশি হওয়ায়_ওখানে উপস্থিত সবাই তাকে দুর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল । চীবর পরিহিত – মুণ্ডিত-মস্তক – সে যুগের ত্রাস অঙ্গুলিমালকে দেখার জন্য সেই সময় ওই স্থানে (কোশল রাজ্যের সীমানায়) বহু মানুষের সমাবেশ হয়েছিল ৷ উভয় রাজ্যের রাজারাই (ওই জঙ্গলের দুই প্রান্তের দুটি রাজ্য) বুদ্ধের শিষ্য ছিল _তাই বোধহয় অঙ্গুলিমালের আলাদা করে বিশেষ কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি , ফলে সে বাকি জীবনটা একজন বৌদ্ধ শ্রমণ হিসাবেই কাটিয়ে দিয়েছিল ।
এইসব ২৫০০ বছর আগের ইতিহাস নিশ্চয়ই বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, পরবর্তী কালের বহু লেখকও এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করেছে – কিন্তু আমরা সেই সব ঘটনায় যেতে চাই না । আমরা স্বামী পরমানন্দের মুখে যেমনটি শুনেছিলাম – সবসময় সেইরকমটাই বলার চেষ্টা করা হয় এবং এখানেও তাই করা হয়েেছে । এই ব্যাপারে গুরুমহারাজ স্বামী পরমানন্দ আমাকে একবার Licence -ও দিয়েছিলেন । আচার্য শঙ্কর, কবি জয়দেব, সিরিডির সাঁইবাবা বা এই ধরনের অনেক মহাপুরুষের জীবনের নানা কথা যখন গুরু মহারাজ বলতেন – তখন আমরা দেখতাম যে, ‘ভারতের সাধক’ বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে সেইসব মহাপুরুষদের জীবনী থেকে আমরা যা তথ্য পেয়েছি – তার থেকে ওনার বক্তব্য অনেকাংশেই আলাদা ! সেই নিয়ে আমি একদিন ওনাকে বললাম – ” গুরুজী ! এই ধরনের মহাপুরুষদের নিয়ে তো অনেক গ্রন্থ রয়েছে , এমনকি এদের নিয়ে সিনেমা বা টিভি সিরিয়াল ও হয়েছে, ফলে বহু মানুষ – বহুদিন ধরে ওইসব গ্রন্থে লিখে রাখা ঘটনাকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছে ! কিন্তু আপনি যখন ওই সমস্ত মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন – তখন কিন্তু সেই সব ঘটনা থেকে, অনেক কিছুই আলাদা বলেন – আমরা লেখার সময় আপনি যেটা বলছেন – সেটাই তো লিখবো !”
গুরু মহারাজ তাৎক্ষণিক এবং সাবলীলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন – “আমি যেটা বলছি – তোরা সেটাই লিখবি ৷ কোথায় কি লেখা রয়েছে – তা তোদের খোঁজার প্রয়োজন নাই ৷ বলবি “স্বামী পরমানন্দ”- এটা বলেছেন, ব্যস ! তাহলেই হবে ৷”
সুতরাং আমাদের কোন চিন্তা নাই – কোথায় কি লেখা রয়েছে, কে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে, তাতে আমাদের কি প্রয়োজন !
আমার মনে আছে আরো একটা ঘটনার কথা – সেটাও এই প্রসঙ্গে বলি । গুরু মহারাজ, ন’কাকাকে নিয়ে একবার জয়দেব-কেন্দুলি গিয়েছিলেন ! সেখানে রাত্রি কাটানোর জন্য ওনারা ছোটখাটো কোন একটা আশ্রমের একই ঘরে শুয়েছিলেন । ন’কাকার মুখে শুনেছিলাম – সেই রাত্রে গুরুমহারাজ প্রায় সারারাত ঘরের বাইরে কার সাথে যেন গল্প করছিলেন । পরদিন সকালে যখন ন’কাকা গুরুমহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – ” ঠাকুর ! কাল সারারাত তো বিছানায় গা-টাও গড়ালে না ! তা – কার সাথে সারারাত বকবকৃ করছিলে ?” গুরুমহারাজ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন – ” জানো ন’কাকা ! কাল রাত্রে বালকের বেশে ‘কবি জয়দেব’ এসেছিল । ও – ওর জীবনের নানা কথা বলছিল ৷ ও এটাও বলছিল যে, পরবর্তী কালের মানুষ ওকে নিয়ে যেসব বই লিখেছে – সেগুলিতে ওনার সম্বন্ধে সব উল্টোপাল্টা কথা লেখা আছে – বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নাই !”
এই ঘটনাটা আমরা সিটিং-এ গুরু মহারাজের কাছেও শুনেছিলাম | সুতরাং সত্যটা কি – তা তো আমাদের কাছে একেবারে পরিষ্কার ! তাই ওসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো না – বরং আমরা আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ফিরে আসি । আগে একদিন বলা হয়েছিল যে, একজন খুব উঁচুদরের বৌদ্ধ শ্রমণের সাথে একবার গুরুমহারাজের অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়েছিল । ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার-শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি দেশের বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারের দায়িত্বে ছিলেন এই শ্রমন (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী)! বিভিন্ন আলোচনার সময় ভগবান বুদ্ধের “আত্মদীপো ভবঃ”- কথাটির ব্যাখ্যা করেছিলেন ওই সন্ন্যাসী । উনি বলেছিলেন – “আত্মদীপো ভবঃ”- কথাটির অর্থ “আত্মা দীপ স্বরূপ”– অর্থাৎ উনি আত্মাকে জ্বলন্ত প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করে (ভগবান বুদ্ধের-ই কথার ব্যাখ্যা) বলতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ যখন কোন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখে, তখন যে শিখাটাকে সে দেখছে – সেটি কিন্তু যে তেলটা পুড়ে গেছে তার শিখা ! প্রতিমুহূর্তে তেল পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন শিখা তৈরি হচ্ছে – শিখাটি যে মুহূর্তে ওই প্রদীপে তৈরি হচ্ছে – সেটা আমাদের চোখে আসতে যেটুকু সময় লাগছে – তাতেই ‘ওই আগের মুহুর্তে’-র শিখাটি অতীত হয়ে যাচ্ছে ! ফলে আমাদের চোখ একটা স্থির নিস্পন্দ দীপশিখা বলে মনে করছে বটে – কিন্তু সেটা প্রতি মুহূর্তে বদলে বদলে যাওয়া দীপশিখার একটি ক্রমাগত পরিণাম ৷ যেটা দেখছি – সেটা অতীতের ফল এবং যা প্রতিনিয়ত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চলে যাচ্ছে ! অর্থাৎ উনি বলতে চেয়েছিলেন – ‘বর্তমান’ ব্যাপারটাই মুল্যইীন | এই ব্যাখ্যায় ‘বর্তমানের’ বিশেষ কোনো ভূমিকাই নাই, যেহেতু তার স্থায়িত্বকাল অত্যল্প ।কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে বর্ত্তমান কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে |
গুরুমহারাজ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন – “একসময় বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ উপরোক্ত যুক্তিজালে বহু বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীদেরকে তর্কে পরাস্ত করেছিল এবং হয় তাদেরকে তুষানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে বাধ্য করেছিল অথবা তাদেরকে বৌদ্ধ ধর্ম মতে নিয়ে এসেছিল ।”
যাইহোক, সেইদিনকার কথায় আসি | ওই বৌদ্ধ শ্রমনের সব কথা শোনার পর গুরুমহারাজ ওনাকে শুধু বলেছিলেন – “আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন, সেগুলি সবই মেনে নিলাম – সত্যি সত্যিই জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা মুহূর্তে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে ৷ কিন্তু ওটা বর্তমান হোক, অতীতের ফল হোক বা অনাগত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রাই করুক–ওটিকে দেখছে কে? কঃ দ্রষ্টা? ওটি যে দীপশিখা-ই সেটা জানছে কে? কঃ জ্ঞাতা? এর অনুভবকারী কে? কঃ বিজ্ঞাতা ? যে বা যিনি এটা দেখছেন এটা জানছেন এটাকে সিদ্ধান্ত করছেন – তিনিই ‘আমি’! সোহহম ৷ সেই ‘আমি’ – যিনি সদা সর্বদা ‘নিত্য বর্তমানে’ রয়েছেন এবং এগুলিকে দেখছেন – বুঝছেন বা জানছেন – তিনিই ‘আমি রুপী আত্মা’ । এটাই উপনিষদের আত্মতত্ব | এই ভাবেই গুরু মহারাজ বৌদ্ধ তত্ত্বের সাথে উপনিষদের তত্ত্বকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন ৷৷ [ক্রমশঃ]
এইসব ২৫০০ বছর আগের ইতিহাস নিশ্চয়ই বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, পরবর্তী কালের বহু লেখকও এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করেছে – কিন্তু আমরা সেই সব ঘটনায় যেতে চাই না । আমরা স্বামী পরমানন্দের মুখে যেমনটি শুনেছিলাম – সবসময় সেইরকমটাই বলার চেষ্টা করা হয় এবং এখানেও তাই করা হয়েেছে । এই ব্যাপারে গুরুমহারাজ স্বামী পরমানন্দ আমাকে একবার Licence -ও দিয়েছিলেন । আচার্য শঙ্কর, কবি জয়দেব, সিরিডির সাঁইবাবা বা এই ধরনের অনেক মহাপুরুষের জীবনের নানা কথা যখন গুরু মহারাজ বলতেন – তখন আমরা দেখতাম যে, ‘ভারতের সাধক’ বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে সেইসব মহাপুরুষদের জীবনী থেকে আমরা যা তথ্য পেয়েছি – তার থেকে ওনার বক্তব্য অনেকাংশেই আলাদা ! সেই নিয়ে আমি একদিন ওনাকে বললাম – ” গুরুজী ! এই ধরনের মহাপুরুষদের নিয়ে তো অনেক গ্রন্থ রয়েছে , এমনকি এদের নিয়ে সিনেমা বা টিভি সিরিয়াল ও হয়েছে, ফলে বহু মানুষ – বহুদিন ধরে ওইসব গ্রন্থে লিখে রাখা ঘটনাকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছে ! কিন্তু আপনি যখন ওই সমস্ত মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন – তখন কিন্তু সেই সব ঘটনা থেকে, অনেক কিছুই আলাদা বলেন – আমরা লেখার সময় আপনি যেটা বলছেন – সেটাই তো লিখবো !”
গুরু মহারাজ তাৎক্ষণিক এবং সাবলীলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন – “আমি যেটা বলছি – তোরা সেটাই লিখবি ৷ কোথায় কি লেখা রয়েছে – তা তোদের খোঁজার প্রয়োজন নাই ৷ বলবি “স্বামী পরমানন্দ”- এটা বলেছেন, ব্যস ! তাহলেই হবে ৷”
সুতরাং আমাদের কোন চিন্তা নাই – কোথায় কি লেখা রয়েছে, কে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে, তাতে আমাদের কি প্রয়োজন !
আমার মনে আছে আরো একটা ঘটনার কথা – সেটাও এই প্রসঙ্গে বলি । গুরু মহারাজ, ন’কাকাকে নিয়ে একবার জয়দেব-কেন্দুলি গিয়েছিলেন ! সেখানে রাত্রি কাটানোর জন্য ওনারা ছোটখাটো কোন একটা আশ্রমের একই ঘরে শুয়েছিলেন । ন’কাকার মুখে শুনেছিলাম – সেই রাত্রে গুরুমহারাজ প্রায় সারারাত ঘরের বাইরে কার সাথে যেন গল্প করছিলেন । পরদিন সকালে যখন ন’কাকা গুরুমহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – ” ঠাকুর ! কাল সারারাত তো বিছানায় গা-টাও গড়ালে না ! তা – কার সাথে সারারাত বকবকৃ করছিলে ?” গুরুমহারাজ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন – ” জানো ন’কাকা ! কাল রাত্রে বালকের বেশে ‘কবি জয়দেব’ এসেছিল । ও – ওর জীবনের নানা কথা বলছিল ৷ ও এটাও বলছিল যে, পরবর্তী কালের মানুষ ওকে নিয়ে যেসব বই লিখেছে – সেগুলিতে ওনার সম্বন্ধে সব উল্টোপাল্টা কথা লেখা আছে – বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নাই !”
এই ঘটনাটা আমরা সিটিং-এ গুরু মহারাজের কাছেও শুনেছিলাম | সুতরাং সত্যটা কি – তা তো আমাদের কাছে একেবারে পরিষ্কার ! তাই ওসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো না – বরং আমরা আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ফিরে আসি । আগে একদিন বলা হয়েছিল যে, একজন খুব উঁচুদরের বৌদ্ধ শ্রমণের সাথে একবার গুরুমহারাজের অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়েছিল । ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার-শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি দেশের বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারের দায়িত্বে ছিলেন এই শ্রমন (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী)! বিভিন্ন আলোচনার সময় ভগবান বুদ্ধের “আত্মদীপো ভবঃ”- কথাটির ব্যাখ্যা করেছিলেন ওই সন্ন্যাসী । উনি বলেছিলেন – “আত্মদীপো ভবঃ”- কথাটির অর্থ “আত্মা দীপ স্বরূপ”– অর্থাৎ উনি আত্মাকে জ্বলন্ত প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করে (ভগবান বুদ্ধের-ই কথার ব্যাখ্যা) বলতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ যখন কোন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখে, তখন যে শিখাটাকে সে দেখছে – সেটি কিন্তু যে তেলটা পুড়ে গেছে তার শিখা ! প্রতিমুহূর্তে তেল পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন শিখা তৈরি হচ্ছে – শিখাটি যে মুহূর্তে ওই প্রদীপে তৈরি হচ্ছে – সেটা আমাদের চোখে আসতে যেটুকু সময় লাগছে – তাতেই ‘ওই আগের মুহুর্তে’-র শিখাটি অতীত হয়ে যাচ্ছে ! ফলে আমাদের চোখ একটা স্থির নিস্পন্দ দীপশিখা বলে মনে করছে বটে – কিন্তু সেটা প্রতি মুহূর্তে বদলে বদলে যাওয়া দীপশিখার একটি ক্রমাগত পরিণাম ৷ যেটা দেখছি – সেটা অতীতের ফল এবং যা প্রতিনিয়ত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চলে যাচ্ছে ! অর্থাৎ উনি বলতে চেয়েছিলেন – ‘বর্তমান’ ব্যাপারটাই মুল্যইীন | এই ব্যাখ্যায় ‘বর্তমানের’ বিশেষ কোনো ভূমিকাই নাই, যেহেতু তার স্থায়িত্বকাল অত্যল্প ।কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে বর্ত্তমান কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে |
গুরুমহারাজ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন – “একসময় বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ উপরোক্ত যুক্তিজালে বহু বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীদেরকে তর্কে পরাস্ত করেছিল এবং হয় তাদেরকে তুষানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে বাধ্য করেছিল অথবা তাদেরকে বৌদ্ধ ধর্ম মতে নিয়ে এসেছিল ।”
যাইহোক, সেইদিনকার কথায় আসি | ওই বৌদ্ধ শ্রমনের সব কথা শোনার পর গুরুমহারাজ ওনাকে শুধু বলেছিলেন – “আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন, সেগুলি সবই মেনে নিলাম – সত্যি সত্যিই জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা মুহূর্তে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে ৷ কিন্তু ওটা বর্তমান হোক, অতীতের ফল হোক বা অনাগত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রাই করুক–ওটিকে দেখছে কে? কঃ দ্রষ্টা? ওটি যে দীপশিখা-ই সেটা জানছে কে? কঃ জ্ঞাতা? এর অনুভবকারী কে? কঃ বিজ্ঞাতা ? যে বা যিনি এটা দেখছেন এটা জানছেন এটাকে সিদ্ধান্ত করছেন – তিনিই ‘আমি’! সোহহম ৷ সেই ‘আমি’ – যিনি সদা সর্বদা ‘নিত্য বর্তমানে’ রয়েছেন এবং এগুলিকে দেখছেন – বুঝছেন বা জানছেন – তিনিই ‘আমি রুপী আত্মা’ । এটাই উপনিষদের আত্মতত্ব | এই ভাবেই গুরু মহারাজ বৌদ্ধ তত্ত্বের সাথে উপনিষদের তত্ত্বকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন ৷৷ [ক্রমশঃ]