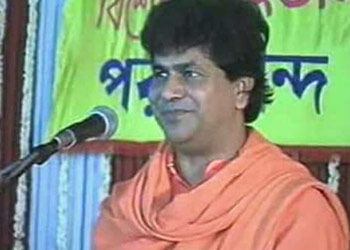স্থান ~ বনগ্রাম পরমানন্দ মিশন । সময় ~ ১৯৮৬, জুলাই ৷ উপস্থিত ব্যক্তিগণ ~ পূর্ণানন্দ মহারাজ, পঙ্কজবাবু, স্বরূপানন্দ মহারাজ, উমাপদ, তপন ইত্যাদি কতিপয় ভক্তজন ৷
জিজ্ঞাসা :– ভগবান বুদ্ধ তাে বেদ-বিরােধী ছিলেন না, তবু বৌদ্ধরা বেদ-বিরােধী হল কেন?
গুরুমহারাজ :– ঠিকই বলেছ, ভগবান বুদ্ধ বেদ বা বেদান্ত-বিরােধী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের কেউই কোন কিছুর বিরােধী নন, কারণ সেখানে কোন ব্যক্তি ইচ্ছার স্থানই নেই–universal will বা universal mind-এর ক্রিয়া হয় । ভেদবুদ্ধি সাধারণ মানবই করে থাকে! এইভাবেই প্রত্যেকটি মহামানবকে, ‘মহামানব’ হিসাবে Represent করতে না পেরে মানবের দল সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে এবং প্রয়ােজনে অমানবিক হয়ে উঠতেও তাদের লজ্জাবােধ করে নি।
বৌদ্ধরা বলেন–ভগবান বুদ্ধ জন্মান্তর স্বীকার করেছেন কিন্তু আত্মাকে স্বীকার করেননি, এটাই বেদ-বিরােধিতার মূলসূত্র। কারণ বৈদিক সিদ্ধান্ত —“অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম” । আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ শরীর ধারণ করেছিলেন। যুগপুরুষগণ যুগের প্রয়োজনে আসেন তাই তৎকালীন মানুষের মানসিকতা অনুযায়ীই মহাপুরুষের শিক্ষাদান হয়ে থাকে ! কারণ এর মাধ্যমেই যুগধর্ম প্রতিষ্ঠা হয়। হয়েছিল কি, একবার ভগবান বুদ্ধের কাছে আনন্দাদি শিষ্যের দল যখন ‘আত্মা’ বা ব্রহ্ম আছে কি নেই—এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ভগবান বুদ্ধ নীরব ছিলেন। ভগবান বুদ্ধের যে ছবি পাওয়া যায় (শিল্পীর আঁকা বা মূর্তি), তাতেই বােঝা যায় বুদ্ধ প্রায়শই শান্ত সমাহিত থাকতেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল থেকে যেন করুণার ধারা ঝরে পড়তাে। সে যাইহােক, ভগবান সেদিন শিষ্যদের কথার উত্তরে হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে শান্ত থেকেছিলেন। ‘মৌন সম্মতির লক্ষণ’–মনে করে শিষ্যরা ধরে নিলেন যে “আত্মা’ নেই। এর ফলে বুদ্ধ পরবর্তীকালে যত গ্রন্থ লেখা হােল তাতে এবং বিভিন্ন ‘ভিক্ষু’ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী )-রাও প্রচারের সময় ‘আত্মা নেই বলে প্রচার করতে লাগলেন। এইভাবেই ভগবান বুদ্ধ পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের কাছে ‘গয়াসুর’ রূপে অথবা বেদ-বিরােধী রূপে পরিগণিত হয়ে গেলেন। এইসব ইতিহাস।
জিজ্ঞাসু :— বুদ্ধ পরবর্তীযুগে অনেক হিন্দু-সাধু-সন্ন্যাসী, বৌদ্ধদের অত্যাচারে মারা যান,এরূপ শােনা যায় কেন ?
গুরুমহারাজ :– অত্যাচার মানে তরবারির আঘাত মনে কোর না। সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক ভারতবর্ষ, ফলে এখান থেকে যে কোন ধর্মশিক্ষাই ছড়িয়ে পড়ুক, তাতে মূল কয়েকটি সূত্র ঠিক থাকে। এর একটি হোল অপর ধর্মমতকে বা ধর্মাবলম্বীকে বলপ্রয়ােগে স্বমতে না এনে বা স্বমতে আনার চেষ্টা না করে_ যুক্তির দ্বারা এবং আলােচনার মাধ্যমে তাকে স্বমতে আনা হোত—“কৃণ্বন্তো বিশ্বমাৰ্যম্” । তাছাড়া ভগবান বুদ্ধেরঅন্যতম শিক্ষাই ছিল ‘অহিংসা’। তবুও ‘তুমি যেমনটা বললে’_ এ ধরণের ঘটনা ঘটেছিল এবং বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বহু তথাকথিত হিন্দু সাধুরা মারা গিয়েছিলেন! এর কারণ, অনাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই এই বিপত্তি । আচাৰ্য্য শংকর আসার পূর্বে ভারতবর্ষে ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল আদি দর্শনসমূহ সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু ‘মীমাংসা’ তখনও আসেনি, যেটা আচাৰ্য্য ‘শারীরক মীমাংসাসূত্রে’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
ইতিমধ্যে কণাদের-‘কণা’বিজ্ঞান (বর্তমানের Particle Physics এর মূল সূত্ৰ-দানকারী ছিলেন কনাদ) ভারতবর্ষে বহুল প্রচলিত ছিল। তাছাড়া শংকরের আগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগার্জুন একজন বিজ্ঞানমনস্ক ও অত্যন্ত মেধাবী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের বিষয়বস্তু গুলিকে খন্ডন করতেন । নিজ নিজ ব্যক্তি-ভাবনা বা সাম্প্রদায়িক-ভাবনা অপরকে গ্রহণ করানাের একটা অপচেষ্টা সবকালেই মানুষের মধ্যে রয়েছেএর ফলেই যত জটিলতা। ফলে “বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য”– প্রকৃতির এই যে মূল সুর রয়েছে_ সেটা আর মেনে চলা হয় না।
যাইহােক, নাগার্জুন বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়ােগ করে ‘অনাত্মবাদ’ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় বিভিন্ন হিন্দু পন্ডিত ও সন্ন্যাসীদের তর্কযুদ্ধে আহবান করতে লাগলেন। তখনকার যুগে নিয়ম ছিল, কোন সন্ন্যাসী বা পণ্ডিতের সাথে কারও তর্কযুদ্ধ হলে যিনি হারবেন, তাঁকে সশিষ্য অপরপক্ষের দলে যােগ দান করতে হবে। এজন্য অনেকে আত্মগ্লানি হতে মুক্তির জন্য তুষানলে প্রাণত্যাগ করতেন। এইভাবেই নাগার্জুনের সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে অনেক হিন্দু পন্ডিত এবং সাধু তুষানলে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।
তবে বৌদ্ধদের এই জয়রথ থামিয়ে দিয়েছিলেন কুমারিল ভট্র! ধর্মপাল নামে একজন মহাপন্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু যখন নালন্দা বৌদ্ধবিহারে অধ্যক্ষ, কুমারিল তখন এক তরুণ ছাত্র হিসাবে ওখানে ভর্তি হয়েছিল। ছাত্রটির বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনসমূহ পাঠ করে কুমারিল অল্প বয়সেই অসাধারণ পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। একদিন বৌদ্ধ সঙ্ঘের সদস্যরা ঈর্ষান্বিত হয়ে কুমারিলকে পাহাড়ের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। অনেক নীচে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হবারই কথা ছিল কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় হাড়গােড় ভাঙা মুমূর্ষু কুমারিলকে একদল হিন্দু সন্ন্যাসী দেখতে পান এবং চিকিৎসার জন্য তাদের আশ্রমে নিয়ে যান। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী সন্ন্যাসীরা সুচিকিৎসার দ্বারা কুমারিলকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তােলেন। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা কুমারিল ধীরে ধীরে হিন্দু সন্ন্যাসী-পরম্পরার শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন তাঁদের কাছে। সন্ন্যাসীরাও কুমারিলের সুমেধার পরিচয় পেয়ে তাকে শিক্ষাদানে অত্যন্ত আগ্রহী হন। এইভাবে কিছু দিন পর তিনি 'কুমারিল ভট্ট' নামে নিজেকে পণ্ডিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরপরই তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ধর্মপালকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ফলে উনিও তুষানলে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হন।কিন্তু আবার অঘটন ! গুরুকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করতে বাধ্য করায়, মনস্তাপে কুমারিল, শিষ্য মণ্ডনমিশ্রের উপর আশ্রমের ও শিষ্যদের ভার দিয়ে প্রয়াগে তুষানলে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদিকে আচার্য শংকর তখনও তরুণ, কিন্তু গুরু গােবিন্দপাদের নির্দেশে তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমায় ও বেদান্ত ভাষ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে বেরিয়ে পড়েছেন। কাশীতে এসে তিনি জানতে পারলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কুমারিল প্রয়াগে তুষানলে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন আচাৰ্য্য। কিন্তু তখনকার দিনে তো আর এখনকার মতাে Transport- এর ভাল ব্যবস্থা ছিল না, তাই পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। তিনি গিয়ে দেখলেন কুমারিল অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেই জ্বলন্ত তুষানলে শান্তভাবে দণ্ডায়মান থেকে ইষ্টের স্মরণ-মনন করছেন। অদ্ভুত দৃশ্য ! শংকর সেই অবস্থায় কুমারিলকে তার নিজের সৃষ্ট বেদান্তভাষ্য শােনালেন (যা উত্তর-মীমাংসারূপে পরিচিত)। কুমারিল ভট্ট সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতার্কিকও। বুদ্ধিমত্তা ওপাণ্ডিত্যের জোরে তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতেন। কিন্তু তাঁর বােধে বােধ ছিলনা। ফলে অন্তরে এক নিদারুণ অতৃপ্তি ছিল তাঁর, তাই তো তিনি আত্মগ্লানিতে ভুগতেন এবং যার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তুষানলে আত্মাহুতি । ভগবান শংকরের অবতার আচার্য শংকরের কাছে শারীরক মীমাংসার সূত্রগুলি ও তার অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে পরম শান্তি পেলেন অর্ধদগ্ধ কুমারিল এবং ঐ অবস্থা থেকেই তিনি তরুণ শংকরকে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন যে এই অপূর্ব ঔপনিষদিক সিদ্ধান্ত তিনি যেন তাঁর শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে শােনান, তাহলেই ভারতবর্ষে শংকরের মত প্রতিষ্ঠা পাবে। এরপর কুমারিল চরম নিশ্চিন্তে ও পরম শান্তিতে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর অন্তিম সংস্কার হওয়ার পর আচাৰ্য শংকর,মণ্ডন মিশ্রের কাছে গিয়ে তাঁকেও তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করেন। সে আবার অন্য ইতিহাস।
জিজ্ঞাসু :– ভগবান বুদ্ধের মতকে খণ্ডন করে ভগবান শংকরের নতুন মত প্রতিষ্ঠা করার কি দরকার ছিল? ঐ মতকেই তাে তিনি পুষ্ট করতে পারতেন ?
গুরুমহারাজ :– তোমার বােঝার ভুল হচ্ছে ! ভগবান বুদ্ধের মতকে শংকর খণ্ডন করেননি, বৌদ্ধদের মত খণ্ডন করেছেন। কোন আধ্যাত্মিক পরম্পরার শক্তি তিন প্রজন্ম পর্যন্ত যে কোন সমাজকল্যাণমূলক সংঘে ক্রিয়াশীল থাকে! তারপর আবার যতদিন না পর্যন্ত কোন আধ্যাত্মিক মানব শরীর গ্রহণ করেন, ততদিন ঐ পূর্বোক্ত মহামানবের জীবন, তাঁর শিক্ষা, নির্দেশ ইত্যাদির অনুসরণ চলতে থাকে মাত্র । কিন্তু মানুষ তো অহংপ্রধানতাই পরবর্তী উত্তরসূরিরা নিজ নিজ মতকেই প্রাধান্য দেয়, এইভাবে শুরু হয় দলাদলি, সঙ্ঘের ভাঙন ইত্যাদি। অাচাৰ্য শংকর যখন এসেছিলেন বৌদ্ধরা তখন বহু দলে বিভক্ত। বিভিন্ন অভিচারক্রিয়া ঢুকে পড়ায় বীভৎস কার্যকলাপ চলছিল বিভিন্ন বৌদ্ধ সঙ্ঘে। মানুষের মনে ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধেও ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। ঠিক তখনই ভগবান শংকর মনুষ্য সমাজে নেমে এলেন । মহামানবদের আগমনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য সনাতন ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখা, ধর্মের মধ্যে গ্লানি এলে তাকে গ্লানিমুক্ত করা, ধর্মের পুনঃস্থাপন নয়—সংস্থাপন করা। আর তিনি এটাই করেছিলেন, অবশ্য সবসময় এটাই অবতারগণ করে থাকেন। “অবতার”-বলতে কি বোঝানো হয় বলছি__যখন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-ই খণ্ড আকারে দেহ ধারণ করেন, অমূর্ত থেকে মূর্তিমান হন, অরূপ থেকে রূপ পরিগ্রহ করেন, অসীম থেকে সীমায় ধরা দেন, সেই ভাগবতী তনুধারী ভগবানের কথাই এখানে বলা হচ্ছে।
ভেদবুদ্ধি থাকলে এই কথাগুলো ঠিকমতো ধরতে পারা যায় না, কথাগুলো জটিল মনে হয়, কথাগুলোর মানে ভিন্ন বলে মনে হয়_ এবং এভাবেই ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই তোমরা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন হয়োনা, ঐক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হও। তবেই মা জগদম্বার লীলার আস্বাদন করতে পারবে।
জিজ্ঞাসু :— বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এমন কি যুক্তি ছিল যা আচাৰ্য্য শংকরের আগে হিন্দু সন্ন্যাসীরা বা পণ্ডিতরা খণ্ডন করতে পারতেন না ?
গুরুমহারাজ :— আমার সাথে রায়নায় একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষুর দেখা হয়েছিল । উনি ভারত, নেপাল, তিব্বত এইসব দেশের ‘ধর্মাঙ্কুর’-সংঘের প্রধান ছিলেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কেন আপনারা ‘আত্মা’ মানেন না। উনি উত্তর দিলেন ‘আত্মা’ বলে কিছু নেই, তাই মানিনা। আমি বললাম, আপনারা জন্মান্তর মানেন, এক-একটা জীবনের অভিজ্ঞতাকে মানেন, অথচ জড় ও জীবনের আধার যে “আত্মা”,তাকে মানেন না কেন? উনি বললেন—জীবন হচ্ছে জ্বলন্ত দীপশিখাবৎ । সেখানে বর্তমানের প্রায় কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ প্রতিমুহূর্তে দাহ্য পদার্থের যােগানে দীপশিখা জ্বলছে_ কিন্তু দেখতে না দেখতেই বা ভাবতে না ভাবতেই নতুন দাহ্যপদার্থের যােগান আসছে এবং নতুনভাবে শিখার সৃষ্টি হচ্ছে–এইভাবেযাকে “দীপশিখা” ভাবছি, তাতে বর্তমানের কোন অস্তিত্বই নাই _তা শুধু অতীতের ফল এবং যা ক্রমাগত চলে যাচ্ছে ভবিষ্যতের গহব্বরে। অর্থাৎ ভ্রান্তিবশতঃ নিরবচ্ছিন্ন বর্তমান জ্বলন্ত দীপশিখা বলে যা ভাবছেন বা দেখছেন তা নেহাৎ-ই অতীতের continuation এবং যা ক্রমাগত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। তাহলে যেখানে বর্তমানেরই কোন অস্তিত্ব নেই, সেখানে নিত্য-শাশ্বত, সনাতন কোন সত্তা–আপনারা যাকে ‘আত্মা’ বা ‘ব্রহ্ম’ বলেন তার অস্তিত্ব কি করে সম্ভব?