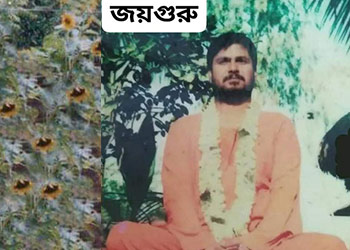স্থান ~ পরমানন্দ মিশন । সময় ~ ১৯৮৬ উপস্থিত ব্যক্তিগণ ~ গঙ্গাবাবু, তরুণ, রবীন ও আরও অনেকে ৷
জিজ্ঞাসু :— আচ্ছা গুরুমহারাজ ! আমরা দেখি আমাদের মত অনেক গৃহীরা আপনার সিটিং-এ বসে থাকে, আপনি তাদের সাথে কথা বলেন_ মেলামেশা করেন! কিন্তু আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের তো এখানে বড় একটা আসতে দেখি না?
গুরুমহারাজ :— ওদের সময় কোথায়? ওরা প্রত্যেকেই তো কোন না কোন কাজে নিয়োজিত। যতদিন না ওরা কাজে আত্মনিয়োগ করেছে ততদিনই তো ওদের সৎসঙ্গ করার প্রয়োজন ছিল — আর কি প্রয়োজন? এবার ‘বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়’ নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলেই ওরা তরতর করে এগিয়ে যাবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন_ নেমতন্নবাড়ির চিঠিটা ততক্ষণই প্রয়োজন যতক্ষণ না ওটা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়! যাই পাওয়া গেল, ওটা ফেলে দিলেও আরকোন ক্ষতি নেই, তেমনি সাধুসঙ্গ-সৎসঙ্গ এসবের প্রয়োজনীয়তা তো শুধু নিজেকে তৈরি করার জন্য — তৈরি হয়ে গেলে আর ওসবের দরকার নেই তো ! তখন সে নিজেই তো সাধু — তার সঙ্গ করে কতজনের উপকার হবে — তাকে কেন্দ্র করেই সৎগ্রন্থ লেখা হবে, তাই নয় কি?
তবে জানো, আমার কাছে থাকে অথচ আমার থেকে অনেক দূরে আছে, আবার অনেক দূরের ব্যক্তি আমার কাছের মানুষ — এমনও কিন্তু অনেক আছে! এসব সত্বেও এখানে(বনগ্রামে) যারা আছে — তারা অবশ্য অন্য স্থানে থাকা ব্যক্তিদের থেকে আধ্যাত্মিক সাহায্য পায় অনেক বেশি! এবার সেটা কাজে লাগাতে পারলেই দ্রুত এগিয়ে যাবে। আসলে ভাব-জগৎটাই তো আসল। ‘যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।’ সেইগুবরে পোকা আর ভ্রমরের গল্পটা জানোতো দুজনের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। ভ্রমর পদ্মবনে মধু খায়। আর গুবরেপোকা গোবর খেয়ে মরে। এই দেখে ভ্রমরের মনে খুব কষ্ট হল। ভাবল বন্ধুকে যদি একদিন মধুর আস্বাদ দিতে পারি, তাহলে ও আর কোনদিন অখাদ্য গোবর খাবে না। এই ভেবে একদিন ভ্রমর গুবরেপোকাকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মবনে গেল। সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসেই ভ্রমরের গুনগুনানি বন্ধ হয়ে গেল! সে পদ্মের সৌরভে আমোদিত, আহ্লাদিত হোল এবং তন্ময় হয়ে মধুর স্বাদ গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরতেই বন্ধুর কথা মনে পড়ায় পাশে চেয়ে দেখল বন্ধু এ ফুল ও ফুল করে বিরক্তমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভ্রমর তো অবাক! জিজ্ঞাসা করল ‘বন্ধু, পদ্মের মধুর কি সুন্দর আস্বাদ তাই নাবলো?” গুবরেপোকা বিরস বদনে বলল,’কই — এ তো গোবরের মতই’। এ কথা শুনে ভ্রমর রেগে-মেগে বলল, “কি বললি, গোবরের মত? দেখি মুখটা হাঁ কর তো!’ মুখ হাঁ করতে দেখা গেল গুবরেপোকার মুখের ভেতর একতাল গোবর ভরা! এই দেখে ভ্রমর গুবরেপোকাকে বলল ‘ফেলে দে গোবর!’ তখন গুবরেপোকা মুখ থেকে গোবর ফেলে দিয়ে মুখ ধুতেই — ভ্রমর বলল ‘এবার পদ্মের মধু খা।’ তখন গুবরেপোকা মধুর আস্বাদ পেল এবং ধীরে ধীরে সেই গন্ধে — সেই স্বাদে তন্ময় হয়ে আত্মস্থ হয়ে গেল। এরপর ঐ গুবরেপোকা ভ্রমরায় পরিণত হল। এই একই কথা অন্যত্র বলা হয়েছে_ মানস সরোবরে স্নান করলে কাকও রাজহংস হয়ে যায়।
যাইহোক, এবার কথা হচ্ছে_ ওই যে গোবর মুখে নিয়ে মধুর আস্বাদ করতে যাওয়া এটা মূর্খতা। কিন্তু মানব-প্রকৃতি এমনই যে, যার যা প্রকৃতি বা স্বভাব তাকে অস্বীকার করাও যাবে না! তা যখন যাবে না,তখন তাকে অতিক্রম করতে হবে! যে পারবে সে মধুর স্বাদ পাবে, আত্মস্থ হবে_ অন্যথায় একূল-ওকূল ঘুরে বেড়াবে।
এখানে ভ্রমর হচ্ছে সদগুরু। গুরু চান শিষ্য কমলবনরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করুক আর তার মধ্যে ঢুকে সহস্রদল পদ্ম বা সহস্রারে মধুরূপ চন্দ্রবারুণী সুধা পান করুক, কারণ তা করলেই আর বিষয়-রস, পার্থিব জগতের মোহ-মায়া ভাল লাগবে না। কিন্তু কথায় আছে না ‘গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের যদি কৃপা হৈল, একের কৃপা বিনে জীব ছারেখারে গেল।’ এখানে “একের কৃপা” অর্থাৎ নিজকৃপা, জীব নিজেই নিজের প্রতি অযত্নশীল। আলস্য, জাড্য, প্রমাদ এগুলি তাকে এমনভাবে গ্রাস করে রেখেছে যে, এখান থেকে আর সে বেরোতে পারছে না। এ যেন অনেকটা গুটিপোকার মত, নিজেই নিজের লালা দিয়ে দিয়ে তৈরি করেছে আবরণ _তারপর সেটা শক্ত হয়ে গেছে, আর বেরোতে পারছে না। ওই গুটি কেটে বেরোতে পারলেই আর পোকা বা কীট নয়, বহুবর্ণবিশিষ্ট মুক্ত আকাশে অবাধ বিচরণরত প্রজাপতি, যার রঙ-বাহারে সবাই আকৃষ্ট! গুটিপোকা কীট অবস্থায় গাছের পাতা খেয়ে তার ক্ষতিসাধন করছিল, এবার প্রজাপতি হয়ে সে ফুলের পরাগমিলন ঘটাচ্ছে,সকলের উপকার করে বেড়াচ্ছে — এটাই রহস্য!
যাইহোক, সদগুরু যাঁরা তাঁরা শিষ্যদের সব ক্রিয়াকর্মই দেখেন, তিনি সবই বোঝেন! তিনি জানেন যে, পৃথিবীগ্রহের এখন নিতান্তই শিশু অবস্থা, এমতাবস্থায় এখানকার মানুষের মানসিকতা আর কতই বা উন্নত হবে, তাই তিনি প্রত্যেকের স্বভাব বা প্রকৃতি অনুযায়ী এগিয়ে চলার নির্দেশ দেন। কিন্তু যখন বেগতিক দেখেন, যখন দেখেন শিষ্য কিছুতেই শুনছে না, তখন ঘাড়ে ধরে বলেন ‘ফ্যাল গোবর!’ সদগুরু যাদেরকে আশ্রয় দেন, তিনি তাদের ভারও নেন। তাদের ইহকাল ও পরকালের দায়িত্ব নেন। তাই তো তিনি “গুরু” ! তিনি “লঘু” নন। এইজন্যই কঠিন কিছু বোঝাতে বলা হয় “গুরুভার” বা “গুরুদায়িত্ব”।
আমাদের আশ্রমের যারা কর্মী, তাদের অনেকে ব্যস্ততার জন্য প্রায়ই আমার কাছে আসতে পারে না, কিন্তু ওদের মধ্যে কয়েকজন স্মরণে-মননে সর্বদা আমাকে খেয়াল রাখে, আমি সেটা টের পাই। আমাদের রান্নাঘরের ছেলেরা বড় একটা এদিকে আসার সময় পায় না — মাঝে মাঝে আমিই সকালের দিকে রান্নাঘরেচলে যাই, ওদের সাথে দেখা করি_কথা বলি! পুকুরের পূর্বপাড়ের গাছগুলোর সঙ্গে দেখা করার জন্যও মাঝে মাঝে যেতে হয়। যেহেতু ওদিকটায় বড় একটা যাই না, তাই ওরা অভিমান করে! গোয়ালের জগবন্ধু আছে, ও একমনে গরুর সেবা করে। দ্যাখো, মানুষের যা যা চাহিদা তার কোনটাই ওর মধ্যে নেই। ওর(জগবন্ধু) রূপ নেই, শিক্ষা নেই, বংশমর্যাদাও তেমন নেই, কিন্তু রয়েছে সরলতা — অকপটতা। এখানে যখন এলো, তখন ভাল করে কথা বলতেও পারতো না। কিছুদিন এখানে কাটানোর পর _আমি শুধু একদিনই বলেছিলাম, "তুই এখন থেকে গরুর দেখাশোনা এবং গোয়ালের অন্যান্য কাজ করবি"! — ব্যস্, নিষ্ঠাসহকারে ও তখন থেকে ওই কাজটাই করছে। কখনও কোন complaint করেনি, কখনও ছোট কাজ বলে কাজে অবহেলা করেনি! আমি কিন্তু সব লক্ষ্য রাখি — ওর প্রতি আমি প্রসন্ন! ও কাজ করতে করতে উদাত্তগলায় গান গায় — গানের কথাগুলো হয়ত ঠিক নয় — সুরটাও বেসুরো, তবু আমি শুনি, আমার ভাল লাগে! ওর এই নিষ্ঠা, অকপটতা, বিশ্বাসই ওকে পূর্ণত্বে পৌঁছে দেবে।আমাদের কেশব রয়েছে — দেবানন্দ, একবার ওর নিম্নাঙ্গে কোন একটা infection মতো হয়েছিল। একদিন দুপুরে ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছি, ও খবরের কাগজ নিয়ে ঢুকল। তারপর একটু ইতস্তত করছে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কিরে কিছু বলবি?’ ও নিঃসংকোচে কাপড় তুলে আমাকে জায়গাটা দেখিয়ে বলল — ‘বাবা, দেখোতো এটা কি হয়েছে?’ আমি ঘা-টা দেখে _ওকে চিন্তা করতে নিষেধ করলাম এবং দীপ্তি মহারাজের কাছে ওষুধ খেতে বললাম। কিছু দিনের মধ্যেই ওর problem_solve হয়ে গেল। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার সন্তানদের মধ্যে ক’জন আমার কাছে এতটা নিঃসঙ্কোচ হতে পারবেবলোতো? সহজ, সরল, নিষ্কপট ব্যক্তিদেরকেই ঈশ্বর সবচাইতে বেশি ভালবাসেন। কিন্তু সহজ হওয়াই সবচাইতে কঠিন কথা, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার না থাকলে সহজ কি হওয়া যায়!
জিজ্ঞাসু :— আপনি আগে বলেছিলেন ৫/৭ জন বিবেকানন্দ তৈরী করবেন, কিন্তু এটা কি কখনও সম্ভব?
গুরুমহারাজ:— কি কথার কি মানে করলে বাবা – ঐজন্যই শাস্ত্র বলেছে সব কথা সবার জন্য নয়। ব্রহ্মবাক্য – আপ্তবাক্য সবার কাছে বলতে নেই! অধিকারী ছাড়া এসব কথা শোনাও ঠিক নয় আর বলাও ঠিক নয়। মহাপুরুষরাও তো এইজন্যেই বহুকথা বলতে চেয়েও বলেননি, বলতে ভয় পেয়েছেন। এমনকি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অনেক কথা বলতে গিয়েও বলতে পারতেন না, বলতেন_’ মা আমার মুখ চেপে ধরছে’/। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে মা জগদম্বা ঢালাও পারমিশন দিয়েছেন, তাই আমি পাত্রাপাত্র বাছি না, সব কথাই সকলকে বলে দিই – তাতে অনেক সময় খারাপও হয়, কিন্তু ভালও হয় – পৃথিবীগ্রহে এটা আমার একটা “এক্সপেরিমেন্ট” বলতে পারো।
যাইহোক, তোমাদেরকে যা বলছিলাম_ যখন সাধুসঙ্গে আসবে, তখন মন থেকে বিষয়চিন্তা বা অন্যচিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হয় – সাধুদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। মনঃ + যোগ = মনোযোগ। এটাও একটা যোগ – বক্তার সঙ্গে শ্রোতার। দ্যাখো, বিবেকানন্দ একটা মানুষ ছিলেন, তিনি শরীর ছেড়ে চলে গেছেন, ফলে সেই শরীরটা আর কি করে পাবে? তোমরা এমন মাথামোটা যে এটাও বুঝতে পারো না – ফলে আমাকে hammering করতে হয়। কিন্তু বিবেকানন্দত্ব একটা স্থিতি, সদাজাগ্রত বিবেকই বিবেকানন্দ! যেমন ভগবান বুদ্ধ বা অমিতাভ বুদ্ধ একজন ব্যক্তি কিন্তু “বুদ্ধত্ব” বা “অর্হত্ব” একটা স্থিতি। অমিতাভ বুদ্ধের পর অনেকেই “বুদ্ধত্ব” লাভ করেছেন, এতে বাধা কোথায়? আর এতো হবেই – এটাই তো চাই। এইজন্যই তো মহাপুরুষদের আসা! জীবের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটবে, চেতনার উত্তরণ ঘটবেজীব মানব হয়ে উঠবে-মানব হবে দেবতাদেবতারা ঋষিত্ব অর্জন করে পূর্ণত্বের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।।
আমিও চাই __তোরা সকলে এক একটা পরমানন্দ হয়ে ওঠ্ অর্থাৎ পরমানন্দ স্থিতিলাভ কর্। প্রাচীণকালে গৃহস্থ সমাজে এবং সাধু সমাজে এইরকমই অনেক “পদ” ছিল, একটা নির্দিষ্ট স্থিতিলাভ করলেই তাদের সেই পদ দেওয়া হোত। যেমন বশিষ্ট, জনক, এখনকার শংকরাচার্য। এঁরা শুধু একজন ব্যক্তি নন, পরপর অনেকে ঐ স্থিতির বা ঐ পদের লোক ছিলেন। বিবেকানন্দ ও সেইরকমই একটা স্থিতি!!এই নিয়ে কে কবে আপত্তি করেছে – মূর্খরা ছাড়া?
তাই বিবেকানন্দ স্থিতি নিয়ে যায় আমি যা বলেছিলাম, তা হোল সম্ভাবনার কথা! পূর্ণভাবে manifestation এর সম্ভাবনা তো প্রথম থেকেই বিদ্যমান। এইজন্যই বলা হয় 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং...' ইত্যাদি - অর্থাৎ এটাও পূর্ণ, ওটাও পূর্ণ। তাহলে একটা জীব যদি পূর্ণ হয়, তাহলে তার কিসের অভাব? শুধু প্রকাশের তারতম্য - তাইনা। এবার যদি কেউ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশিত করার কৌশল আয়ত্ব করে ফেলে, তাহলে সে আর জীব নয়, তখন "শিব"। এই শিবস্থিতিই "বিবেকানন্দ স্থিতি"। শিবস্থিতির আবার কয়েকটা প্রকাশের তারতম্য রয়েছে যেমন রুদ্র, প্রচণ্ড, শান্ত ইত্যাদি। যেমন রামায়ণে উল্লেখিত হনুমান _ শিবস্থিতির এক ধরণের প্রকাশ, স্বামী বিবেকানন্দ আরেক ধরণের প্রকাশ। এইভাবে প্রকাশের তারতম্য! সুতরাং আজও যে বা যাঁরা শিবস্থিতিতে রয়েছেন, তাঁদের কাজও কি ঐ একইরকম "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" হবে না! তাহলে বিরোধ কোথায় - শুধু বৈচিত্র্য রয়েছে। আর বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। সেখানে একরস - একসুর __সেখানে একাকার। অধ্যাত্মজগতের রহস্য বড়ই বিচিত্র 'গোপাল'(ছেলেটিকে মজা করে ঐরকম সম্বোধন করে বললেন)সেখানে না ঢুকলে কিছুই ধরতে পারবে না।